‘মাতাল’ তারাপদ
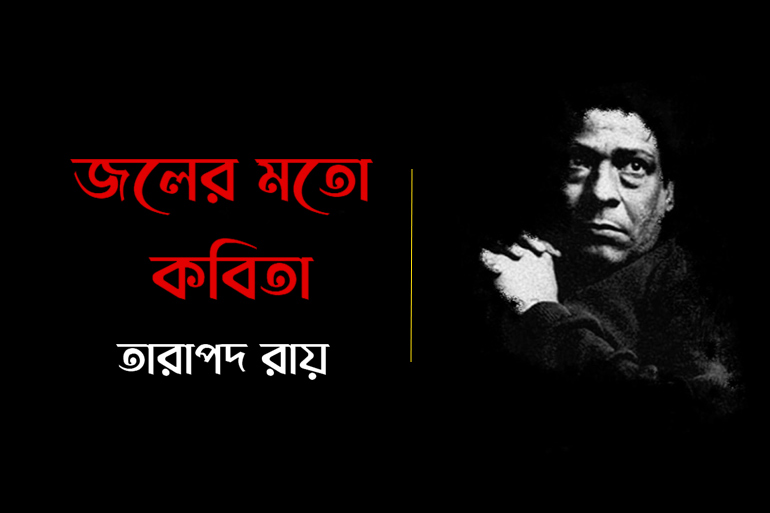
যাঁরা তারাপদ-ভক্ত তাঁরা জানবেন তাঁর মদ ও মাতাল প্রীতি। যখন কেউ-কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মদ ও মাতাল নিয়ে তিনি এত মাথা ঘামান কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তাঁর ‘মাতাল সমগ্র’ বইয়ের ভূমিকাতে।
“সাধে কি আর মাথা ঘামাই। সব কথা বলতে গেলে বিপদ হতে পারে। তবে কবুল করি, মদ এবং মদ্যপানের প্রতি আমার আযৌবন তেষ্টা আকর্ষণ ছিল এবং আছে।…”
থ্রি চিয়ার্স
তারাপদ রায়
১ জানুয়ারি, ২০০২
মাতাল সমগ্রের ‘মত্ত’ গল্পে লিখেছিলেন, একটি মামলার প্রয়োজনে একবার জেলা শহরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সেখানে গিয়ে সবচেয়ে বড়ো উকিলের খোঁজ করলে, তিনি জানতে পারেন এলাকার এক নম্বর উকিল বলাইবাবু; অবশ্য তিনি যদি মাতাল অবস্থায় না থাকেন। ‘মাতাল উকিল’ শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন তারাপদ। উকিলের আগে মাতাল বিশেষণটা ভালো না ঠেকায়, তিনি জানতে চান, ‘দু নম্বর ভালো উকিল কে?’
আরও পড়ুন: জয় গোস্বামী : চূর্ণিতীরের এক প্রাচীন বালক
তাঁকে জানানো হয়, ‘দু নম্বর ভালো উকিল হলেন ওই বলাইবাবুই, তিনি যখন মত্ত অবস্থায় থাকেন’। এহেন হেঁয়ালি শুনে অন্য উকিলের দ্বারস্থ হন তারাপদ।
এরপর, আদালত নয় বিদেশী এক শহরে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটি পানশালার নাম নাকি ‘অফিস’। এমন চমকপ্রদ নামকরণের ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে না পারলেও, পরে রহস্যটা উদ্ধার করেছিলেন। সেই পানশালায় যাঁরা যেতেন, তাঁরা ফন্দি এঁটেছিলেন, যত দেরি করেই বাড়ি ফেরা যাক, মিথ্যে না বলে সত্যি কথাই বলা যাবে, ‘অফিসে দেরি হয়ে গেল।’
আবার, ‘মকারান্ত’ গল্পে তিনি বুঝিয়েছিলেন লম্পট আর মদ্যপ এক নয়, পার্থক্য রয়েছে। লুজ ক্যারেকটার বা লম্পট চরিত্রের লোকেদের আমরা সবাই অল্প-বিস্তর চিনি। সকলের মতোই এঁরাও সংসারে বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এঁরা সাধারণত ফিটফাট থাকেন। এঁরা সর্বদাই হাসিমুখ। ঘাড়ে পাউডার, চুলে টেরিকাটা, রুমালে সুরভি, রমণী-মোহন। ওঁদের জন্যই নাকি শাস্ত্রে উপদেশবাক্য লেখা হয়েছিল, ‘পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে।’
এবার মদ্যপ। লম্পট আর মদ্যপ, এক জিনিস নয়। বহু লম্পট আছে যারা মদ ছুঁইয়েও দেখে না। আবার প্রকৃত মদ্যপের লাম্পট্য আসক্তি নেই। যে মদ খায় সে শুধুই মদ খায় আর মদ তাকে খায়, তার আর কিছুই করার থাকে না। এদিকে, লম্পটের মদ্যপ হলে বিপদ। তাকে ভেবেচিন্তে, মেপে চলতে হয়। তার উদ্দ্যেশ্য সাধনের জন্য তাকে নানারকম অভিনয় করতে হয়, মুখোশ পরতে হয়। মাতালের মুখোশ নেই। সে অভিনয় করতেও অপারগ।
পানাসক্তি এবং লাম্পট্যের একটা যুগ্ম গল্পও বলেছিলেন তিনি।
গভীর রাতে মত্তাবস্থায় অনিমেষবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় চাবিটা লাগানোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় পুলিশের জমাদার তাঁকে ধরে।
জমাদারকে দেখে অনিমেষবাবু তাঁকে বাড়িটা শক্ত করে ধরতে বলেন কারণ বাড়িটা এত কাঁপছে যে তিনি চাবি লাগাতে পারছেন না। জমাদার সাহেব অনিমেষবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এত রাতে এখানে কী হচ্ছে?’
অনিমেষবাবু বলেন, ‘এটাই আমার বাড়ি। আমি বাড়ির মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।’
ঘুঘু জমাদার সাহেব তাঁর কথা বিশ্বাস না করে, অনিমেষবাবুকে বললেন, ‘চলুন আপনাকে ভিতরে দিয়ে আসি।’ টলটলায়মান অনিমেষবাবুকে ধরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে জমাদার সাহেব দেখলেন ঘরের মধ্যে বিছানায় এক মহিলা এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে অনিমেষবাবু বললেন, ‘এবার বুঝছেন তো এটা আমার বাড়ি। ওই বিছানায় শুয়ে আছেন আমার মিসেস, আর যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন সে হলাম আমি।’ দু’ একটা নয়, এরকম অজস্র গল্প লিখে গিয়েছেন তারাপদবাবু। তাঁর আফসোস ছিল ‘আমাদের দেশে এরকম গুরুতর বিষয় নিয়ে মজার গল্প হয় না’। মৃত্যুর বিষাদ নয়, তিনি আজীবন হাস্যরসের সন্ধান করে গিয়েছেন—জীবনের রস। যে ‘স্যাটায়ার’-এ চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বাস করতেন, তিনিও তা-ই। যেমন- তাঁর লেখা এই কবিতাটা:
দু’ একটা নয়, এরকম অজস্র গল্প লিখে গিয়েছেন তারাপদবাবু। তাঁর আফসোস ছিল ‘আমাদের দেশে এরকম গুরুতর বিষয় নিয়ে মজার গল্প হয় না’। মৃত্যুর বিষাদ নয়, তিনি আজীবন হাস্যরসের সন্ধান করে গিয়েছেন—জীবনের রস। যে ‘স্যাটায়ার’-এ চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বাস করতেন, তিনিও তা-ই। যেমন- তাঁর লেখা এই কবিতাটা:
তিনি আমার ছায়া
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি।
চুল আঁচড়াই, দাড়ি কামাই,
কখনও নিজেকে ভাল করে দেখি,
ফিসফিস করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি,
‘কেমন আছ, তারাপদ?’
কখনও কখনও নিজেকে বলি,
‘ছেষট্টি বছর বয়েস হল,
যদি আর অর্ধেক জীবন বাঁচো,
শতায়ু হবে।’
নিজের রসিকতায় নিজেই হাসি
নিজে অর্থাৎ আমি নিজে এবং আয়নার নিজে।
এইরকম ভাবে একদিন,
কথা নেই, বার্তা নেই আয়নার নিজে
কি কৌশলে আয়নার থেকে বেরিয়ে আসে।
আমি তাকে বোঝাই, ’এ হয় না, এ হতে পারে না ।’
সে আমাকে বোঝায়, ’এ হয় না, এ হতে পারে না ।’
আয়নার সামনে এইরকম কথা কাটাকাটি হতে হতে
হঠাৎ সে আমাকে এক ধাক্কায়
আয়নার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।
তারপর থেকে আমি আয়নার ভিতরে।
আর যার সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা, চলাফেরা,
সে তারাপদবাবু কেউ নন,
তিনি আমার ছায়া।






























