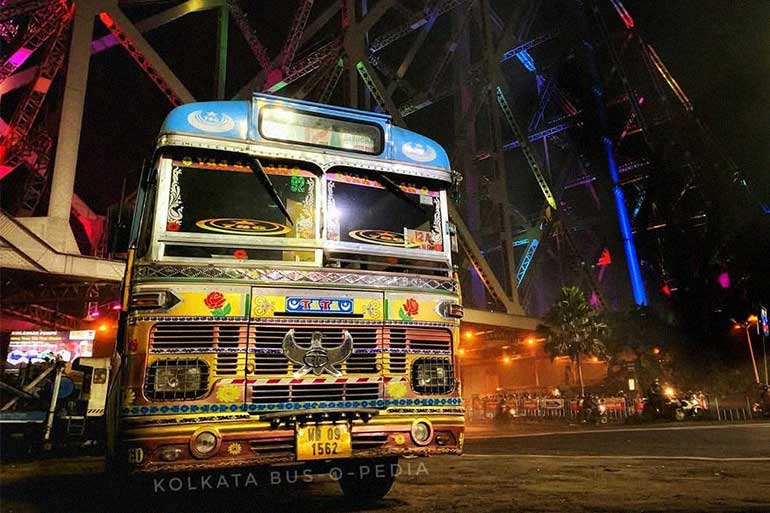উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ‘দেশ’ কাকে বলে, প্রশ্নের উত্তর শহর কলকাতায় ছিল না।

‘দেশ’ কাকে বলে? এই প্রশ্নের কোনও সদ্উত্তর, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার শহর কলকাতায় ছিল না। তখন ১৮১৭ সালের কলেরার মহামারীর পর জঙ্গল কেটে, পুকুর বোজাচ্ছে লটারি কমিটি। পথে হস্তী-চলাচল নিষিদ্ধ হলেও বাঙালিটোলাতে ধনী চূড়ামনীদের আচার আড়ম্বরের অভাব নেই। সাত-আট মহলা অট্টালিকাতে দোল, রাস, দূর্গোৎসব, কাঙ্গালি বিদায়ে খরচা হয় হাজার হাজার সিক্কা টাকা, ঘুড়ির লড়াই বা শখের কুস্তিতেও হয় অভাবনীয় জাঁকজমক। এর মধ্যেই হাজার হাজার গোলপাতার ঘর, দুর্গন্ধময় পগার, উড়ে পাল্কি বেহারাদের আড্ডা ও হাড়গিলেদের ভীড় কাটিয়ে এগিয়ে চলে অনাহার, চোর ডাকাত, রোগ, বেশ্যালয়ে পরিপূর্ণ কলকাতার ব্ল্যাক টাউন। সেখানে ধনীদের অট্টালিকায়তে মুনশী আসেন ফার্সী বয়েৎ শিক্ষা দিতে, আর চতুষ্পাঠীতে পন্ডিতের কাছে পোড়োরা তালপাতার ওপর অক্ষর লেখা শেখে। ‘দেশ’ কাকে বলে, সেই পাঠ সেখানে অনুপস্থিত। বরং লাট-বেলাটের নজর কাড়ার জন্য সভাবাজার, জোড়াসাঁকো, শিমুলিয়া, হাটখোলার প্রাসাদগুলিতে রোশনাই, বাইনাচ ও খানাপিনার আমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়দের বিপুল সমাগম ঘটে। আলোচনায় শোনা যায়, আসছে ইংরেজির যুগ। কিছুদিনের মধ্যে আদালতেও ফার্সীর জায়গায় ব্যবহার হবে ইংরেজী।

নড়েচড়ে বসলেন বিত্তবান বাঙ্গালীরা। কিছুদিনের মধ্যেই ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের সাথে জোট বেঁধে বাঙ্গালী ‘ম্যানেজারেরা’ ১৮১৭ সালে স্থাপন করলেন হিন্দু কালেজ। হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের পরিবর্তে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ চালু হল। ইউরোপিয় অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিতে আসতো বিত্তবান জমিদারপুত্রেরা এবং হেয়ার সাহেবের আরপুলির ফিরিঙ্গী পাঠশালার কিছু দরিদ্র মেধাবী ‘ফ্রি’ ছাত্র। এই প্রথম শুরু হল সমাজের তিনটি শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান। তাঁতি, কায়েত, স্বর্ণবণিক সবাই পড়ছে একই মহাবিদ্যালয়ে, খাচ্ছে একই টানাপাখার হাওয়া।

১৮২৬ সাল নাগাদ কলেজের ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করল। তার প্রধান কারণ, সেই বছর মে মাসে, হেনরী ডিরোজিও নামে এক সতের বছর বয়সীযুবক ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে কলেজে যোগ দেয়। সে নিজে ধর্মতলা অ্যাকাডেমির স্কটিশ এনলাইটমেন্টে দীক্ষিত ডেভিড ড্রামন্ডের ছাত্র। তাই নিজের প্রায় সমবয়সী ছাত্রদের সে দিতে শুরু করেবেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রিড, স্টুয়ার্ড প্রমুখ দার্শনিকের তত্ত্বের পাঠ।
আশ্চর্য! এত বছর পর,ধর্ম, কুসংস্কার, দলাদলি ছাড়িয়ে জন্ম হল কয়েকটি তরুণ মনের। এই উন্মুক্ত মানসভুমির নামই কি দেশ? যেখানে চিন্তারা স্বাধীন, যেখানে মন কালাপানি পেরিয়ে দিব্যচক্ষে দেখতে পায়, ভেঙে যাচ্ছে বাস্তিলের দরজা, আকাশে উড়ছে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফরাসী পতাকা?
তখন থেকেই থেকে পাল্টে গেল সব কিছু। অন্যান্য ব্যবসায়ীর মতন, দেওয়ান রামমোহন রায় বা দ্বারকানাথ ঠাকুরও ধারণা পোষণ করতেন, যে নীল চাষ বা বৃটিশ সাম্রাজ্য ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলময়। এই সময় ডিরোজিওর ‘India my native land’ কবিতায় ‘দেশ’ প্রথম প্রকাশ পেল দেবীরুপে। ‘পার্থেনন’ পত্রিকায় তাঁর ছাত্রদেরই লেখা প্রবন্ধে উঠল ইংরেজদের এ দেশে বসবাস নিয়ে প্রশ্ন । হিন্দু কলেজের ছাত্র, প্রথম ‘স্বদেশী’ ইংরেজি ভাষার কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখলেনIndian Gazetteপত্রিকায়,
Land of the Gods and lofty name;
Land of the fair and beauty’s spell;
Land of the bards of mighty fame;
My native land! for ever fare well!
হে পাঠক! এই সময়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিল তিতুমীরের বিদ্রোহের আগুন, পাগলপন্থীদের আন্দোলন। বর্মা যুদ্ধে কালাপানি পেরোতে অস্বীকার করেছিল কোম্পানী বাহাদুরের ভারতীয় সৈন্যেরা। পাল্কী বাহকেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য হলেও, জন্ম দিয়েছিল ধর্মঘটের। আর নবনির্মিত অক্টারলোনী মিনারের ওপর কেউ একদিন উড়িয়ে দিয়েছিল ফরাসী পতাকা।
এভাবেই, সবাইকে অবাক করে স্বাধীনতার প্রথম পাঠ নিয়েছিল শহর কলকাতা।