শ্যামলী খাস্তগীর : সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনের শনিবারের হাট

শান্তিনিকেতনের শ্যামলী খাস্তগীর (Shyamali Khastagir) সেই সব বিরলতম মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা মনে করেন এই পৃথিবী নামক গ্রহটির কাছে তাঁদের অনেক ঋণ এবং সেই ঋণ যে শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত, তা নয়। সমগ্র মানবসভ্যতার যাবতীয় ঋণের দায় তাঁরা তাঁদের প্রাণে অনুভব করেন। আবার এই অনিঃশেষ ঋণের দায় যে তাঁদের জীবনভর একেবারে জর্জরিত করে রাখে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে জনমানব বিচ্ছিন্ন করে রাখে – তা কিন্তু একেবারেই নয়। উল্টে সেইসব আনন্দময় নারী-পুরুষদের আনন্দ-ভাণ্ডার থেকে আমরা সবাই যদি মুঠো ভর্তি করে আনন্দ তুলেও নিই তাও তাঁদের আনন্দের খনি কখনোই নিঃশেষিত হয় না। শ্যামলী খাস্তগীর সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে একজন। শ্যামলী খাস্তগীরের পরিচয় অনেকগুলি। শিল্পী, ভাস্কর, লেখক, পরিব্রাজক – যদিও তাঁর এই সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে যে পরিচয়টি তাঁকে চিনে নেবার বিশেষ অভিজ্ঞান তা হল তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বা। পরমানুশক্তি এবং অস্ত্রবিরোধী, যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্রবিরোধী, ভোগবাদী সভ্যতার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার কথা শ্যামলী সারাজীবন সোচ্চারে বলেছেন। কখনও তার জন্য জেল খেটেছেন বিদেশের মাটিতে, কখনও ভারতবর্ষের কত অখ্যাত জনপদ, মফস্সলে পৌঁছনোর জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ পথ একলাই হেঁটেছেন, শান্তিনিকেতনের রাস্তায় শুয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার নির্লজ্জ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, নির্বিচারে পলাশ ফুল ধ্বংস রুখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন, বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন।
আচার্য নন্দলাল বসু-র অন্যতম প্রিয় ছাত্র, বিখ্যাত শিল্পী সুধীর খাস্তগীর এবং মনোরমাদেবীর একমাত্র সন্তান শ্যামলী খাস্তগীর-এর জন্ম ১৯৪০ সালের ২৩ জুন কলকাতায়। শ্যামলীর জন্মের ঠিক দশমাস পরেই এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মনোরমাদেবীর জীবনাবসান ঘটে। সেই থেকে মাতৃহারা শিশু শ্যামলী কখনও বাবার সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্র দুন স্কুলে, কখনও সিলেটে তাঁর বড়োপিসির বাড়িতে থাকতেন। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে শ্যামলীর বয়স যখন নয়-দশবছর, তখন ঠাকুমা সৌরনলিনীদেবীর সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। এসে ওঠেন কবিকন্যা মীরাদেবীর ‘মালঞ্চ’ বাড়িতে। সেখানে থেকেই ১৯৫০ সালে আশ্রম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু হয় শ্যামলীর। এই আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পরবর্তীকালে কলাভবনের শিক্ষা, তার মুক্ত পরিবেশ, অবিস্মরণীয় শিক্ষকদের সামীপ্য, সহপাঠীদের সঙ্গে সহযাপনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা এবং সর্বোপরি সে যুগের শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সান্নিধ্য শ্যামলীর জীবনের সলতে পাকানোর দিনগুলিতে তাঁকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল একথা শ্যামলী জীবনভর পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। শিল্পীকন্যা শ্যামলীর শিল্পে হাতেখড়ি সেই শিশুকাল থেকেই। একথা জানলে আশ্চর্য হতেই হয় শ্যামলীর যখন মাত্র দশবছর বয়স তখনই এলাহাবাদে তাঁর বাবার চিত্রপ্রদর্শনীতে শ্যামলীরও আট/দশখানা ছবি প্রদর্শিত হয়। পরবর্তী জীবনেও তাঁর প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তাঁর শিল্পই। শিল্প রচনার তাগিদ, তার বিষয়বস্তু, তার মাধ্যম এবং তার ব্যাবহারিক দিক এমনভাবে মিলেমিশে গিয়েছিল যে শ্যামলী খাস্তগীরের ছবিই তাঁর প্রতিবাদের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল।

শ্যামলী পুতুল গড়তেন। তাঁর বিখ্যাত ‘বসুন্ধরা’ পুতুলের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইতেন ভোগবাদী সভ্যতার সত্যিকারের স্বরূপ। শ্যামলীর রান্না ছিল তাঁর বিকল্প পথের সন্ধানী মনের পরিচায়ক, সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শনিবারের হাট, সে হাট আজ তার মূল থেকে সরে গিয়ে অন্যরূপ নিয়েছে। যে রূপকে মনেপ্রাণে ঘৃণাই করতেন শ্যামলী।
কলাভবনের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬২ সালে শ্যামলী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন আইআইটি-র সম্ভাবনাময় তরুণ অধ্যাপক তান লীর সঙ্গে। ভারত-চীন যুদ্ধের আবহে তাঁদের এই বিবাহ সেযুগের শান্তিনিকেতন তো বটেই, সমগ্র দেশেই একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। বিয়ের কিছুকাল পরেই স্বামীর কর্মসূত্রে তাঁরা পাড়ি দেন কানাডার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ছোটো শহর কিটিম্যাটে। প্রবাস জীবনের এই পর্ব থেকেই শ্যামলীর ভাবনাচিন্তা একটি ভিন্নপথে বাঁক নিতে শুরু করে। সৌখিনতার ঘেরাটোপে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগসর্বস্ব একঘেয়েমির জীবনে এবং ক্রেডিট কার্ডের সংসারে কিছুকালের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠেন শ্যামলী। বাবা সুধীর খাস্তগীরও চাননি ওই বৈভবপূর্ণ জীবনের মধ্যে থেকে তাঁর মেয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাক। শান্তিনিকেতনের শালবীথির মেয়ে শ্যামলীর কেবলই ওই সুখের জীবনকে দুর্বিষহ সোনার খাঁচা মনে হতে শুরু করে। তাঁর নিজের ভাষায় এ যেন “Living in a house of Credit Cards” এবং কোথাও কোথাও যেন সভ্যতার আলোকিত পর্দাটা একটু একটু তুলে ধরে সভ্যতার অন্ধকার দিকটাও দেখে ফেলেন শ্যামলী। সেখানে আলো নেই। আছে ক্ষমতার প্রদর্শন, ভোগবাদী নাগরিক সভ্যতার বিকট অট্টহাসি, যুদ্ধের মহড়া, আকাশ অন্ধকার করা যুদ্ধাস্ত্র, মাটি এবং জলকে বিষাক্ত করে তোলা বিকিরণ।
১৯৭৪ সালে সুধীর খাস্তগীর প্রয়াত হন। সেই বছরই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় রাজস্থানের পোখরানে। এ প্রসঙ্গে শ্যামলী লিখছেন, “১৯৭৪ সালে ভারত যখন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল তখন ঘুমটা গেল ভেঙে ...ওই সময় থেকেই যেখানে যা লেখা পেতাম পড়তে লাগলাম। পারমাণবিক অমানবিকতার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে জানতে এবং যুদ্ধ কেন, কেন অস্ত্রের পিছনে এত খরচ? লাতিন-আমেরিকার অভিজ্ঞতাও খানিকটা চিন্তার খোরাক জোগাল। তারপর কানাডা ফিরে নানান সভা ও শিক্ষামূলক আলোচনা ও প্রতিবাদের মারফৎ যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা ও পারমাণবিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্যের ভাণ্ডার বাড়তে লাগল; আলাপ হল অহিংস নীতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন নিজেদের জীবনেও ভয়ংকর সব যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদে; সেসব অভিজ্ঞতা দেশে ফিরে লিখতে শুরু করলাম ছোটো পত্রপত্রিকায়।”
কানাডায় থাকাকালীন সময়ে যখন মাঝে মাঝে দেশে ফিরতেন শ্যামলী, তখনই শ্যামলীকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন তাঁর জ্যাঠামশাই পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার রূপহীন, গন্ধহীন, নিঃশব্দ মারণ ক্ষমতার কথা শ্যামলী জানতে পারছিলেন এই সময়কাল থেকেই। এই সময় পর্বেই ভাঙ্কুভারে শেলী ডগলাস এবং জিম ডগলাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা Pacific Life Community-র পক্ষে যুদ্ধজাহাজ শিবিরের ফটক রোধ করে শ্যামলীরা বৃক্ষরোপণ করে প্রতিবাদে সামিল হন। ফলস্বরূপ কারাবরণ করতে হয় শ্যামলীদের। এই সময় পর্বেই যুদ্ধ বিরোধী আরও অনেকগুলি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন শ্যামলী, তারমধ্যে ‘Voice of Women’, ‘Canadian Coalition for Nuclear Responsibility’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
১৯৮১ সালের শেষের দিকে শ্যামলী পাকাপাকিভাবে চলে আসেন দেশে। তারপর আমৃত্যু শান্তিনিকেতনে তাঁর ‘পলাশ’ বাড়িটিই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। যদিও দেশে ফিরে শ্যামলীর কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি তাঁকে একজায়গায় বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ৮০ দশকের গোড়াতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গান্ধিবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনকারী শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্তের। ‘পলাশ’ বাড়িতেই জীবনের শেষ কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন পান্নালাল। পান্নালালের গ্রামীণ অর্থনীতি ভাবনার শরিক হয়ে বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন শ্যামলী। পান্নালালের সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং গ্রামীণ সভ্যতার পুনরুদ্ধারের কাজে, গ্রামে গ্রামে ‘মীনমঙ্গল’ উৎসবের প্রচলন, স্বনির্ভরতার শিক্ষাদান, দেশীয় প্রযুক্তি এবং শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ছোটো শিমূলিয়া ফার্মের কর্মকাণ্ড – সবেতেই শ্যামলী ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী।
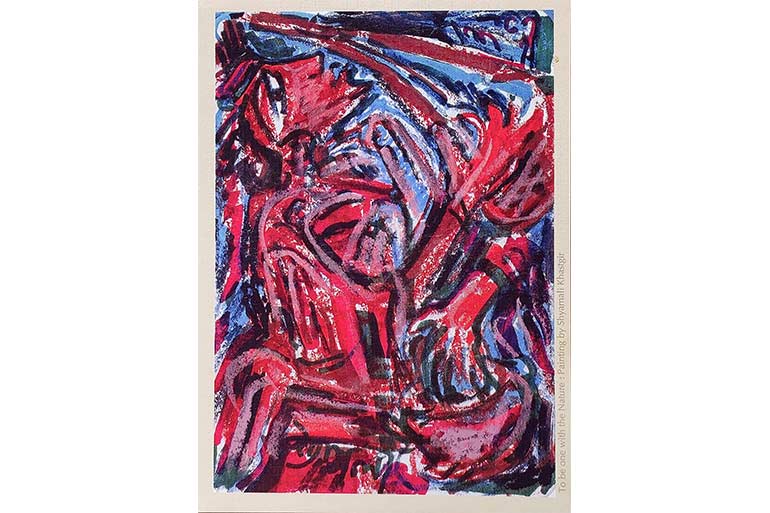
দেশে ফেরার পর থেকেই শ্যামলী নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন ‘অনুমুক্তি’ সংগঠনের সঙ্গে। ২০০০ সালের গোড়াতে অধুনা ঝাড়খণ্ডের পূর্ব-সিংভূম জেলার জাদুগোড়াতে ইউরেনিয়াম খনি অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভয়াবহ ফলাফলের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা চালিয়েছিলেন পদার্থবিদ সুরেন গাদেকর এবং ডাক্তার সঙ্ঘমিত্রা গাদেকর। সেই সমীক্ষায় অংশ নিতে শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে গিয়েছিলেন শ্যামলী। জাদুগোড়াতে UCIL এর খনি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং শ্রমিকদের পরিবারগুলিতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ক্যান্সার প্রভৃতি মারণ রোগ, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, গর্ভপাতের মতো ভয়াবহ ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে শ্যামলী স্লাইড- প্রোজেক্টারের মাধ্যমে তা সর্বত্র দেখাতেন এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতেন। শ্যামলী পুতুল গড়তেন। তাঁর বিখ্যাত ‘বসুন্ধরা’ পুতুলের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইতেন ভোগবাদী সভ্যতার সত্যিকারের স্বরূপ। শ্যামলীর রান্না ছিল তাঁর বিকল্প পথের সন্ধানী মনের পরিচায়ক, সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শনিবারের হাট, সে হাট আজ তার মূল থেকে সরে গিয়ে অন্যরূপ নিয়েছে। যে রূপকে মনেপ্রাণে ঘৃণাই করতেন শ্যামলী। তাঁর অবারিত দ্বার ‘পলাশ’ বাড়ির প্রাঙ্গণে পৃথিবীর কত দেশের, কত মানুষের পদধূলি যে পড়েছে – তার সঠিক কোনো হিসেব নেই।
শ্যামলী চলে গিয়েছেন ২০১১ সালের ১৫ অগাস্ট। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের অদূরে তাঁর পার্থিব দেহ মাটির বুকে মিশে গিয়েছে। মাটি ছিল তাঁর বড়ো প্রিয়। সেই মাটির কাছেই তিনি ফিরে গিয়েছেন। শ্যামলী বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ ভারতবর্ষই একদিন পৃথিবীকে পথ দেখাবে। তিনি তাই তাঁর ‘বিস্ফোরণের মাঝখানে’ বইটির উৎসর্গ পত্রে আশাবাদের সঙ্গে লেখেন, “এই বইটি উৎসর্গ করি এই ভারতের গ্রামের মানুষদের উদ্দেশ্যে আর শিশুদের যাতে তারা এই পৃথিবীকে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞানের নামে এই ধ্বংসাত্মক ভোগবাদী সমাজের অবসান ঘটুক -- অবসান ঘটুক পারমাণবিক উন্মাদনার, জীবনের জয়গান গেয়ে সবাই মিলে চেষ্টা করলে পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে না কি?”
































