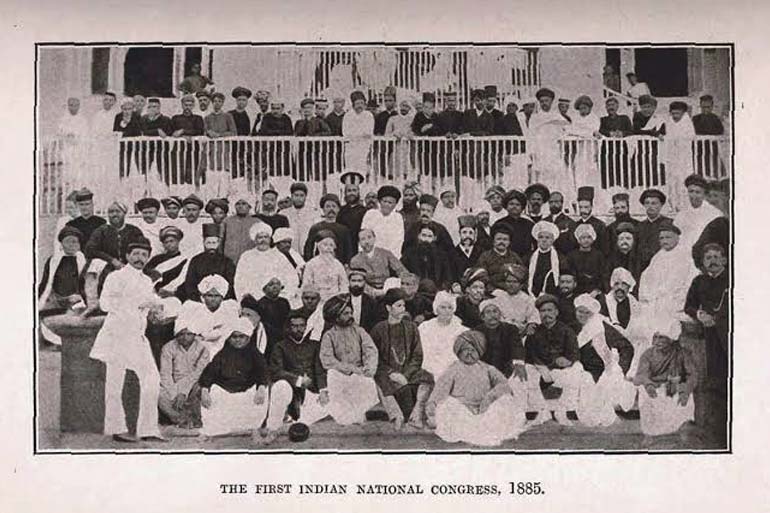যতদিন কাজের ধারা থাকবে, অবসাদ যেন না আসে : কয়েকটি মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ
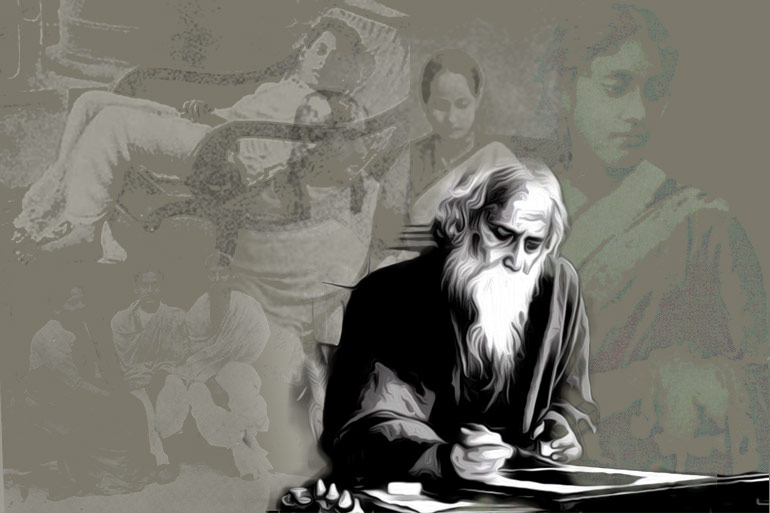
এমন এক অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি যে বারবার বলতে ইচ্ছে করছে, ‘এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়’। মৃত্যু মিছিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে। কী বিপুল শক্তিতে মৃত্যুর সঙ্গে বারবার দ্বৈরথে নেমে বলেছিলেন,
—‘দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি, শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।’
মাঝে মাঝে মনে হয় এই ‘মরণব্যথা’ সহ্য করে সৃজনে মগ্ন থাকাটা সত্যিই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। রবি ঠাকুর বারবার দাঁড়িয়েছেন সেই মৃত্যুর মুখোমুখি। সব আঘাত সহ্য করার পর তিনি সত্যিই মৃত্যুঞ্জয়। তাঁর মনের আকাশ থেকে যত প্রিয়জন তারার মতো খসে পড়েছে অকালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সযত্নে গেঁথে রেখেছেন নিজের সৃজনে। রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ কজনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ আজ আলোচনা করা যাক।
প্রথম যে মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে বিহ্বল করে দেয়, সে তাঁর মায়ের মৃত্যু। যে রাতে রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবীর মৃত্যু হয়, তখন ঠাকুরবাড়ি ঘুমন্ত। দাসির আর্তনাদকে আড়াল করেন কাদম্বরী। মায়ের মৃত্যুর ভয়াবহতা সেভাবে বোঝেননি রবীন্দ্রনাথ। শুধু সারদাদেবীকে নিয়ে সকলে যখন চলে গেল, তখন শোক এসে এক দমকায় বুকের ভিতর হাহাকার তুলল। মা যে এই বাড়ির এই দরজা দিয়ে আর একদিনও তাঁর এই চিরজীবনের ঘরকন্নার মধ্যে আপনার আসনটিতে এসে বসবেন না, এই ভাবনাটিই শোক হয়ে কষ্ট দিল রবিকে। এরপর এল রবির জীবনের গভীরতম শোক। তাঁর শৈশবের সাথী নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু। অভিমানী মেয়েটি লুকিয়ে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মনের খবর আর কেউ নেয়নি। শুধু কাদম্বরীর সব স্মৃতি, সব চিহ্ণ মুছে দেওয়া হয় ঠাকুরবাড়ির থেকে। কাদম্বরী শুধু রয়ে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুশোচনায় আর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীরে। নির্ঘুম রাতে রবীন্দ্রনাথ কাকে যে খুঁজে চলতেন অবিরাম! তার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ হঠাৎ মারা যান। রবীন্দ্রনাথ তখন কাদম্বরীর শোক থেকেই বেরোতে পারেননি। নিজেকে মগ্ন রেখেছেন সৃজনে—
‘দূর হতে কেন টানে
ব্যথা কেন বাজে প্রাণে
কাঁদায় কি ফল তবে, কাঁদিলে ফেরে না যদি কেহ।’
জীবনের স্রোত আবার রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সংসারে। মৃণালিনীর সঙ্গে নতুন সংসার জালে আবার আটকা পড়েছেন কবি। শিলাইদহ, জোড়াসাঁকো আর শান্তিনিকেতনে তাঁর ভরা সংসার। তিন মেয়ে — মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা আর দুই ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন একে একে। সব সন্তানকে মনের মতো করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। তাদের অন্তরে ভরাট করছেন মূল্যবোধ। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরির পরিকল্পনায় মৃণালিনীকে আন্তরিকভাবে পাশে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজে লেখক হিসেবে নামও ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার উপর বটবৃক্ষের মতো রয়েছেন বাবামশাই দেবেন্দ্রনাথ। ঠিক এইসময় আবার অতর্কিতে মৃত্যু এল।
প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথ চলে গেলেন ১৮৯৯ সালের ১৯ অগাস্ট, মাত্র ২৯ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথকে শক্ত হয়ে সব সামলাতে হল। এর মধ্যে খুব অল্পদিনের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা আর মেজোমেয়ে রেণুকার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন কবিপত্নী মৃণালিনী। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লালবাড়ির দোতলায় মৃণালিনীকে রাখা হল। বাড়িতে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অবিরাম তালপাতার বাতাস করে যেতেন মৃণালিনীকে। কিন্তু কোনো প্রার্থনা, কোনো নিরলস সেবা মৃণালিনীকে ফেরাতে পারল না। ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর মৃণালিনীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে পারলেন না। শুধু লিখলেন—
‘তোমার সংসার মাঝে, হায় তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন দুর্দিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?’
গভীর শোক! অথচ শান্ত, সমাহিত তার প্রকাশ ওয়আত্মসংবরণ। শুধু ‘স্মরণ’-এর কবিতায় নয়, মৃণালিনী রয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে। মৃত্যুর তাণ্ডব তখনও শেষ হয়নি। এবার মেজো মেয়ে রেণুকা অসুস্থ। কোনোভাবেই সুস্থ হতে পারছে না। রেণুকার যখন খুব বাড়াবাড়ি, রবীন্দ্রনাথ আলমোড়া গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। পথে লিখলেন ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি, লিখলেন—
‘জগৎপারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণদূত উড়িয়া চলে
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।’
কিন্তু মরণদূত এবার এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রেণুকাকে। যাবার ঠিক আগে রেণুকা বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিল, ‘বাবা ওঁ পিতা নোহসি বলো।’ রবীন্দ্রনাথ অসীম শক্তি সঞ্চয় করে বলেছিলেন সে মন্ত্র। ১৯০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রেণুকার মৃত্যু হয়।
রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেন গ্রন্থিমোচন পর্ব চলছিল। ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি গভীর রাতে চলে গেলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করছিলেন— ‘অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যের্মাহমৃতংগময়—’। প্রিয়পুত্রের কণ্ঠে এই মন্ত্র শুনে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল প্রশান্তি। হয়তো তাঁর পরলোক যাত্রার পথ সুগম হয়েছিল।  একলা মানুষ রবীন্দ্রনাথের নতুন পথ চলা শুরু হল। কাজের ভুবনে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়লেন রবি ঠাকুর। দুঃখ ভোলার এর চেয়ে বড়ো অবলম্বন আর কীই বা হতে পারে? এর মধ্যে ছোটোমেয়ে মীরার বিয়ে হয়েছে। ছোটোছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠিক যেন বাবার প্রতিকৃতি। তাকে ঘিরে মনটা আবার জড়িয়ে পড়ছিল স্নেহের বন্ধনে। কিন্তু কোনো বাঁধন যে রবীন্দ্রনাথের রইবে না! তাই যেন ১৯০৭-এর ২৪ নভেম্বর শমীন্দ্রনাথও আকস্মিক ভাবে হারিয়ে গেল না ফেরার দেশে। মুঙ্গেরে বন্ধুর মামারবাড়ি তাকে রেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজে গিয়েছিলেন কলকাতায় ছোটোমেয়ে মীরাকে দেখতে। সেখানেই খবর আসে, শমীর চলে যাওয়ার। মুঙ্গের গিয়ে শমীর সামনে এবার আর দাঁড়াতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। পাশের ঘরে বসেছিলেন। সৎকারের পর ফিরে যেতে যেতে দেখলেন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে , কোথাও কিছুর কম পড়েনি। সমস্তর মধ্যে সব রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন এই সমস্তর মধ্যে তিনিও রয়ে গেছেন। যতদিন তার কাজের ধারা থাকবে, ততদিন যেন অবসাদ না আসে— এই প্রার্থনাই করলেন সেদিন। নিজেকে নিজে দিলেন স্তোকবাক্য— ‘ঈশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা শিরোধার্য করিয়া লইব। আমি পরাভূত হইব না। ’
একলা মানুষ রবীন্দ্রনাথের নতুন পথ চলা শুরু হল। কাজের ভুবনে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়লেন রবি ঠাকুর। দুঃখ ভোলার এর চেয়ে বড়ো অবলম্বন আর কীই বা হতে পারে? এর মধ্যে ছোটোমেয়ে মীরার বিয়ে হয়েছে। ছোটোছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠিক যেন বাবার প্রতিকৃতি। তাকে ঘিরে মনটা আবার জড়িয়ে পড়ছিল স্নেহের বন্ধনে। কিন্তু কোনো বাঁধন যে রবীন্দ্রনাথের রইবে না! তাই যেন ১৯০৭-এর ২৪ নভেম্বর শমীন্দ্রনাথও আকস্মিক ভাবে হারিয়ে গেল না ফেরার দেশে। মুঙ্গেরে বন্ধুর মামারবাড়ি তাকে রেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজে গিয়েছিলেন কলকাতায় ছোটোমেয়ে মীরাকে দেখতে। সেখানেই খবর আসে, শমীর চলে যাওয়ার। মুঙ্গের গিয়ে শমীর সামনে এবার আর দাঁড়াতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। পাশের ঘরে বসেছিলেন। সৎকারের পর ফিরে যেতে যেতে দেখলেন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে , কোথাও কিছুর কম পড়েনি। সমস্তর মধ্যে সব রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন এই সমস্তর মধ্যে তিনিও রয়ে গেছেন। যতদিন তার কাজের ধারা থাকবে, ততদিন যেন অবসাদ না আসে— এই প্রার্থনাই করলেন সেদিন। নিজেকে নিজে দিলেন স্তোকবাক্য— ‘ঈশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা শিরোধার্য করিয়া লইব। আমি পরাভূত হইব না। ’
কিন্তু তাঁর জীবনের পায়ে পায়ে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে। শমীর মৃত্যুর ঠিক আগের মাসে চলে গেছেন প্রিয় বন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এরপর মাঝে এল প্রবল কর্মমুখর কিছু বছর। জীবনের গতিপথ বদলে গেল। ঘন ঘন বিলেত যাত্রা, নোবেল পুরস্কার, নতুন নতুন সাহিত্যসৃজন। ঠিক তারপরেই আবার এল মৃত্যু। ১৯১৮ সালের ১৬ মে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বড়ো আদরের মেয়ে মাধুরীলতাকে। রোজ মেয়েকে গল্প শোনাতে যেতেন রবি। সেদিন পথেই যখন খবর পেলেন মাধুরীলতার মৃত্যুর, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেলেন। মহাকাল কোন এক উল্লাসে টুকরো টুকরো করে দিল রবীন্দ্রনাথের সাজানো সংসার।
বন্ধু পরিজন যাকে চেয়েছেন, ভালোবেসেছেন অনেকেই চলে গিয়েছেন তাঁকে ছেড়ে। অথচ দীর্ঘজীবনে অবিরাম ফলের আশা না করে কর্মই তো করে গিয়েছেন তিনি। তারপর যখন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর মুখোমুখি, তখন তিনি সত্যিই মৃত্যুঞ্জয়। হয়তো শেষদিনে অস্ফুটে বলেছিলেন , ‘আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো’...
একথা তাঁকেই বলা মানায়।