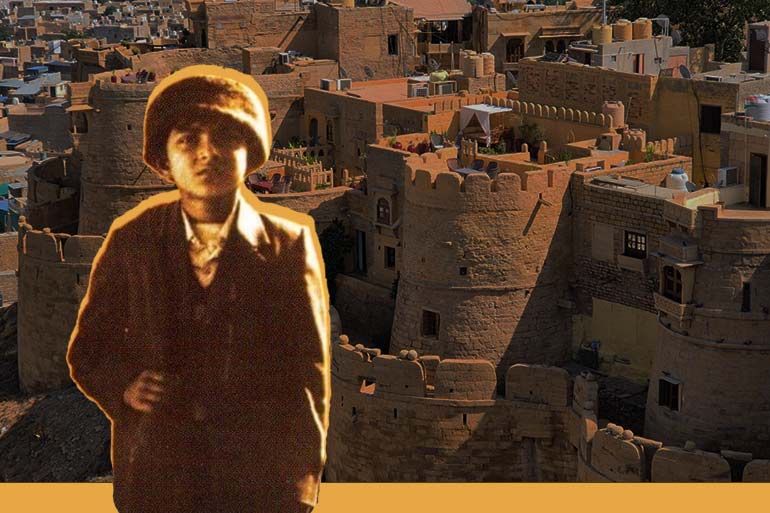তিলোত্তমার সবচেয়ে পুরোনো মহল্লা – শিয়ালদহ থেকে বৌবাজার

আজকের কলকাতা সফরে ইতিহাসের পাশাপাশি উপভোগ করবেন বর্তমানের রোমাঞ্চ। যাত্রা শুরু হবে শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে। অতীতে ফিরলে দেখা যায়, মহানগরীর সঙ্গে যেন সমান তালে বেড়ে উঠেছে এলাকাটি। শিয়ালদহ এক সময় ছিল শহর এবং সুন্দরবনের সীমানা। যার ওপারে ছিল লবণ হ্রদ, খাঁড়ি এবং ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে এখন ম্যানগ্রোভ অরণ্য কয়েকশো মাইল দূরে। শিয়ালদহ আজ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। চলুন এবার ভিড়ভাট্টার মধ্যেই হাঁটা শুরু করি –
শিয়ালদহ
‘শৃগাল’ বা ‘শিয়াল’ থেকে সম্ভবত জায়গার নামটি এসেছে। এক সময় তারা ঘুরে বেড়াত এই অঞ্চলে। ইতিহাসবিদ পি থাংকাপ্পন নায়ার লিখেছেন, প্রথম দিকে কলকাতা ছিল জলাভূমির ওপর কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। তাঁর মতে, ‘শিয়ালদহ’ নামটি এসেছে ‘শিয়ালডিহি’ থেকে। ‘ডিহি’ মানে গ্রাম। এখনকার কলকাতা আদতে পঞ্চান্নটি গ্রামের যোগফল। যাদের একসঙ্গে ‘ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম’ বলা হত। আজও ইএম বাইবাসের কাছে একটি জায়গার নাম পঞ্চান্নগ্রাম।
অনেক আগে শিয়ালদহ ছিল লবণ হ্রদে যাওয়ার প্রবেশপথ। ১৭৪২ সালে ‘মারহাট্টা ডিচ’ খনন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা বর্গি দস্যুদের আটকানো। কলকাতার বড়ো অংশ ঘিরে ফেলা হয় এই পরিখা দিয়ে। পরে আপার এবং লোয়ার সার্কুলার রোড (এখন এপিসি রোড এবং এজেসি রোড) বানানোর জন্য পরিখা ভরাট করতে হয়েছিল।
আরও পড়ুন: পুরোনো কলকাতার ‘নেটিভ’ প্রাসাদের বনেদিয়ানা
১৮৫৭ সালে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গকে রেলপথ দিয়ে যুক্ত করা হয় শিয়ালদহের মাধ্যমে। প্রথম রেললাইন চালু হয় পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া পর্যন্ত। ১৮৬২ সালে ক্যানিং বন্দরও জুড়ে যায়। পরিবহনের দায়িত্বে ছিল ক্যালকাটা অ্যান্ড সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েজ। এই মুহূর্তে এশিয়ার ব্যস্ততম রেল জংশন শিয়ালদহ। তবে ইতিহাসের চিহ্ন খুব অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। চার্চ অফ আওয়ার লেডি অফ ডলরস
চার্চ অফ আওয়ার লেডি অফ ডলরস
শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের একেবারে শুরুতে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে যান। কয়েকটা দোকান পেরোলেই চার্চ অফ আওয়ার লেডি অফ ডলরস। কয়েকটি নথিতে ভুল করে ‘চার্চ অফ দ্য লেডি অফ ডরিস’ লেখা আছে। অফিশিয়াল ঠিকানা ১৪৭, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কোলে মার্কেট। ভারতীয় খ্রিস্টান, বিশেষ করে গোয়ানদের জন্য ১৮০৯ সাল নাগাদ চার্চটি গড়ে ওঠে। অর্থ সাহায্য করেছিলেন গার্সিয়া এলিজাবেথ। চার্চের গঠন খুবই সাধারণ, তবে আকর্ষণীয়। এখনও প্রতি রবিবার প্রার্থনার জমায়েত হয়। বেদির বাঁ দিকে কুলুঙ্গিতে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সমাধি রয়েছে। দেখতে ভুলবেন না। বৈঠকখানা বাজার
বৈঠকখানা বাজার
পুরোনো এই বাজারের নাম ব্রিটিশরা উচ্চারণ করতেন ‘Bytaconnah’। ১৭৫৮ সালে বানানো ম্যাপে বাজারটির উল্লেখ রয়েছে। তবে নামের উৎস নিয়ে সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হয়নি আজও। কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী, ১৭৪০ সাল নাগাদ তৈরি হওয়া একটি বাংলোকে ঘিরে বাজার গড়ে ওঠে। আরেকটি মতে, সল্টলেক এবং সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো হতেন এক প্রাচীন বট গাছের নিচে। নিয়মিত ‘বৈঠক’ জমত। পুরোনো কলকাতার কিছু নথি থেকে জানা যায়, স্বয়ং জোব চার্নক হুঁকো নিয়ে বসতেন সেই গাছের তলায়। লোকজনের সঙ্গে আড্ডা মারতেন।
বাজারে পাওয়া যাওয়া বিচিত্র রকমের সামগ্রী। ইচ্ছে মতো সংগ্রহ করতে পারেন। এখানকার শুটকি মাছ বিখ্যাত।
 বৌবাজার স্ট্রিট
বৌবাজার স্ট্রিট
এই রাস্তা এখন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট নামে পরিচিত। ‘বৌবাজার’ নামটি সম্ভবত এসেছে ‘বহু বাজার’ থেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নামের উৎস হারিয়ে গিয়েছে। অনেকে মনে করেন, শোভারাম বসাকের পুত্রবধূর থেকেই ‘বৌ’ কথাটি এলাকার সঙ্গে জুড়েছে। এই রাস্তায় জগন্নাথের রথ চলত। আয়োজন করতেন শোভারাম। আবার কয়েকজনের মতে, নুনের গোলার দেওয়ান বিশ্বনাথ মতিলালের পুত্রবধূই ‘বৌ’ নামটির উৎস। ১৭৪৯ সাল নাগাদ গড়ে ওঠে রাস্তাটি। শিয়ালদহ থেকে সহজেই পৌঁছনো যায়। মাঝখানে পড়বে বসুমতী সাহিত্য মন্দির। জাঁকজমকে ভরা ইউরোপীয় এবং ভারতীয় স্থাপত্যের অদ্ভুত মিশ্রণ। ১৮৮১ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। সাপ্তাহিক বসুমতী এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকা এখান থেকেই বেরোত। হাঁটতে হাঁটতে তারপর আপনি একগুচ্ছ গয়নার দোকানের সামনে এসে পড়বেন। গয়নার বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। সামনের বড়ো রাস্তার নাম রিফিউজ লেন। সেখানে অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন কারখানায় বসে আছেন কারিগরেরা। আগুনের অল্প শিখা জ্বালিয়ে প্রাচীন কৌশলে বানিয়ে চলেছেন সোনার গয়না।
হাঁটতে হাঁটতে তারপর আপনি একগুচ্ছ গয়নার দোকানের সামনে এসে পড়বেন। গয়নার বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। সামনের বড়ো রাস্তার নাম রিফিউজ লেন। সেখানে অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন কারখানায় বসে আছেন কারিগরেরা। আগুনের অল্প শিখা জ্বালিয়ে প্রাচীন কৌশলে বানিয়ে চলেছেন সোনার গয়না।
বৌবাজার স্ট্রিট থেকে চলে যান মদন দত্ত লেনে। দেখতে পাবেন শীলদের দুটি জমকালো কিন্তু প্রায় ভেঙে পড়া অট্টালিকা। সম্ভবত উনিশ শতকের শুরু এবং মধ্যভাগে গড়ে উঠেছিল।
 চার্চ অফ সেন্ট জেভিয়ার’স, ভারত সভা, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি
চার্চ অফ সেন্ট জেভিয়ার’স, ভারত সভা, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি
গির্জাটি প্রাথমিকভাবে একটি উপাসনাঘর হিসেবে গড়ে ওঠে ১৮৮১ সালে। পরে ভূমিকম্পের কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন সেন্ট জেভিয়ার’স চার্চ নির্মিত হয় ১৮৯৮ সালে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর্চবিশপ পল গোথাল। গির্জার প্রধান আকর্ষণ রয়েছে হলের পেছনে একটি ফলকে। তাতে লেখা, মার্কুইস অফ রিপন (১৮৮০-৮৪ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল) ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। অ্যাংলিকান চার্চ অফ ইংল্যান্ড ছেড়ে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের অনেকেই অসন্তুষ্ট হন এই ঘটনায়। খানিকটা এগোলেই ভারত সভা ভবন। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গড়ে উঠেছিল ১৮৭৬ সালে। এই বাড়িতেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ঘোষ বক্তৃতা দিতেন পার্টিকর্মীদের সামনে। আন্দোলনের পরিকল্পনা করতেন। বাড়ির সামনে মার্বেল ফলকে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাণী লেখা রয়েছে।
খানিকটা এগোলেই ভারত সভা ভবন। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গড়ে উঠেছিল ১৮৭৬ সালে। এই বাড়িতেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ঘোষ বক্তৃতা দিতেন পার্টিকর্মীদের সামনে। আন্দোলনের পরিকল্পনা করতেন। বাড়ির সামনে মার্বেল ফলকে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাণী লেখা রয়েছে। ভারত সভা ভবনের ঠিক উল্টোদিকে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। সামনের ফলকে বলা আছে, ৯০৫ বঙ্গাব্দ নাগাদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই অনুযায়ী প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো মন্দির এটি। তবে ‘ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি’ নামটি ব্রিটিশ যুগের। যখন প্রচুর ইউরোপিয়ান যাতায়াত করতেন কলকাতায়। স্থানীয় লোকেরা ইউরোপীয়দের ডাকতেন ফিরিঙ্গি বলে। আরেকটি প্রচলিত গল্প, আন্তোনিও কাবরাল বা অ্যান্টনি কবিয়ালের স্মৃতিতে মন্দিরের এমন নাম। আদতে পর্তুগিজ অ্যান্টনি বাংলা কবিগানের জন্য বিখ্যাত হন ১৮ শতকে। দেবী কালীর পরম ভক্ত ছিলেন তিনি।
ভারত সভা ভবনের ঠিক উল্টোদিকে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। সামনের ফলকে বলা আছে, ৯০৫ বঙ্গাব্দ নাগাদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই অনুযায়ী প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো মন্দির এটি। তবে ‘ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি’ নামটি ব্রিটিশ যুগের। যখন প্রচুর ইউরোপিয়ান যাতায়াত করতেন কলকাতায়। স্থানীয় লোকেরা ইউরোপীয়দের ডাকতেন ফিরিঙ্গি বলে। আরেকটি প্রচলিত গল্প, আন্তোনিও কাবরাল বা অ্যান্টনি কবিয়ালের স্মৃতিতে মন্দিরের এমন নাম। আদতে পর্তুগিজ অ্যান্টনি বাংলা কবিগানের জন্য বিখ্যাত হন ১৮ শতকে। দেবী কালীর পরম ভক্ত ছিলেন তিনি। মেটকাফ স্ট্রিট
মেটকাফ স্ট্রিট
সফরের একেবারে শেষে ঢুঁ মারুন কেরি ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চে। প্রখ্যাত ভারতবিদ এবং সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম কেরির নামে এই গির্জা। ১৭৯০ সালে ধর্মপ্রচারের কাজে ভারতে আসেন। সাধারণ মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করার জন্য উৎসর্গ করেন নিজের জীবন। ১৮০১ সালে বাইবেল অনুবাদ করেন বাংলায়। প্রথম বাংলা খবরের কাগজ ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশ শুরু করেন। শ্রীরামপুরে তাঁর ছাপাখানায় চালু হয় বাংলা ব্লক প্রিন্ট। তাঁর উদ্যোগেই ১৮২০ সালে যাত্রা শুরু করে রয়্যাল এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি। যা আজও পুরোদমে চলছে।
আরও পড়ুন: কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো রাস্তার গল্প
মিশন চার্চ থেকে বেরিয়ে ঘুরুন বাঁ দিকে। মেটকাফ স্ট্রিটে দেখতে পাবেন আগা খানের বাড়ি। ইসলাম ধর্মের ইসমাইলি শাখার প্রধান ব্যক্তিত্ব। ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে পার্সিদের অগ্নিমন্দির। আঞ্জুমান জরাস্ট্রিয়ান আতিশ আদারান নামে যা পরিচিত। কলকাতার চারটি অগ্নিমন্দিরের মধ্যে এটি অন্যতম।
পরের সপ্তাহে আমরা যাব শহরের ঠিক মাঝখানে – সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। আজকের যাত্রা শুভ হোক।