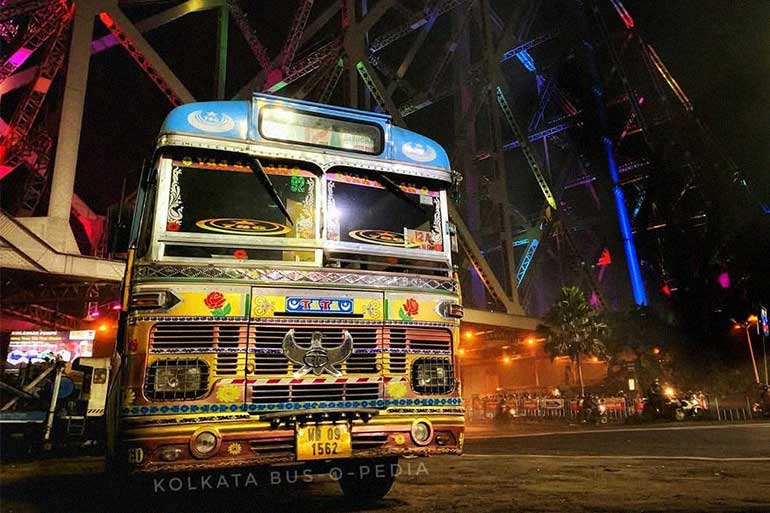সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল, নানান কারুকার্যের মধ্যে গমগম করছে যামিনী রায়ের আঁকা যিশু

আগামীকাল বড়োদিন। কলকাতার গির্জায় গির্জায় ভিড় জমাবেন নানা ধর্ম নির্বিশেষে অনেক মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকেই যাবেন সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল গির্জায়। অনেকে প্রাণ ভরে দেখবেন যিশুর অর্চনা আবার অনেকে হয়তো মন দিয়ে দেখবেন গির্জার নানা শিল্প সৌকর্য। সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল গির্জায় রয়েছে যামিনী রায়ের আঁকা একটি ছবি, ‘লাস্ট সাপার’। একটি বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি ছবি এঁকেছিলেন যামিনী রায়। সেটি কোনো একদিনের ইতিহাস নয়। সেই ইতিহাসকে দেখতে গেলে আমাদের বড়োদিনের প্রাক্কালেই ফিরে তাকাতে হবে এক সুদূর অতীতের দিকে।
কলকাতার উপনিবেশে তখন রোজই জাহাজ লাগার ধুম। ইংল্যান্ড থেকে লোকজন তো আসছেই, সঙ্গে আসছে আরও হরেক প্রকার জিনিসপত্র। তার মধ্যে আছে লর্ড, ব্যারনদের মূর্তি, যা বসবে কলকাতার চার রাস্তার মাঝে। আসছে তৈলচিত্র, বাগানে বসানোর জন্যে ফোয়ারার পাথর শিল্প, ভেনাসের মূর্তি সঙ্গে আরও কত কী। আর নয়ই বা কেন? আসলে ততদিনে কলকাতাকে দ্বিতীয় লন্ডনে রূপান্তর করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই কলকাতারও অনেক কিছু দরকার। যেমন গঙ্গার কাছে ‘এসপ্ল্যানেড’ নামক একটি চত্বর দরকার যেখানে চারদিক থেকে সব রাস্তা এসে মিলবে। এবং সেখানে খোলা জায়গায় পসরাও কেনা বেচা করা যাবে। তাছাড়া কলকাতার ঘরবাড়ির নকশা হতে হবে এমন, যাতে ইংল্যান্ডের প্রাসাদপোম বাড়িগুলির ছায়া অনুভব করা যায়। আর সর্বোপরি কলকাতার চাই গির্জা। নইলে ধর্মপ্রাণ সাহেবগুলোর তো এদেশে থাকাই দুষ্কর। সেই মতোই একে একে গির্জা তৈরির ধুম লাগলো শহরে। দেখা গেল ময়দানের কাছে জঙ্গল ঝেড়ে মুছে শুরু হল এক গির্জা নির্মাণের কাজ। সেটা ১৮৩৯। একটি চোখ জুড়ানো গির্জা পেল কলকাতা। গথিক রিভাইভ্যাল শৈলীতে তৈরি। গির্জাতে বসল স্টেইন্ড গ্লাসের জানালা, গির্জার দেওয়ালে লাগল ফ্লোরেন্স শৈলীর ভিত্তি চিত্র। শুধু কী তাই, সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার মেজর উইলিয়াম নৈর্ন ফর্বস নরউইচ ক্যাথিড্রালের শিখর ও চূড়ার মতো করে গড়ে দিলেন ক্যাথিড্রালের চুড়ো। সঙ্গে রইলেন সি.কে.রবিনসন। কিন্তু ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে এমন চমৎকার নিদর্শন পড়লো ভেঙে। শুধু সাহেবদেরই নয় মন খারাপ হল কলকাতারও। আবার শুরু হল তোড়জোড়। আর তখনই দেখা গেল যে, ক্যানটারবেরি ক্যাথিড্রালের বেল হারি টাওয়ারের মতো করে আবার তৈরি হল সেন্টপলস-এর চুড়ো।
সেই থেকে চলছে। কিন্তু এরই মধ্যে বাঙালি, কলকাতা ও ভারতবর্ষ সব জুড়ে গেল চার্চের সঙ্গে। যার খোঁজ আমাদের রাখা হয় না। এই চার্চের সঙ্গে বাঙালির হৃদয়, মনন জুড়ে দিলেন যিনি তিনি একজন চিত্রশিল্পী। নিজেকে পটুয়া বলতে ভালবাসতেন। নাম যামিনী রায়। ফলে মানেটা যা দাঁড়ালো তা অনেকটা এরকম। এই গির্জার পূর্ব দিকে যে স্টেইন্ডগ্লাস পেন্টিং বসানো রয়েছে সেটি মূলত তৈরি হয়েছিল উইন্ডসরের সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলের জন্যে। রাজা তৃতীয় জর্জের নির্দেশে সেটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়কার বিশপ বলে কয়ে ছবিটিকে নিয়ে আসলেন কলকাতায়। মহারানি ভিক্টোরিয়া এই গির্জার সার্ভিসের জন্যে পাঠালেন রুপোর প্লেট। এসবের মাঝেই গমগম করছে যামিনী রায় অঙ্কিত লাস্ট সাপার।
 সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল, কলকাতা
সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল, কলকাতা
সেটা ষাট-সত্তরের দশক। বাংলা তখন একদিকে আটটা ন’টার সূর্যের আলোর খোঁজে যেমন উত্তাল অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে চলেছে দেশ। এদেশের মানুষ তত দিনে প্রভু যিশুর মধ্যে নিজেদের প্রাণের মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। কারণ এদেশের জনগণ তত দিনে জেনেছেন যিশু রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন, আবার ইনি দরিদ্র মানুষের মধ্যে রুটি বিলি করেন। এমন মানুষই তো তাঁদের প্রাণের মানুষ হবেন। এরকম অবস্থায় বিশপ এইচ লাকদাসা জে ডেল মেল চাইলেন উপাসনার নিয়ম কানুনে ভারতীয় ভাবধারা আনতে। বাঙালি শিল্পীদের কথাও ভাবলেন গির্জার ছবির জন্যে। সেই ভাবনা থেকেই যামিনী রায়ের সঙ্গে নিরন্তর কথা বললেন বিশপ। আর সেই সূত্রেই যামিনী রায় এই গির্জার জন্যে আঁকলেন লাস্ট সাপার। বাঙালি সেদিন একাধিক রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে লাস্টসাপার ছবিটিকে মিলিয়ে নিয়েছিল। কারণ নৈশভোজের গল্পের মধ্যেই রয়েছে যিশুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনির ইঙ্গিত।
ছবিসূত্রঃ যামিনী রায়, ডঃ সঞ্জয় কুমার মল্লিক
প্রকাশকঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারুকলা পর্ষদ