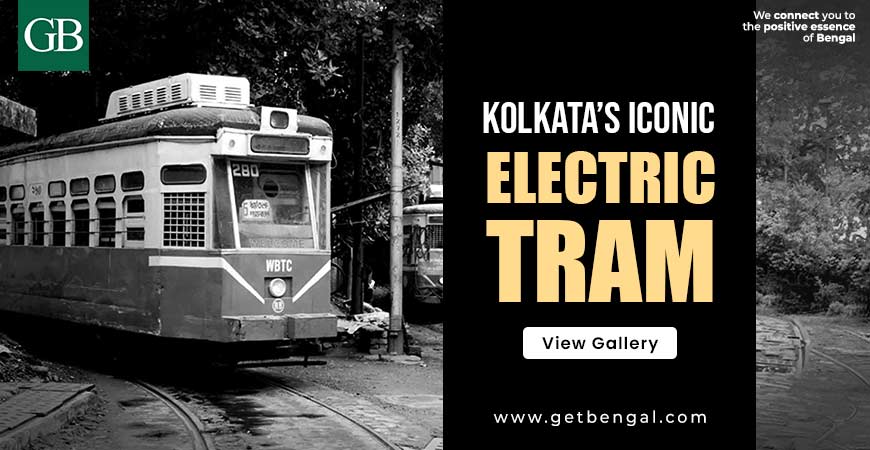মায়ানগর/ ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা : একটি শহর যেন বিষম পাথর হয়ে আছে
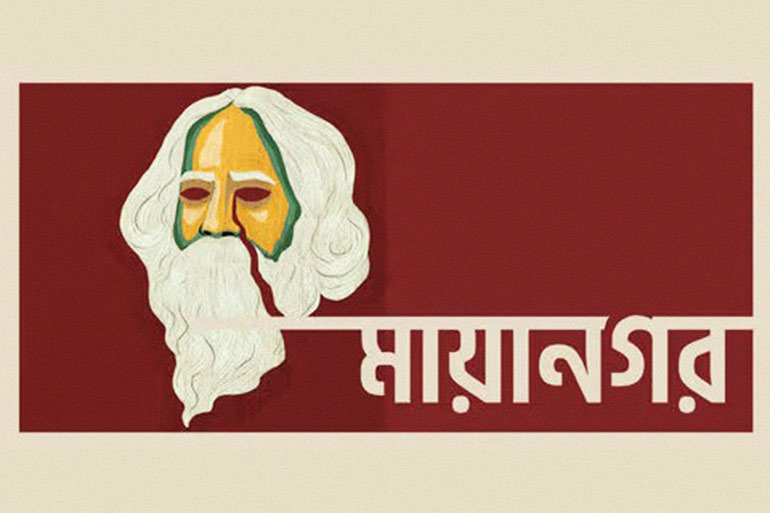
১)
“কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—”
‘স্মৃতির শহর’-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একসময় লিখেছিলেন এ কবিতা। আসলে স্মৃতি সততই উস্কানিমূলক। বলে পিছন ফিরে তাকাও। তাকালে যদি ভালো কিছু মনে না পড়ে? যদি খারাপটাই বারবার স্মৃতিদগ্ধ করে। তাই স্মৃতিদের বিস্মৃতি হতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু তবুও কেউ কেউ থেকে যান মাঝসমুদ্রের নাবিকের মতো। যিনি সমস্তটা দ্যাখেন। তারপর একসময় তাঁর স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসে এ জীবদ্দশার পাল্টে যাওয়া। দেখা যায় দুর্নীতি, বিকৃতি, দূষণ আর পচনশীল পাহাড়ের সারি সারি দৃশ্য।
মাঝ সমুদ্রের সেই নাবিকের নাম আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত (Aditya Vikram Sengupta)। সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রে যিনি ফাগুন এনেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক সংযোজন মায়ানগর, যার পূর্ব নাম ছিল ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা (Mayanagar / Once Upon a Time in Calcutta)। তিলোত্তমার ক্রমশ বদলে যাওয়ার গা শিরশিরানি তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। দেখা যাচ্ছে, এ শহরের প্রায় প্রত্যেকেই এই পচনশীল সমাজব্যবস্থার অংশ। ব্যতিক্রমী শুধু এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ, শিশির। তার সম্বল বলতে একটি অবলা প্রাণী। কেন যে তার বাচ্চা হচ্ছে না, এই দুশ্চিন্তায় তিনি জর্জরিত। তিনিই একমাত্র শান্তির ঘুম ঘুমান।

এ শহরের ল্যান্ডমার্ক বলতে যা কিছু বোঝানো হয়, সবই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে পোস্তা ব্রিজ, ভেঙে যাচ্ছে সায়েন্স সিটির সামনে বসানো ডাইনোসর, উবে যাচ্ছে সার্কারিনা থিয়েটার, নতুন শহর হয়ে উঠছে রাজারহাট-নিউটাউন। শহরে ব্যস্ততা বাড়ছে। আর ক্রমশ মানুষ একা হতে হতে আরও গভীর একা হয়ে পড়ছে। দুর্নীতির জাঁতাকলে কেমন যেন সকলেই আটকে৷ কেউ কাউকে দু-ইঞ্চি ছেড়ে কথা বলবে না।
‘মায়ানগর’ ছবিতে প্রধান চরিত্র এলা। মধ্যবিত্ত পরিবারে বাস। স্বপ্ন দ্যাখে গগনচুম্বী অট্টালিকার। মেয়ে মারা যাবার পর ঠিক করে স্বামী শিশিরের সঙ্গে আর থাকবে না। না, ওসব রোজকার অশান্তি টশান্তি নেই। মনের মিল না থাকলে এক ছাদের তলায় থাকাটা বড্ড মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এলা ফ্ল্যাট কেনার জন্য লোন নিতে পারে না৷ শরিকি দাদাকে বলে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না৷ আগে টুকটাক অভিনয় করত, এখন টিভিতে সঞ্চালনা করে। ভাগ্য ফেরানোর অনুষ্ঠান। ওই টিভি স্টুডিওতেও আবার দুর্নীতি। মশার কামড়ের দুর্নীতি। বসের সঙ্গে এলার একটা ভাব-ভালোবাসা হয়। মনের নয়, শরীরের। আশার নয়, আকাঙ্খার। স্বপ্নের নয়, লোভের। অট্টালিকা পাবার লোভ। পায়ও। তবে শহরের বাইরে। ঠিকানা কলকাতা। কিন্তু সে জোর করে টানাহেঁচড়ার কলকাতা। এমন কলকাতা যে একটা ওলাও বাড়ির দুয়ার অবধি পৌঁছায় না।
আদিত্য বিক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রধান চরিত্র এলাকে দেখান পাড়ার এক কোণে পড়ে থাকা ‘Use Me’-র মতো। অথচ সে আগলে রেখেছে হাজার যন্ত্রণা। মাকে ছোটোবেলায় না পাওয়ার যন্ত্রণা। এমনকি নিজের মেয়ে হারানোর যন্ত্রণা।
২)
“আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে—”
সাউন্ড ডিজাইন এবং অ্যাস্থেটিক সেন্সের বাইরেও এই ছবি সরাসরি এবং সংলাপ প্রধান। যা আদিত্যর আগের দুটি কাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছবিতে ব্যবহৃত ডাইনোসরটি আসলে সভ্য সমাজকে দিকনির্দেশ করে। এই ‘সভ্য সমাজ’ যেন ডাইনোসর যুগের মতো আজ অতীত হয়ে গেছে৷ ছবিতে অসাধারণ একটি চরিত্র আছে, বুবুদা। যিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া থিয়েটারকে আগলে রাখেন আজও। প্রধান চরিত্র এলার দাদা। তবে নিজের নয়। ইলার বাবার আরেক সম্পর্কের ছেলে। বুবুদা বন্ধ হয়ে যাওয়া সমাজব্যবস্থার ভূত। মৃতপ্রায় এই মানুষটি বাড়ি আগলে বসে থাকে একা। একটা সময় আসে, যখন সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো কাজের লোকটিকে বিষাক্ত মনে হয়।

সাউন্ড ডিজাইন এবং অ্যাস্থেটিক সেন্সের বাইরেও এই ছবি সরাসরি এবং সংলাপ প্রধান। যা আদিত্যর আগের দুটি কাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছবিতে ব্যবহৃত ডাইনোসরটি আসলে সভ্য সমাজকে দিকনির্দেশ করে। এই ‘সভ্য সমাজ’ যেন ডাইনোসর যুগের মতো আজ অতীত হয়ে গেছে৷
ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে রবীন্দ্রনাথের গান (Rabindra Sangeet)৷ সে গান যেন পরিবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ৷ একটি ছোট্ট দৃশ্যে দেখানো হয় এক বাচ্চা মেয়ে রবীন্দ্রনাথের রিমিক্স গানে নাচছে। আসলে তার পরিবার বা সমাজ তাকে শেখাতে পারেনি যে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল। হিন্দি-ভোজপুরিঘেঁষা উত্তেজনামূলক হাই রিদমের রবীন্দ্রসংগীতে বাচ্চাটির মন গেছে। পুরো ছবিতেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আছেন। যেভাবে থাকেন বাঙালির মননে৷ শহরের মেজাজ পাল্টায়, কিন্তু বাঙালির রক্ষাকবচ হয়ে, নিদেনপক্ষে দেওয়ালে টাঙানো ফুলের মালা সজ্জিত ‘ঠাকুর’ হয়েও। তাই ইলার অফিসে পার্টির দিন ‘আলোকেরই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও’ বাজে, রিমিক্সে। পাশের পাড়ার গলি থেকেও শোনা যায়, রিমিক্স। বাচ্চা মেয়েটি নাচে, রিমিক্স গানে৷ কিন্তু সমাজব্যবস্থা (পড়ুন ফ্লাইওভার) যখন ভেঙে পড়ে, বাঙালির উপর যখন বলপূর্বক রবীন্দ্রচেতনা বৃদ্ধি করতে চায় রাষ্ট্র, তখন রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপিয়ে পড়েন এই সভ্যতার কাঠামোর উপর। শয়ে শয়ে মানুষ মারা যায়। এলার বস দুর্ঘটনায় মারা যায়৷ এলার শয্যাসঙ্গী একজন ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এলা সব টিভিতে দ্যাখে। এলা হাসে। এলা প্রবল হাসে। সে আরও আরও একা হয়ে যায়।

তাকে আবার ফিরে আসতে হয় ফেলে আসা স্বামীর কাছে। ইলার পা টলমল। নকলের স্বপ্ন দেখা ইলা আসলে ফিরে আসে আসলের কাছে। এ-ও এক রূপক। যেমন রূপক, এলা অট্টালিকা পাবার লোভে বসের সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হয়; অন্যদিকে দেখা যায় দুই কুকুরের মিলন। মানুষ বনাম পশুর যৌনতা। কিংবা যৌন আবেদনের লড়াই।
৩)
“আশ্চর্য ক্রেন ছিঁড়ে খাচ্ছে শহরের শিরা-উপশিরা
গল গল করে বয়ে যাচ্ছে, জমে থাকছে শহরের রক্ত—”
এত দুর্নীতি, বিকৃতি আর সামাজিক ক্ষয়ের মধ্যে আদিত্য বিক্রম একটি চমৎকার প্রেম দেখিয়েছেন। রাজা আর পিংকি। কিন্তু সেই প্রেমের শেষটাও অত্যন্ত মর্মান্তিক। তারা পালাতে চায়। অথচ পিংকি প্রেমিকের কথা রাখতে পারে না শেষবেলায়। রাজা তার সমস্ত সাম্রাজ্য হারিয়ে একা একা লোকাল ট্রেনে চলে যায় নিরুদ্দেশে। কী চমৎকারভাবে তাদের চরিত্রায়ণ করেছেন পরিচালক। যেন পাঁকের মধ্যে ফুটে ওঠা পদ্ম।

ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে রবীন্দ্রনাথের গান৷ সে গান যেন পরিবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ৷ একটি ছোট্ট দৃশ্যে দেখানো হয় এক বাচ্চা মেয়ে রবীন্দ্রনাথের রিমিক্স গানে নাচছে। আসলে তার পরিবার বা সমাজ তাকে শেখাতে পারেনি যে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল।
সকল অভিনেতাই ভীষণ দৃপ্ত। তবে এই ছবিতে দর্শক আবিষ্কার করবেন শ্রীলেখা মিত্রের (Sreelekha Mitra) অভিনয়। প্রতিটি দৃশ্য যেন তিনি অনুভব করেছেন। মেয়ের অস্থি বিসর্জনের পর তিনি যখন বাড়ি ফিরে বিছানায় বসছেন মদের গেলাস হাতে নিয়ে, সেই দৃশ্যে কী পরিমিত অভিনয় করেছেন শ্রীলেখা। কিংবা যখন হঠাৎ ভাস্করদার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একটা শপিং মলে, যে সামান্য ‘গায়ে পড়া’ সুলভ আচরণ তিনি অভিনয়ে এনেছেন, তা যথাযথ। এছাড়াও বুবুদার চরিত্রে ব্রাত্য বসু (Bratya Basu), শিশিরের চরিত্রে সত্রাজিৎ সরকার, রাজার চরিত্রে শায়ক রায়, পিংকির চরিত্রে ঋত্বিকা নন্দিনী শিমু, বুবুর বাড়ির কর্মচারীর চরিত্রে ত্রিদিব সেনগুপ্ত, কল্পতরু কোম্পানির প্রধানের চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী, ভাস্করের চরিত্রে অরিন্দম ঘোষ প্রত্যেকেই অসামান্য অভিনয় করেছেন। অসামান্য চিত্রগ্রহণ করেছেন পাম ডি’ওর বিজয়ী তুরস্কের গোখান তিরিয়াকি (Gökhan Tiryaki)। অত্যাশ্চর্য সংগীত পরিচালনা করেছেন ডাচ সুরকার মিনকো এগার্সম্যান (Minco Eggersman)। প্রযোজনা করেছে আদিত্য-জোনাকির ‘ফর ফিল্মস’ এবং ফ্রান্স ও নরওয়ের দুটি প্রযোজনা সংস্থা। পরিবেশনায় এসভিএফ।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে (Venice Film Festival) এ ছবি পাড়ি দেওয়াকালীন আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, “এই ছবিটি কলকাতা শহর এবং শহরের মানুষের জন্য ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং আবেগের সমাপ্তি। বিশেষত দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বের দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করছে। সত্যিকারের চরিত্র এবং বাস্তব ঘটনাবলী যা আমার অতীতের ‘কমিউনিস্ট’ শহরের বিভিন্ন স্তরকে দেখানো হয়েছে, যা হয়তো কিছু মাত্রায় বেদনাদায়ক, কিন্তু তবুও তাতে আশা এবং আনন্দ ছিল। ফিল্মটি বিস্তৃত মহানগরীতে শ্বাস নিতে-নিতে হাঁপাতে থাকা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে তুলে ধরে।”
আদিত্যর কথামতো প্রতিটি চরিত্রই সত্যিকারের। ছবিতে ব্যবহৃত বন্ধ হয়ে যাওয়া থিয়েটার আসলে সার্কারিনা থিয়েটারের ভগ্নদশা, যার মালিক অমর ঘোষের ছেলে এবং সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্রাত্য বসু (বুবুদা)।
ছবিতে এলা বারবার তার মায়ের কথা বলে। বেশ কয়েকটি সংলাপে উঠে এসেছে তার মা একজন ক্যাবারে ডান্সার ছিলেন। রাতের পর রাত বাইরে থাকতেন। আসলে তাঁর নাম মিস শেফালি (Miss Shefali)। সে যুগের সবচেয়ে রহস্যময় চরিত্র। তাঁর মেয়ে এলা অর্থাৎ শ্রীলেখা মিত্র।
ইতিহাস বলে সার্কারিনা থিয়েটারের (Sarkarina Theatre) মালিক অমর ঘোষের সঙ্গে মিস শেফালির একধরনের বিবাহ বহির্ভুত প্রেম হয়। যার পরিণতিও হয় ভয়ংকর। এই ছবিতে উঠে এসেছে স্বর্ণযুগের সেই ইতিহাস।
৪)
“রেশমি সূর্যের প্যারাসুটে ঝুলে
একদিন ঈশ্বর নেমে আসবেন কলকাতায়—”
আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তের ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা (মায়ানগর) আসলে কলকাতা শহরের পোস্টমর্টেম। কিন্তু পোস্টমর্টেম হলেও এই শহরের মৃত্যু নেই। দুর্নীতি, বিকৃতি, মতলব, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদ সবকিছু পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হয়তো এ শহর এমনই থাকবে। হয়তো এটাই শহরের বৈশিষ্ট্য। এক থিয়েটার হল বন্ধ হলে আরেক থিয়েটার হল গড়ে উঠবে, একটা ব্রিজ ভাঙলে আরেকটা ব্রিজ নির্মিত হবে, এক সম্পর্ক ভাঙলে আরেক সম্পর্ক প্রাণ পাবে।

অসামান্য সব দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। থিয়েটার হলের লং শট, কন্সট্রাকশন কর্মীদের গাড়ির শট এবং সেখানে বিরহের সুর মন মাতিয়ে দিয়েছে।
‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা’-য় আদিত্য নিজেকে ভেঙেছেন। ‘আসা যাওয়ার মাঝে’ এবং ‘জোনাকি’ কিছুটা সমগোত্রীয় ছবি। সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে আদিত্য বাংলা ছবির দুর্দিনে পরম যত্ন নিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন এই ছবি। স্লো মোশন এনেছেন, দেওয়ালের রঙের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চরিত্রদের পোশাকের রং পরিকল্পনা করেছেন, সংলাপ বাড়িয়েছেন।
আমাদের কলকাতার কি সব ঐতিহ্যই শেষ হয়ে এল? হয়তো না। হয়তো শেষের পরেও থাকে শুভ সকালের ইঙ্গিত। তার জন্য চাই অক্ষয় অপেক্ষা।
*মতামত লেখকের নিজস্ব