নেতাজির নির্দেশে ‘চাকরি’ গেল শিবরামের
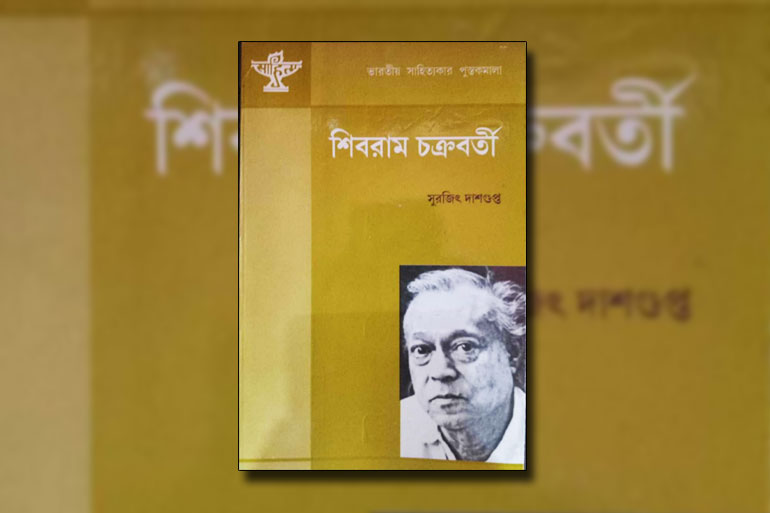
শিবরাম চক্রবর্তী একটি গল্প শুরু করেছিলেন এইভাবে। একজনের তিন কাকা। তাদের নাম, কুঞ্জকাকা, নিকুঞ্জকাকা এবং কুঞ্জরকাকা। তারপরই বলে দেওয়া হয়েছে, কুঞ্জরকাকা কিন্তু কুঞ্জকাকার কাকা নয়, ওনার নামই কুঞ্জরকাকা। এই গল্পে সম্ভবত শিবরামের বাবা, মা, ভাইদের নামের প্রভাব পড়েছে। কারণটা বলা যাক। শিবরামের বাবার নাম ছিল শিবপ্রসাদ। মা, শিবরানি। তিন ভাই, শিবরাম, শিবসত্য এবং শিবহরি। শিবহরি অবশ্য খুব কম বয়সে মারা যান। ঠিক যেন কুঞ্জ, নিকুঞ্জ আর কুঞ্জর।
শিবরাম কবে জন্মেছেন? তিনি নিজে কখনও বলতেন, সিপাই বিদ্রোহের সময়। কখনও বলতেন, যে বছর প্রথম ট্রাম চলেছিল কলকাতায়, সেই বছর। আবার কখনও বলতেন, তিনি জসীমউদ্দীনের সমবয়সী, কখনও আবার বলতেন, তাঁর আর প্রেমেন মিত্রের জন্ম একই বছরে। যদিও সুরজিৎ দাশগুপ্ত শিবরামের যে জীবনী লিখেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন, শিবরামের জন্ম ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। কলকাতার দর্জিপাড়ায়, নয়নচাঁদ দত্ত লেনে, দাদামশাইয়ের বাড়িতে। বইটি ছেপেছে সাহিত্য অকাদেমি। দাম, ৫০ টাকা।
শিবরামের বাবা ছিলেন মালদহের চাঁচলের রাজ পরিবারের সন্তান। জন্মের পর কিছু দিন কলকাতায় কাটিয়ে এক ভাইয়ের মৃত্যুর পর শিবরামরা সপরিবারে চলে আসেন চাঁচলের রাজবাটিতে। এই বাড়িতেই এস্টেটের ডাক্তার হিসেবে সপরিবারে থাকতেন। ডাক্তারের মেয়ে রিনি ছিল শিবরামের সমবয়সী। রিনিই শিবরামের প্রথম প্রেম। কিশোরী রিনি যখন বাবার সঙ্গে চাঁচল ছেড়ে কলকাতায় চলে এল, তার কিছুদিন পরে শিবরাম এন্ট্রান্স পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষায় পাস করেন। ওই সময় মালদহে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারে। শিবরাম দেশবন্ধুর সভায় ছিলেন ভলান্টিয়ার হিসেবে। এবং পরদিনই দেশবন্ধুর সঙ্গে দেশের কাজ করবেন বলে কলকাতা চলে এলেন শিবরাম। যদিও লেখক সুরজিৎ দাশগুপ্তর মতে, হয়তো তিনি এসেছিলেন রিনির খোঁজে, যাকে শিবরাম বলেছিলেন, “আমার জীবনে তুই একমাত্র মেয়ে। তুই প্রথম আর তুই-ই শেষ”।
আরও পড়ুন
আসল ঘনাদার বাড়ি, শিবরাম এবং...
কলকাতায় এসে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে অসহযোগীদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলেন। খুব দ্রুত দেশবন্ধুর প্রিয় হয়ে উঠলেন। একই সঙ্গে ভর্তি হলেন নেতাজি পরিচালিত গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে এবং যথাসময়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন ম্যাট্রিক। আর দিন চলত দৈনিক পত্রিকা বিক্রি করে। সেকথা জানতে পেরে দেশবন্ধু তাঁকে ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করে নেন, যাতে শিবরামের সামান্য কিছু রোজগার হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আন্দামান ফেরত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ম্যানেজার ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভয়ঙ্করভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার পক্ষে, আর শিবরাম ছিলেন তার উলটো, কখনই নিয়ম শৃঙ্খলার পরোয়া করতেন না। শিবরামের বেপরোয়া হালচাল দেখে একদিন সুভাষ বসু শিবরামকে ডেকে সব পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে বলে দিলেন “কাল থেকে আর আসার দরকার নেই”।
কাজ খুইয়ে শিবরাম ভাবলেন নিজেই একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। প্রকাশ করলেন ‘যুগান্তর’। এদিকে যুগান্তর নামে আগে বিপ্লবীদের একটা কাগজ ছিল। পরে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ পুলিশ ভাবল বিপ্লবীরাই বোধহয় ফের যুগান্তর প্রকাশ করেছে। ফলে গ্রেফতার হয়ে গেলেন শিবরাম। জেলে থাকাকালীন বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন শিবরাম। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হল, “কোকিল ডাকে ভোরের ফাঁকে আম্রশাখে/ ভোরের হৃদয় যায় যে চিরে ব্যথার তীরে/ বুক ভেসে যায় নয়ন নীরে.....”। বোঝা যায় গভীর কষ্ট পাচ্ছিলেন, ভালবাসার কষ্ট, হয়তো রিনির জন্যই, কে জানে! তখনও চেনা যাচ্ছে না সেই হাসির শিবরামকে। জেল থেকে লেখা আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভারতী’ পত্রিকায়। সেটার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ।
শিবরাম ‘চুম্বন’ নামে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষের ‘বিজলী’ পত্রিকায়। ‘বিজলী’ সে কবিতা ছাপেনি। শুধু তাই নয়, শিবরাম এই নিয়ে কথা বলতে ‘বিজলী’ দফতরে গেলে তাঁকে একটু অপমানিতই হতে হয়। কিন্তু সে কবিতা ছাপা হল, ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। আর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ‘ভারতবর্ষ’-র সম্পাদককে ‘শনিবারের চিঠি’-র সজনীকান্ত দাশ এমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান শিবরাম।
বেশ কিছু দিন শিবরাম রাতে ঘুমোতেন ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনের ফুটপাথে আর খেতেন মল্লিকদের মার্বেল প্যালেসে লঙ্গরখানায়। কাছেই মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে তখন একটি নতুন বড় বাড়ি উঠছে। শিবরামের সেখানে চৌকিদারির কাজ জুটে গেল। ফলে সেখানে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাও মোটামুটি একটা হল। পরে বাড়ি শেষ হলে, বাড়িটি একটি মেসবাড়ি হয়। সেখানেই একটি ছোটো ঘর ভাড়া নিয়ে আজীবন ছিলেন শিবরাম।
১৯২৫-এ প্রথম উপন্যাস ‘ছেলেবয়েস’। ১৯২৯-এ দুটি কাব্যগ্রন্থ,’ চুম্বন’ এবং ‘মানুষ’। সে বছরই আরেকটি বই এম সি সরকার থেকে বেরিয়েছিল, ‘আজ এবং আগামীকাল’। এই তিনটি বইই হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়। প্রবন্ধের বই ‘আজ এবং আগামীকাল’-এ দুটি বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগে সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ। দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম লেখাটি ছিল ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি’। বাকি লেখাগুলি ছিল, ‘অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য’, ‘দো রোখা’, ‘ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্ততা’, ‘শূদ্র না ব্রাহ্মণ’। ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি’ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘ দিন আলোচনা হয়েছে। তখন শিবরামের বয়স তিরিশ পেরোয়নি। এই বইয়ের ভূমিকায় পরে শিবরাম লিখেছেন, “গান্ধীবাদই, আমার মনে হয়, কমিউনিজমকে সম্পূর্ণ করতে পারে। ভারতীয় আত্মিক সাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্যনীতির আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের সাফল্য ঘটতে পারে। আর ঘটবেও তাই”। ‘যখন তারা কথা বলবে’, ‘চাঁদের আলো’ ইত্যাদি নাটকও এই সময়ই লেখেন শিবরাম।
‘রামধনু’ পত্রিকায় প্রকাশের বেশ কিছু পরে বই হয়ে বেরোলো ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ১৯৩৭ সালে। তার ৩৩ বছর পর ঋত্বিক ঘটক এই লেখা নিয়ে সিনেমা বানালেন। তখন ছোটদের কাগজ ‘মৌচাক’-এর খুব নাম-ডাক। সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি ১৫ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে শিবরামকে বললেন, ছোটোদের জন্য লিখতে। সেটা ১৯৩৫ সাল। সেই প্রথম শিবরামের লেখা থেকে আয়। শিবরামের ভাষায়, “অ্যাতো লিখেও একটা পয়সা পাইনি, আর এই না লিখেই টাকা পেতেই সেই যে আমার হাসি পেল, সেই হাসিটাই প্রকাশ পেল আমার প্রথম ছোটোদের লেখায়। তার পর সেই হাসিটি ছড়িয়ে গেল আমার আরো আরো গল্পে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সেই হাসিরই সুর”। সেই প্রথম গল্পের নাম ছিল ‘পঞ্চাননের অশ্বমেধ’। সেই যে শুরু হল, আর থামেননি। অন্য লেখা লিখলেও শিবরাম ছোটদের লেখক হিসেবেই বাঁচলেন বাকি জীবন।
বাঁচলেন দাপটের সঙ্গেই, তবে আর্থিক কষ্ট মিটল না। শিবরামের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। চাঁচলের রাজবাড়ি থেকে একটা মাসোহারা পেতেন। স্বাধীনতার পর জমিদারি বিলোপ আইনে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। শিবরাম এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। কিন্তু কোনও উকিল দেননি। একজনের নাম দিয়েছিলেন সাক্ষী হিসেবে। তিনি আর কেউ নয়, যাঁর বিরুদ্ধে মামলা তারই নাম। কারণ, তিনিই নাকি বিষয়টি সব থেকে ভালো জানেন। মামলা খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্ট বলেছিল, হাইকোর্টের ইতিহাসে এমন আজগুবি মামলা নাকি কেউ কখনও করেনি। এদিকে শিবরাম নিশ্চিত ছিলেন যে মামলা জিতবেন, এবং জিতে এক লক্ষ টাকা নিয়ে তিনি কোন পথে বিশ্বভ্রমণে যাবেন সেসবও ঠিক করে ফেলেছিলেন। তখন নিয়মিত লেখা বেরোচ্ছে ‘মৌচাক’, ‘রামধনু’, ‘রংমশাল’ পত্রিকায়। কাছেই থাকতেন শিবরামের এক বোন, বিনি। শিবরামের নির্দেশে বিনি আর তার বন্ধুরা বিভিন্ন বইয়ের দোকানে গিয়ে নিয়মিত খোঁজ করতেন শিবরামে চক্রবর্তীর বই আছে কি না, তাতে নাকি চাহিদা এবং বিক্রি বাড়ে, শিবরাম মনে করতেন।
‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ নিয়ে ছবি করার জন্য ঋত্বিক ঘটক অনেকগুলো টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে সম্পর্কে এক ভাগ্নেকে একটা বইয়ের দোকান করে দিয়েছিলেন। মৌচাক পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন শিবরাম।
১৯৮০-র গ্রীষ্মকালটা পাখা ছাড়া প্রবল গরমে কষ্ট পেয়ে এবং নাছোড়বান্দা জ্বরে ভুগে কাটল। বর্ষার সময় একদিন প্রতিবেশীরা দেখলেন বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন শিবরাম। তাঁরাই পিজি হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলেন। পরে আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু এবং তাঁর এক সঙ্গী যখন হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিলেন, ততক্ষণে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে মৃতদেহ চলে গেছে মর্গে।
হায়দ্রাবাদ প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক সুরজিৎ দাশগুপ্তকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই বইটি উপহার দেওয়ার জন্য। বইটির সামান্য অংশই এখানে লেখার সুযোগ ঘটল। আশা করি পাঠক সংগ্রহ করে বাকিটা পড়ে নেবেন।
বই - শিবরাম চক্রবর্তী
লেখক - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
প্রকাশক - সাহিত্য অকাদেমি
দাম - ৫০ টাকা





























