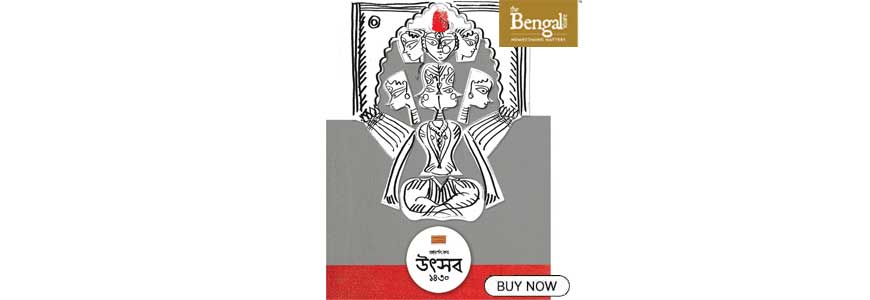রেবেকা মণ্ডল : নকশিকাঁথার বুনোটে পল্লিবাংলার মেয়েদের সাবলম্বী হতে শেখাচ্ছেন

স্যাঁতসেঁতে বর্ষা হোক বা হালকা ঠাণ্ডা, একদা বাঙালির নিত্যসঙ্গী ছিল নকশিকাঁথা। কেবল ঘুমের সঙ্গী বলা ভুল, বাঙালির লোকচার ও লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল নকশা করা কাঁথা। এককালে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নকশিকাঁথা নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। পাত্রী নকশিকাঁথা বুনতে পারে জানলে পাত্রপক্ষ প্রীত হত। নকশিকাঁথায় ধরা দেয় পল্লি বাংলার লোকায়ত জীবন, বেঁচে থাকার গল্প। লুকিয়ে থাকে ইতিহাস। সুতোর কাজে ফুল, পাখি, শঙ্খলতা, মটরলতা, লতা-পাতার নকশা আর বউ-ঝিদের সহজাত শিল্পবোধে অনন্য হয়ে ওঠে এ জিনিস। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, এমনকি সিনেমায় বারবার উঠে এসেছে নকশিকাঁথার কথা। আবহমান বঙ্গসংস্কৃতির এহেন উপাদানকে কেন্দ্র করে বীরভূমের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলছেন রেবেকা মণ্ডল। বিগত দু’বছর ধরে তিনি নকশিকাঁথা নিয়ে কাজ করছেন। মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন এই শিল্পকে। তাঁর নিজের কথায়, আদ্যন্ত ভালোবাসা থেকেই এ কাজ করে চলেছেন তিনি।

রেবেকা থাকেন বীরভূম-এর ইলামবাজারে, শান্তিনিকেতন থেকে জায়গাটির দূরত্ব প্রায় আঠারো কিলোমিটার মতো। আশপাশের গ্রামের প্রায় পঞ্চাশজন মহিলা সূচিশিল্পীকে নিয়ে কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন রেবেকা। একদিকে হারিয়ে যেতে বসা শিল্প অক্সিজেন পাচ্ছে, পাশাপাশি প্রান্তিক মহিলারাও উপার্জন পাচ্ছেন। গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান জুগিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন সফল ‘অন্ট্রাপ্রেনার’ (Entrepreneur) তথা উদ্যোক্তা।
ইলামবাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়েরা আয়ের পথ পাচ্ছেন, রেবেকার মতো মহিলাদের নেতৃত্বে লাল মাটির দেশে স্বনির্ভরতা আন্দোলনের রূপ পেয়েছে নকশিকাঁথা

রেবেকা মণ্ডল
রেবেকা মণ্ডল জানাচ্ছিলেন, কাঁথার জন্য কাপড়, সুতো সব তিনিই শিল্পীদের কাছে পৌঁছে দেন। ডিজাইনও তাঁর নিজের। তারপর কাঁথা বোনেন গ্রামের মেয়ে-বউরা। সেই কাঁথা তিনি বিক্রির ব্যবস্থা করেন। বড়ো একটা কাঁথা বুনতে প্রায় দুই-আড়াই মাস সময় লেগে যায়। পরিশ্রম ও ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে শিল্পীরা পারিশ্রমিক পান। রেবেকার পুরো ব্যবসাই চলে অনলাইন মাধ্যমে। অর্ডার নিয়ে তিনি কাজ করেন। ক্রেতারা যোগাযোগ করলে তিনি নকশার নমুনা পাঠান। তারপর ক্রেতার যেটা পছন্দ হয়, সেই নকশা অনুযায়ী সম্ভাব্য সময় চেয়ে নেন। তাঁর কোনও শিল্পীই আজ আর খালি হাতে বসে থাকেন না। অর্থাৎ কাজের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে। তাঁর নিজের কথায়, তিনি ‘স্টক’ রাখেন না। শিল্পীদের একটার পর একটা কাজ এখন দিতে পারছেন।
কিন্তু কেমন ছিল গোড়ার দিকের দিনগুলো? বঙ্গদর্শন.কম-কে রেবেকা জানালেন, “আমি পরিবার থেকে উৎসাহ পেয়েছি। একেবারে শুরুর দিকে গ্রাহকদের থেকে বা সূচিশিল্পীদের থেকে সাড়া পাওয়া একটু কঠিন ছিল। তারপর গ্রামের মহিলাদের অনেক বোঝাই। যেসব বয়স্ক মহিলারা আগে নকশিকাঁথার কাজ করতেন, তাঁদেরকে দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম কাঁথা কেনার বিষয়ে অনেককেই আগ্রহী, তখন ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের মহিলাদের (যাঁরা কাঁথা স্টিচের কাজ জানেন) দিয়ে কাজ শুরু করলাম। নতুন প্রজন্মও এগিয়ে এল। ওঁদের উৎসাহ বাড়ল।”

নকশিকাঁথার গ্রাহক কারা? রেবেকা বলেন, “মূলত কলকাতার লোকেরাই তাঁর প্রধান ক্রেতা। ৯০ শতাংশ ক্রেতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা উপহার হিসেবে কাউকে দেওয়া জন্য নকশিকাঁথা কেনেন ( B to C অর্থাৎ সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রি করা হয়)। বাকি দশ শতাংশ রিটেল হয় (B to B অর্থাৎ অন্য কোনও ব্যবসায়িক সংস্থাকে বিক্রি করা হয়)।” কাঁথার বিক্রয়মূল্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন, “ডিজাইনের উপর নির্ভর করে দাম। একটা ৭/৬ (সাত ফুট X ছয় ফুট) কাঁথার দাম শুরু হয় ৩,২০০ টাকা থেকে। ৬,২৫০ টাকা দামের কাঁথাও রয়েছে। আর ছোটোদের কাঁথা শুরু ৩৮০ টাকা থেকে।”

নকশিকাঁথাকে কেন্দ্র করে কাজের যাবতীয় কৃতিত্ব, শিল্পীদেরই দেন রেবেকা। তাঁর কথায়, “আমরা হয়তো শুধুমাত্র ওঁদের জায়গাটা দেখাচ্ছি, কীভাবে কাজ করবে বা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি সবাই মিলে। বাংলার এই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পটাকে সবাই মিলে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছি কেবল, কিন্তু কাজটা সম্পূর্ন ওঁদের হাতের। সব কৃতিত্বই শিল্পীদের। আগে যে জায়গাটা ওঁরা পায়নি, এখন হয়তো সেটা পাচ্ছেন। ওঁদের হাতের কাজ গোটা দেশে ছড়াচ্ছে, দেশের বাইরেও যাচ্ছে। সেটা শিল্পীদের কাছে সম্মানের ও খুব আনন্দের বিষয়।”

কথায় বলে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। কত মায়া-স্মৃতিতে জড়ানো, দুই বাংলার এক্কেবারে নিজের জিনিস নকশিকাঁথাকে কেন্দ্র করে সেই লক্ষ্মীকে বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছেন রেবেকা। মা-ঠাকুমাদের ঐতিহ্যবাহী সূচিশিল্পই হয়ে উঠেছে ‘ইউএসপি’। ইলামবাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়েরা আয়ের পথ পাচ্ছেন, রেবেকার মতো মহিলাদের নেতৃত্বে লাল মাটির দেশে স্বনির্ভরতা আন্দোলনের রূপ পেয়েছে নকশিকাঁথা।