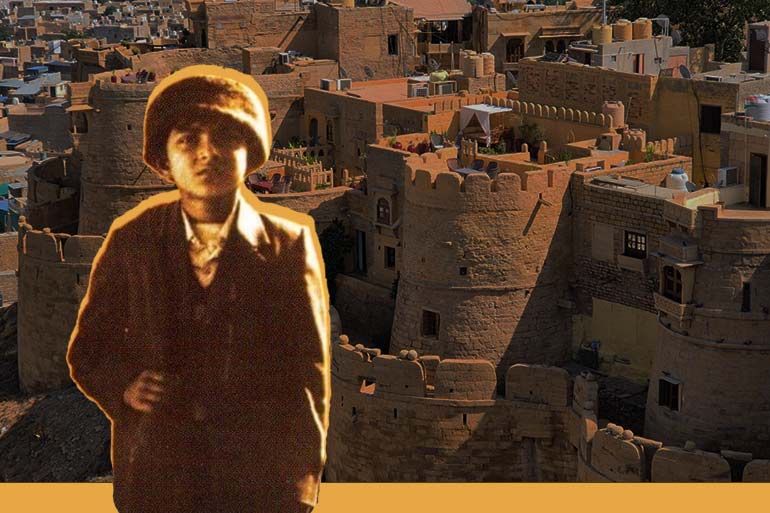ঘাটের কথা – পুরোনো কলকাতার জীবন্ত ইতিহাস

হুগলি নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা দেখছি তিলোত্তমার রূপ। এই সপ্তাহে কয়েকটি বিখ্যাত ঘাটে যাব। নদীর মৃদুমন্দ বাতাসে সফর ভালোই জমবে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে খানিকটা এগিয়ে শুরু হবে আজকের যাত্রা। শেষ হবে দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে গিয়ে। মাঝখানে পড়বে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। চলুন শুরু করা যাক –
ইডেন গার্ডেনস
ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কথা এখন বলব না। প্রিন্সেপ ঘাটের প্রায় আধ কিলোমিটার উত্তরে স্ট্র্যান্ড সংলগ্ন রাস্তায় এক বাগান রয়েছে, যার থেকে স্টেডিয়ামের নামকরণ। গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের দুই বোন এমিলি এবং ফ্যানি ইডেনের স্মরণে বাগানের নাম রাখা হয়েছে। বাগান এবং স্টেডিয়াম নিয়ে গোটা এলাকা প্রায় ৫০ একর বিস্তৃত। কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো পার্ক এটি। ইডেন বোনেদের তৈরি নকশা অনুসরণ করে ১৮৪১ সালে পার্কের নকশা চূড়ান্ত করেন ক্যাপটেন ফিটজজেরাল্ড।
বাগান আর আগের মতো প্রাণবন্ত নেই। তবে পুরোনো গাছের সারি আজও মন জুড়িয়ে দেয়। মুগ্ধ করে পাখিদের কলতান। আরেকটি বড়ো আকর্ষণ খাঁটি ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির আদেশে প্রোম থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ১৮৫৪ সালে।
 বাবুঘাট
বাবুঘাট
এই ঘাটের ‘বাবু’ হলেন জানবাজারের রাজচন্দ্র দাস। রানি রাসমণির স্বামী। প্যাটিও আকৃতির সৌধে ডোরিক কলামগুলো আজ আগের মতো নেই। এক সময় ঘাটে গঙ্গাস্নানে আসা বাঙালিদের আশ্রয় দিত এই প্যাটিও। এখন পুরোহিত, ফুলওয়ালা, নাপিত এবং ধর্মীয় আচার সংক্রান্ত আরও নানা লোকের ভিড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা। তবে নদীর দিকে তাকালে অসাধারণ দৃশ্য চোখে পড়ে – হাওড়া ব্রিজ কিংবা হাওড়া স্টেশনের মনোহর সৌন্দর্য।
 চাঁদপাল ঘাট
চাঁদপাল ঘাট
বাবুঘাটের তুলনায় এটিকে খুঁজে বের করা একটু কঠিন। সম্ভবত ১৮ শতকের এক মুদি চন্দ্রনাথ পালের নামে ঘাটের নামকরণ। এখন চা এবং অন্যান্য জিনিসের স্টলে ভর্তি। প্রায় স্থায়ী কিছু দোকানপাট রয়েছে। এক সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতায় আসার প্রধান ঘাট ছিল এটি। ব্রিটিশ রাজ-সরকারের যুগে নদীর থেকে প্রবেশপথ হিসেবে বাবুঘাটের পরেই ছিল চাঁদপাল ঘাটের মর্যাদা।
 মল্লিক ঘাট
মল্লিক ঘাট
চাঁদপাল ঘাট থেকে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাঁটতে থাকুন। পথে কোম্পানির লাল রঙের গুদামগুলি দেখতে ভুলবেন না। বেশিরভাগই গড়ে ওঠে ১৯ শতকে। তবে সাধারণ গুদামের থেকে অনেক বড়ো দেখতে। মল্লিক ঘাটে পৌঁছলে দৃশ্য বদলে যাবে। রবীন্দ্র সেতুর দিকে যাওয়া ফ্লাইওভারের বাম দিকে তার অবস্থান। ব্রিটিশ আমলে নুন এবং রিয়েল এস্টেটের এক ব্যবসায়ী ছিলেন নিমাইচরণ মল্লিক। তাঁর স্মৃতিতে ১৮৫৫ সালে ঘাট তৈরি করেন ছেলে রামমোহন মল্লিক। পাথুরিয়াঘাটায় রামমোহনের ভাই মতিলাল গড়ে তোলেন প্রাসাদোপম মল্লিক বাড়ি।
আরও পড়ুন: পায়ে হেঁটে জানুন কলকাতার ইতিহাস
প্রথম থেকেই কলকাতার অন্যতম গঙ্গাস্নানের জায়গা এই মল্লিক ঘাট। বাবুঘাট প্যাটিওর থেকে দেখতে অনেক বেশি ভারতীয়। নিয়মিত এখানে কুস্তির অনুশীলন চালান পালোয়ানেরা। গঙ্গার কাদা গায়ে মেখে। ফটোগ্রাফারদের খুব পছন্দের গন্তব্য। কুস্তিমঞ্চের পাশেই রয়েছে ১৮ শতকের মারোয়াড়ি বণিক রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার স্মৃতিস্তম্ভ। স্যার হরিরাম এবং স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার বাবা।
মল্লিক ঘাটের আরেক আকর্ষণ ফুলের বাজার। ভোর থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত সবচেয়ে জমজমাট থাকে। খুচরো এবং পাইকারি দরে বিচিত্র সব ফুল বিক্রি হয়। মহামারি সময় বাজার অনেকটা ম্লান হয়ে এলেও খোলা রয়েছে।
 পুরোনো রুপোর টাঁকশাল
পুরোনো রুপোর টাঁকশাল
কলকাতার এটি তৃতীয় টাঁকশাল। স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালের মার্চে। বন্দর পুলিশ কোয়ার্টারের ঠিক উল্টোদিকে স্ট্র্যান্ড রোডে হুগলি নদীর একটি ঘাটের পাশে আজও দাঁড়িয়ে। গড়ে তুলেছিলেন মেজর ডাব্লু এন ফোর্বস। কলকাতার তিন প্রসিদ্ধ ধনপতির সহায়তা পেয়েছিল এই টাঁকশাল – পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। জমকালো সম্মুখভাগ-সহ বিশাল ভবন নির্মাণ শেষ হয় ১৮৩০ সালে।
আরও পড়ুন: পুরোনো কলকাতার সর্বধর্ম সমন্বয় কেন্দ্র
১৮৬০ সালে ভবনের উত্তরপূর্ব দিকে গড়ে ওঠে তামার টাঁকশাল। সেখানে তামার মুদ্রা তৈরি হতে থাকে ১৮৬৫ থেকে। দুই টাঁকশালেই ব্রোঞ্জ, রুপো এবং সোনার মুদ্রা উৎপাদন হত। কিছু নথি থেকে জানা যায়, প্রতিদিন ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা তৈরি হত রুপোর টাঁকশালে। ১৯০৭ সালে এখানেই বানানো হল এশিয়ার প্রথম বিশুদ্ধ নিকেল কয়েন। একদিনে ১৯ লক্ষ কয়েন উৎপাদন করে টাঁকশাল বিশ্বরেকর্ড গড়ল ১৯১৮ সালে।
২০০৮ সালে রুপোর টাঁকশালকে হেরিটেজ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও এখন গোটা ভবনই উদাসীনতার শিকার। ধীরে ধীরে একিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। সংস্কারের অল্প কিছু কথাবার্তা হলেও সত্যিকারের কাজ শুরু হয়নি কিছুই।
 নিমতলা ঘাট
নিমতলা ঘাট
কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত শ্মশানের একটি। পথের বিশৃঙ্খল ভিড় আপনাকে আশাহত করতে পারে। সাহস করে এগিয়ে যান। ১৮ এবং ১৯ শতকের নানা লেখায় বর্ণিত চরম অপ্রীতিকর সব দৃশ্য এখন আর দেখতে পাবেন না। শ্মশান বহুবার সংস্কার হয়েছে। বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙালির শেষকৃত্য ঘটেছে এখানে। তাই নিজে এসে দেখার মূল্য আলাদা। নিমতলা এবং আহিরিটোলা ঘাটের মাঝখানেই কোথাও জোব চার্নক প্রথম ১৬৯০ সালে নৌকা থেকে নেমেছিলেন বলে জানা যায়। কলকাতার ‘জন্ম’ হওয়ার কিংবদন্তি জুড়ে গিয়েছে এই এলাকার সঙ্গে।
দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট
নিমতলা থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড পেরিয়ে চলে যান দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে। ইনি রবীন্দ্রনাথের এক পূর্বপুরুষ। ঠাকুর পরিবার গোবিন্দপুর এলাকা থেকে চলে আসে এখানে। কারণ পুরোনো বাড়ির জায়গায় আজকের ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ শুরু হয় ১৭৫৮ সালে।
.jpg) কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদ, বৈষ্ণবদাস মল্লিকের তৈরি দুশো বছরেরও পুরোনো ভগবতী মন্দির ছাড়াও দেখতে পারেন ১৭৯০-র দশকে গড়ে ওঠা বৈষ্ণবদাসের বসতবাড়ি ‘মধুপুর’। এই বাড়ি থেকেই মল্লিক পরিবারের দুটি প্রধান শাখা ছড়িয়ে যায়। একটি মার্বেল প্রাসাদের মল্লিকরা, অন্যটি চিৎপুর রোডের ঘড়ি ঘরের মল্লিক পরিবার।
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদ, বৈষ্ণবদাস মল্লিকের তৈরি দুশো বছরেরও পুরোনো ভগবতী মন্দির ছাড়াও দেখতে পারেন ১৭৯০-র দশকে গড়ে ওঠা বৈষ্ণবদাসের বসতবাড়ি ‘মধুপুর’। এই বাড়ি থেকেই মল্লিক পরিবারের দুটি প্রধান শাখা ছড়িয়ে যায়। একটি মার্বেল প্রাসাদের মল্লিকরা, অন্যটি চিৎপুর রোডের ঘড়ি ঘরের মল্লিক পরিবার।
চিৎপুর রোড থেকেই পরের দিনের হাঁটা শুরু হবে। ততক্ষণ যাত্রা শুভ হোক।