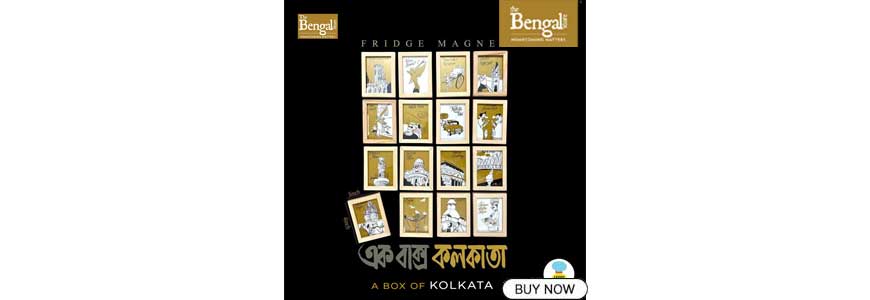দেশভাগের ৭৫-এ ঋত্বিকের ‘কোমল গান্ধার’ : সীমানাকে অতিক্রম করে যাওয়ার নাছোড় বাসনা

ঋত্বিক (Ritwik Ghatak) এমন একজন চলচ্চিত্রকার (Film Maker), শিল্পী (Artist) যিনি তাঁর জীবন ও শিল্পকে কোনোদিন আলাদা চোখে দেখেননি। জীবনচর্চা আর শিল্পচর্চাকে এমন মিলিয়ে দেওয়ার বিশেষ উদাহরণ আমাদের কাছে নেই। সেই নাগরিক (Nagarik) থেকে যুক্তি তক্ক (Jukti Takko Aar Gappo)... এমনই তার দর্শন শেষ পর্যন্ত আত্মজীবনীও বানাতে হলো বলার কথা স্পষ্ট করে বলার জন্য। আমাকে বিস্মিত করে দেয় এই জীবন দর্শন। তা সবাই বুঝে উঠতে পারেনি তার মূল কারণ যাঁরা এর সমালোচনা করেছে তাঁদের এই যাপন সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।
ঋত্বিককে শুধুমাত্র দেশভাগের (Partition) প্রতি আটকে থাকা ভাবনা বা গণ্ডি বলে বহু সমালোচনা হয়েছে। যারা ভুক্তভোগী তারাই জানে দেশভাগের যন্ত্রণা। আমি এপারের কিন্তু তাতে তফাৎ কিছু পড়েনি। শিল্পের যে ভিতরের যন্ত্রণা, আমি তার সাথে জীবনের বেশিরভাগ সময় ঘর করেছি। পরিবার ছেড়ে, নিশ্চিত ছাদ, নিশ্চিত পরিমণ্ডলকে ছেড়ে আসার পর কিশোর বয়সে, বাকি জীবন শিল্পকেই মূল পরিধান ভেবেছি।

ঋত্বিক সব অর্থেই এক নাগরিক শিল্পী। নাগরিক থেকেই আমরা এই নাগরিক অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পারছি। তিতাস যদিও জেলে বা মল্লবর্মণদের জীবন নিয়ে এক বিশাল ক্যানভাসের গল্প, তবুও তার দেখার চোখ আমাদের নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেয় তার মুক্তমনা মনুষ্য জীবনের গভীর আর্তি, তার বিপন্নতা, তার অসহায়তা, সেখানে নগর বা গ্রামকে ভাগ করা যায় না।
অনসূয়াকে ভৃগু যখন সেই ট্রেন লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে দূরের দিগন্ত, বলছে ওই পারে আমার দেশ। সামনে নদী বয়ে যাচ্ছে, যা জীবন। যে যান্ত্রিকতা, যে ট্রেনের বাফার, লাইনের প্রান্ত, তার আগে আমরা জানছি দোহাই আলির আর্তনাদ। এভাবে শব্দকে দৃশ্যভাষা করে তোলা, শব্দকে দর্শন বানিয়ে তোলা, একমাত্র, একমাত্র ঋত্বিকই পেরেছিলেন।

ঋত্বিক ছিলেন ওপার বাংলার মানুষ। তার আবেগ থাকা স্বাভাবিক কিন্তু, সেই ভৌগোলিক দেশভাগকে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ, শ্রেণির মধ্যে সংঘাত সবই বিচার্য ছিল। ‘কোমল গান্ধার’ (Komal Gandhar) চলচ্চিত্রে একটি নাট্যদল তার অন্তর কলহ ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ, সন্দেহ, সংশয়, মতবিরোধ সবই এসম্বন্ধে থেকেছে। সেখানেই ভৃগু আর অনসূয়ার মিলন। তাদের মধ্যে সংশয়, শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটে। এই মিলনকে আমি দেখি ঋত্বিকের ইচ্ছেপূরণের আকৃতি হিসেবে। যেভাবে ক্যামেরা উপর থেকে নেমে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গিয়ে আবার উপরে উঠে অনুসূয়াতে গিয়ে থামে, আমার সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্য। যেন একটা স্বপ্ন হরণের, আবেগের কাহিনি। দেশ হয়তো জুড়বে না কিন্তু মনটা জুড়তে পারে। শিল্পী, বিশেষ করে প্রগতিশীল শিল্পীরা সমাজে-মানুষে আশাকে গুরুত্ব দিতে চান। যে আশা পূরণ হোক বা না হোক, আশাই জীবন।

অনসূয়াকে ভৃগু যখন সেই ট্রেন লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে দূরের দিগন্ত, বলছে ওই পারে আমার দেশ। সামনে নদী বয়ে যাচ্ছে, যা জীবন। যে যান্ত্রিকতা, যে ট্রেনের বাফার, লাইনের প্রান্ত, তার আগে আমরা জানছি দোহাই আলির আর্তনাদ। এভাবে শব্দকে দৃশ্যভাষা করে তোলা, শব্দকে দর্শন বানিয়ে তোলা, একমাত্র, একমাত্র ঋত্বিকই পেরেছিলেন। চাবুকের শব্দ, ড্রামের শব্দ, নানা কর্কশ শব্দ, সবই যেন দৃশ্যকথা। বলার কথা আমাদের আবেগে আঘাত করে। এত নির্মম চিত্র পরিচালকও আমরা বিশ্ব চলচ্চিত্রে বিশেষ পাইনি।

মেঘে ঢাকা তারার (Meghe Dhaka Tara) শেষ দৃশ্য, যা নিয়ে মৃণাল সেন (Mrinal Sen) ও ঋত্বিকের মতবিরোধ হয়। ঋত্বিক মানেননি। সামাজিক স্বাভাবিক ব্যবহার, যেখানে দাদা বোনের কুশল জিজ্ঞেস করারপরিবর্তে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে নীতা চলে যাবার পর সংসারটা কেমন ফুলের তোড়ার মত সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কী নির্মম। তখনই নীতার আবেগ উথলে ওঠে এবং সেই বিখ্যাত আর্তি।
দেশভাগ তখন প্রতীক হয়ে যায়। জীবন ও মৃত্যুর মাঝের সীমানা, সেই সীমানাকে একধারে অগ্রাহ্য করতে চাওয়া, একধারে অতিক্রম করে যাওয়ার বাসনা।

সমস্ত অলংকরণ (‘কোমল গান্ধার’ ছবির) - হিরণ মিত্র