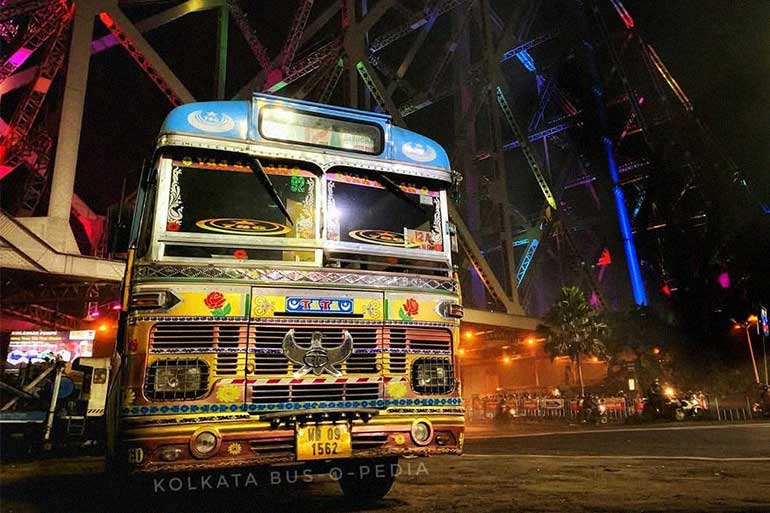দারুণ গরম দিনে কলকাতার পাংখাপুলিং

ভরা শ্রাবণ মাস। তবু গরম কমে না। এ শহরে আটমাস গরম। আর বাকি চারমাসে শীত আসতে আসতেই ফুরুত। তা এই গরম শহরে কিন্তু বিলিতি সাহেবসুবোরা এসে বেশ কাহিল হয়েই পড়তেন। চড়া রোদে খানিক ঘোরাঘুরি করেই সাগরপারের প্রাণ টুপটাপ খসে পড়ত। বয়সের তোয়াক্কাও করত না গরমের দাপট। তবু তারা আসত দলে দলে। গরমে থেকে থেকে নিজেদের অভ্যাসকেও বদলে নিয়েছিল তারা। নিয়মিত স্নান, পরিমিত পান – এইসব রপ্ত করতে হয়েছিল এই শহরে থাকার জন্যে। অবশেষে একটা সুরাহা তারা খুঁজে পেয়েছিল অবশ্য। তা হল টানা পাখা। তপ্ত গ্রীষ্মের একমাত্র আরাম। আর কলকাতায় শুধুই তো গরম নয়। মশা-মাছির মারাত্মক উপদ্রব। মশার কামড়ে কম ইউরোপীয় প্রাণ খোয়ায়নি। তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে পাখাই একমাত্র সম্বল ছিল [ল্যাজ যখন নেই, কী আর করা যাবে!]
তবে, পাখা ব্যাপারটা এদেশে তো নতুন নয়। চামরই ছিল সেই কত যুগ ধরে। তারপর বাহারি নকশাদার হাতপাখা। রাজা-বাদশার পিছনে লম্বা ডান্ডার পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবিচল ভৃত্যদের ছবি প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতায় পাখা চালু হয় বেশ পরে। আর টানা পাখার চলন তো আরো পরে। ফলে শহরে গরম সহ্য করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। যদিও কোনো কোনো বিদেশি এই শহরের মোহে এমনি আটকে ছিলেন যে গরমকেও বেজায় ভালোবেসেছিলেন। গরম যেন একটা ‘মায়া’, আসলে নেই – নিজেদের স্মৃতিচারণে তারা এমনটাই লিখেছেন অনেকে। লিখেছেন, সকালে খুব গরম পড়লেও বিকেল হতেই কালবৈশাখী ঝড় ছুটে আসে, তাতেই শহর একেবারে ঠান্ডা। অবশ্য এই অন্ধ গুণগ্রাহীর সংখ্যা বিরলই। এমিলি ইডেন এই শহরের গরম সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন, ‘It was so HOT- I don’t know how to spell it large enough...’। আবার কেউ কেউ লিখেছেন, আত্মহত্যার পক্ষেও এই রোদ আর গরম অত্যন্ত কার্যকরী। এক-আধবার ঘুরলেই হল। প্রবল গরম, তবু হেস্টিংসের সময়কাল পর্যন্ত কলকাতায় পাখা নেই।
পাখা এখানে হাজির হয়, ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে। তার আগে পাংখাকুলি বা পাংখাবরদারের কোনো উল্লেখা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় প্রায়শই মনে হয়। শহর গড়ার সেই আদি যুগে কতরকমের পেশাই না তৈরি হয়েছিল। হুঁকাবরদার, ভিস্তিওয়ালা, পাংখাকুলি – শহর প্রাপ্তবয়স্ক হতে না হতেই সেসব পেশারা হারিয়ে গেল। মানুষগুলোও।
যাই হোক, এই হাতে-টানা পাখা নিয়ে গল্প কম নেই কলকাতায়। বিশেষত পাংখাকুলিদের নিয়ে। তাদের ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পাখা টানা। পায়ে দড়ি বেঁধে সমান তাল বজায় রেখে চলা – ইত্যাদি কত কিছু। আসলে টানা-পাখা হাত পাখার চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগত। একটা বড়ো ঘরে অনেকের মাঝে হাত-পাখা বড়োই সমস্যার। তার চেয়ে টানা-পাখায় আরাম অনেক বেশি। ওপরের কড়িবরগা থেকে ঝোলানো প্রায় ২০ ফুট লম্বা লাঠি। কাঠ দিয়ে তৈরি ফ্রেম। সেখান থেকে ঝুলত লং ক্লথ। কখনো তাতে জুড়ে দেওয়া হত মসলিনের ঝালর বা লেস। কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে লাগানো বিশাল দড়ি ঘরের ভিতর থেকে চলে যেত বাইরে। সেই দড়ি ধরেই একবার টান, একবার ঢিল দেওয়া।
আরও পড়ুন: হেয়ার সাহেবের মৃত্যু ও একটি বিস্মৃত সমাধি
কিন্তু কার হাত ধরে এই টানা-পাখা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে অবশ্য বিবাদ আছে। শোনা যায়, আঠেরো শতকের শেষে চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নর আবিষ্কার করেছিলেন এই কেরামতি। আবার ১৭৯২ সালে ক্যালকাটা ক্রনিক্যালে লেখা মেলে, সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা নাকি এই টানা-পাখার প্রচলন শুরু করেন। য়ুল বার্নেল সাহেব আবার লিখেছেন ইংরেজ, ডাচ, পর্তুগিজ কেউ না। টানা-পাখার প্রথম বন্দোবস্ত করে আরব দেশের মানুষ। কে এই মহৎকর্মের জন্মদাতা – তা নিয়ে রাজায়-রাজায় দারুণ লড়াই। কিন্তু শোনা যায়, কলকাতায় সবার আগে এই ফন্দিটি যার মাথায় এসেছিল, তিনি নাকি একজন ইউরেশিয় কেরানি। ফোর্ট উইলিয়ামের এক মারাত্মক গরম ঘরে ছিল তার নিত্যদিনের কাজ। একদিন গরম আর মশার ভনভনানি তার অসহ্য লাগল। সে তখন তার ক্যাম্প টেবিলের একটি দিক কাঠ-সমেত খুলে ফেলে। তারপর মাথার ওপর ঝুলিয়ে দেয়। একটা দড়ি দিয়ে তা টেনে টেনে হাওয়া খেতে থাকে। এভাবে কলকাতায় টানা-পাখার জন্ম। কেরানির এই বুদ্ধি এরপর কাজে লাগে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, লাটবেলাটের ঘরে টানা পাখা ঢুকে যায়। রাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে, নবাব মুনশির বাড়িতে হাওয়া বইতে থাকে৷ সেই নতুন হাওয়া মনপ্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছিল শহরের সবার। কেরানি জীবনের এমনিতে তেমন সুনাম নেই। কিন্তু
সেই অনামা কেরানির বুদ্ধিটি যেভাবে টোকাটুকি করেছিল বড়োবাবুরা, তাতে কেরানিত্বের খানিক জয়জয়কার মেলে আরকি। টান-পাখার আবির্ভাব শহরকে প্রায় নবজীবন দান করেছিল আরকি। আজকের গ্লোবাল ওয়ার্মিং শব্দবন্ধটি তখনো বেশ দূরে ছিল কিনা।
ঋণ: ‘কলকাতা’ - শ্রীপান্থ
ছবি: স্যার চার্লস ডি’অলি