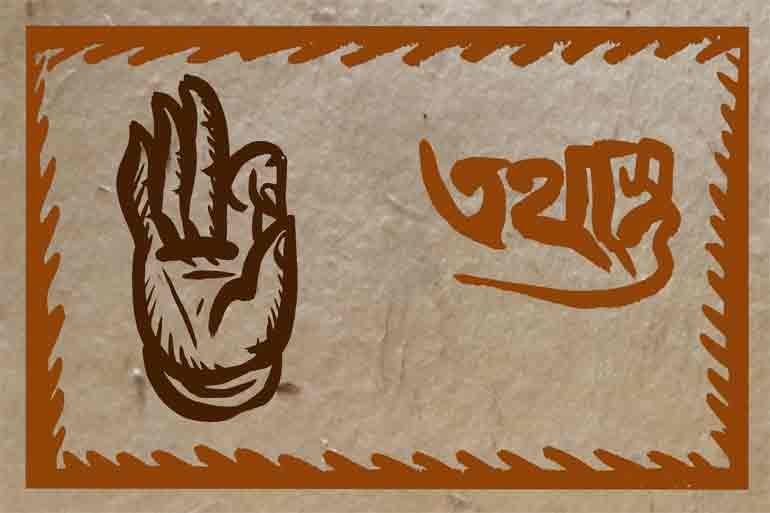মুদ্রারাক্ষস

উঠোনের রোদ্দুরে উবু হয়ে বসে গোঁফটা কামিয়ে ফেলছিল সুবল। অনেকদিন হয়েছে, আর না। বহুৎ ঝামেলা এসবের। তাছাড়া বুড়ো হতে চলল, এখন কাত্তিকে-গোঁফের শখ-টখ আর জিইয়ে রেখে কাজ নেই। এমন সময় বরের কাছটায় গিয়ে গলা নামিয়ে আরতি বলল, আমার বেশ কিছু টাকা যে বেআইনি হয়ে গেল গো!
আধখানা গোঁফ বাকি রেখেই জুলজুলে চোখে বউয়ের দিকে তাকাল সুবল। ‘বেআইনি’ কথাটাই কেমন ধক-জাগানো—রাজা-উজির থেকে ফকির-ভিখিরি সবাইকেই এক ঘায়ে তাতিয়ে দেয়!জল-ভরা প্লাস্টিক মগটার পাশে খুর আর হাত-আরশিটা রেখে ও জিজ্ঞেস করল, কত? এল কোত্থেকে?
সুবলের না বোঝার কথা নয়। কিন্তু মানুষটা অমনই—আলাভোলা। তবু সংসারের সব কথাই ওর কানে একবার তুলে রাখে আরতি। ওকে ছাড়া আর শোনাবেটাই বা কাকে।
ওই লখুর জন্য কাজের বাড়িগুলো থেকে চেয়ে রেখেছিলাম না, কাল হঠাৎ করে দিয়ে দিয়েছে দুজন।
পাঁচটা বাড়িতে ঠিকেকাজ করে আরতি। দুবাড়ি দেয় পাঁচশো করে, আর বাকিরা প্রত্যেকে আটশো। আরতি-সুবলের ছেলে লক্ষ্মণ, ছোটো থেকেই ওর শক্ত বুকের ব্যারাম। দিন দিন কষ্টটা বাড়ছে। কিছুদিন আগে সদরের হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি করেছে আরতি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন হার্টের মধ্যে একটা ছোট্ট কব্জা বদলাতে হবে।
এমনিতে নিখরচাতে সব হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হাসপাতালেরই এক চেনা নার্স পরামর্শ দিয়েছে—যা অপারেশন অন্তত তিরিশটি হাজার টাকা হাতে না নিয়ে নেমো না আরতিদি। ডাক্তার নয় টাকা নেবে না, কিছু ওষুধপত্তরও পাবে। কিন্তু ওই কমদামি ওষুধগুলো সবকটা কাজ দেয় না। তাছাড়া আয়া-খরচা আছে, আরও হ্যান-ত্যান হাজারখানা হাঁ। মাঝপথে জোগাতে না পারলে তখন কী হবে ছেলেটার?
সে বাড়ির গিন্নিই কাল আচমকা ছটা পাঁচশো ধরিয়ে বলল, এই নাও তোমার দুমাসের মাইনে আর ছেলের জন্য সেই যে চেয়েছিলে—তার দুহাজার। মোট তিন ধরো। সময়-সুযোগ মতো শোধ দিও।
আরেকটা বাড়িতেও তাই। দুহাজার ধার আর আঠশো মাইনে—মোট আঠাশশো হয়, তার বদলে এক হাজারের তিনখানা নোট ধরিয়ে বৌদি বললেন, রেখে দাও।
মানুষের এত মাখামাখি দয়া দেখে বেবাক ভিজে গিয়ে আরতি আর তলিয়ে ভাবেনি। বাড়ি ফিরে কৌটোয় ভরে রেখেছিল। এ-মাসের মাইনেগুলো আর বাকিদের দাক্ষিণ্য মিলিয়ে তিরিশ হাজার হয়ে যাবে। শীত পড়বার আগেই অপারেশনটা করাতে হবে। লখুটা বিছানায় শোয়া। জাড়ে বড্ড কাহিল হয়ে পড়ে—শ্বাস নিতে পারে না। দেখে কে বলবে যে তেইশ বছরের ছেলে। চামড়া ফ্যাকাশে, হাত-পা কাঠিসার। এক-মাথা ঝামর চুল। আজকাল বিছানা ছাড়লেই হাঁফিয়ে পড়ে। নেহাত গরিবের জান বলে এখনও টিকে আছে।
কালকের দিনটা আহ্লাদে কেটে গেলেও, বাজটা পড়ল আজ। কাজে বেরিয়ে লোকমুখে আরতি শুনল— এক ধাক্কায় সব পাঁচশো আর হাজারের নোট বাতিল।
প্রথম-চোটে বিশ্বাস করতে পারেনি ও। চুরি-চামারি জোচ্চুরি-ছিনতাই, নয় খাটনির টাকা, তা আবার বাতিল হবে কেমন করে? কিন্তু বেলা গড়াতেই ও টের পেল—ব্যাপারটা সত্যি। দিনকতক সময় আছে, ব্যাঙ্কে গেলে পুরোনো নোট বদলে দেবে। জমাও নেবে। তারপর থেকে একেবারেই বাতিল।
বাড়ি ফিরে সেকথাটাই জানাল বরকে।
রজনীবাবুর রিক্সা টানে সুবল। সারাদিনে পঞ্চাশ-একশো যা রোজগার করে বিড়িটা চা-টা বাদ দিয়ে আরতির হাতেই তুলে দেয় সব। নেশাভাঙের দোষ নেই। তবে সুবল সংসারী নয়। উদ্যমের ছিটেফোঁটাও নেই।তার ওপর যত দিন যাচ্ছে আরও যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছে।
বাকি গোঁফটুকু কাটা হলে, ওকে ঘরে ডেকে সব খুলে বলল আরতি। ও নোট তো আর চলবে না, তাই দরদ দেখিয়ে সবাই চাপিয়ে দিল আরতির ঘাড়ে। তবে শুধু এটুকুই নয়, যা জমিয়েছিল কৌটোয় প্রায় সবই যে পাঁচশোর নোট!
২
গঙ্গানগরের আট কিলোমিটার পুবে একটা ট্রাকের কারখানা হয়েছিল বছর বারো আগে। তারই লেজ ধরে আশেপাশে গড়ে উঠল ছোটো-মাঝারি নানান ফ্যাক্টরি। লাগোয়া অঞ্চলগুলো ভোল-বদলে শহর হল দ্রুত। তাদের ছাপিয়েও ছড়িয়ে পড়ল জনবসতির ঢেউ। তেমনই একখানা ঢেউ এই গঙ্গানগর। আধা-মফস্সল বললে ঠিক হয়। বারো ক্লাস পর্যন্ত ছেলে আর মেয়েদের আলাদা আলাদা দুটো ইস্কুল, একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দুখানা মন্দির, একটা মসজিদ। গঙ্গার ধারে পীরের মাজার। টাউনের মধ্যিখানে বাজার, সেখান থেকে কিলোমিটারটাক গেলে আরতিদের পাড়া। সার-বাঁধা এক-কামরার বাসা, লাগোয়া ছোট্ট বাথরুম। ঘরের সামনে হাত-পাঁচেক চওড়া উঠোন। নিজেদের বাড়ি নয়, ভাড়া। শহুরে বস্তির থেকে একটু খোলামেলা, ঠাসাঠাসি কম। এই ঘরগুলো রিক্সামালিক রজনীবাবুরই। এই তো, চার তারিখেই তিনটে একশো আর একখানা পাঁচশো দিব্যি নিয়ে নিলেন—ঘরভাড়া। আর এর মধ্যেই বেআইনি! রাস্তায় শুনেছে বটে সুবল, কিন্তু গা করেনি। সন্ধেবেলা ও একবার রজনীবাবুর কাছ থেকে ঘুরে এল ও। উনি জানালেন, হ্যাঁ বাতিল। মিত্রবাবু নিজে টিভিতে বলে দিয়েছেন।
এদিককার মানুষজনের তো পাঁচশো-হাজারের সঙ্গে ওঠবোস কম। তাই খবরের ঝাঁঝটা এসে পৌঁছল একটু দেরিতে।
প্রধানমন্ত্রীকে রজনীবাবু ডাকেন ‘মিত্রবাবু’ বলে। ঠিক মিত্রবাবু নয়—‘মিত্রোঁবাবু’! কেন, তা অবশ্য জানে না সুবল। মিত্রবাবুকে টিভিতে বারকয়েক দেখেছে। গটমট করে হাঁটেন, হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে বক্তৃতা করেন। বেশ ভক্তি হয়। রেডিওতে একটা অনুষ্ঠানও করেন উনি। গান-টান গান বোধহয়। কত গুণ হয় এমন মান্যমানেদের। সুবল অবশ্য শোনেনি কখনও। মিত্রবাবু নাকি খুব বেড়াতে ভালোবাসেন। প্রায়ই এখানে-সেখানে যান। এই তো নোটপত্তর সব বাতিল-টাতিল করে একবার ঝট করে জাপান থেকে ঘুরে এলেন। জরুরি কাজ ছিল নিশ্চয়ই। তারপর কোথায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে নাকি কেঁদে ফেলেছেন। আহা রে, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য টাকাগুলো বাতিল করল, তারাই ওর নামে আকথা-কুকথা বললে কাঁদবে না মানুষটা?
দেশের কী ভালোটা হবে শুনি? লখুর চিকিৎসাটা হবে? খুব তো মিত্রবাবু মিত্রবাবু করে মরছ। নিজের ছেলের থেকে মিত্রবাবু তোমার-আপনার হল?—ঝামরে উঠেছিল আরতি।
এক সওয়ারির মুখ থেকে শোনা বাক্যি ধাঁ করে জিভে এসে গেল সুবলের—
কালো-টাকা সব ধুয়ে-পুঁচে যাবে, হেঁ হেঁ...
কালো-টাকা ধোবে না পুঁচবে তাতে তোমার আমার কী? আর যাদের কালো-টাকা থাকে, তাদের বড়ো বড়ো সাঁটও থাকে। ওই টিভিতে একবার কী হেঁকে দিলাম, তাতেই কালো টাকা মোছে না।
একটু থমকিয়ে সুবল জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বিল্যাক-মানিটা ঠিক কী?
দুনম্বরি টাকা সব, চুরি-চামারি করে জোটানো।
আহা, সে নয় বুঝলাম। কিন্তু একটা নোট দেখে কেউ বুঝবে কেমন করে মালটা কালো না সাদা?
উত্তর দিতে পারে না আরতি। ওর কি আছে যে কালা-ধলা ফারাক করবে?একেই মাথায় আরমাথা নেই।ছেলেটার রোগা মুখখানা দেখলে তরাসে বুকটা আকুলি-বিকুলি করে। চোখ দুটো কেমন হয়ে উঠছে দিনে দিনে—যেন চাউনি দিয়েই কত কথা বলতে চায়। মাথার চুলগুলো ঝুপসি। জগাকে একবার খবর দিতে হবে। বাইরেটায় চেয়ার পেতে বসিয়ে চুলগুলো ছেঁটে দিয়ে যাবে।
৩
রজনীবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন সুবলকে। সন্ধেবেলা একটা ঘরে সাগরেদদের নিয়ে মজলিস বসান উনি। মেলা কারবার থাকলেও লোকটা যাকে বলে মাটির মানুষ। হেলায় মিশে থাকেন সুবলদের সঙ্গে।
রিক্সাটা বাইরে দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকতেই সুবল দেখল ওরই মতো আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। সকলেই রজনীবাবুর গাড়ি টানে—কেউ রিক্সা, কেউ ভ্যান, কেউ টোটো। হাতের গেলাসটা খালি করে অমায়িক গলায় রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর সব তোদের? কাজকম্ম ঠিকমতো চলছে তো, নাকি?
হ্যাঁ হু করে উত্তর দিল কেউ কেউ। কেউ বসতে যাচ্ছিল দুঃখের ঝাঁপি খুলে, কিন্তু নিপুণ কৌশলে ঢাকনাটা মাঝপথেই নামিয়ে দিয়ে, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন স্বরে রজনীবাবু বললেন, হ্যাঁ রে, হালে সব ব্যাঙ্কের এক্যাউন্ট খুললি না তোরা? বিনি পয়সার জনধন এক্যাউন্ট?
মাথা নাড়ল কেউ কেউ—হ্যাঁ, খুলেছে।
সুবলের মনে পড়ল, মাস-কয়েক আগে বাস ধরে ও আর আরতি গিয়েছিল বটে ভদ্রবেড়েয়। এ-অঞ্চলে ওখানেই একটা ব্যাঙ্ক আছে। দুজনে লাইন দিয়ে নাম তুলেছিল ব্যাঙ্কের খাতায়। এ-ও মিত্রবাবুরই হুকুমে। নইলে ওদের আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কী কারবার।কিন্তু সেসব কাগজপত্তর কি আর আছে?
রজনীবাবু বললেন, পাসবই-টইগুলো একটু বের করে রাখিস, দরকার আছে। ধাঁ করে বড়ো নোটগুলো সব বাতিল হয়ে গেল... ঘরে রাখতে হয় কিছু, সব তো একা গিয়ে জমা দিতে পারব না... মেলা কড়াক্কড়ি হচ্ছে... এখন তোরা যদি নিজেদের খাতায় দশ-বিশ হাজার করে ফেলে রাখিস... সময় করে পরে নয় তুলে নেব... কিছুই না, একদিন গিয়ে একটু লাইন দিয়ে ফেলে আসা—কাজ বলতে এই... সে তোদের শ-পাঁচেক করে দেব নয়...
রজনীবাবু সুবলদের মা-বাপ—ওর কথায় না বলে কার সাধ্যি। আর বলবেটাই বা কেন? একবার ব্যাঙ্কে যাও, পুট করে টাকাটা জমা করে এসো। ব্যাস। আর মাগনায়ও তো নয় রে বাবা। লোকটার দরাজ দিল। নইলে কি আর এমন তুচ্ছ কাজের জন্য পাঁচশো করে দেয়?
আর সকলে চলে গেলেও সুবল রয়ে গেল। রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর রে? ছেলেটা আছে কেমন?
ওই ধুঁকছে। তার ওপর শীতটাও পড়েছে জবর।
ফেলে কেন রাখছিস বাবা, বেলায় বেলায় অপারেশনটা করিয়ে নে না।
হ্যাঁ হ্যাঁ... এই নেব... বউ খুব চেষ্টা করছে...
‘বউ’ কথাটা শুনতেই একটু টনকো হয়ে বসলেন রজনীবাবু। বললেন, তোর বউও খুলিয়েছিল নাকি এক্যাউন্ট?
মাথা নাড়ে সুবল। ওই জনগণমন এক্যাউন্ট—হ্যাঁ, খুলল তো।
আছে? বাহ... বেশ... তা ওর খাতাতেও যদি আমার কিছু টাকা ফেলে দেয়...
নিশ্চয়ই দেবে—গদগদ হয়ে বলে ওঠে সুবল। তারপর দাঁড়িয়েই থাকে।
কিছু বলবি?
বলছিলাম কী, কালো-টাকা জিনিসটা কী রজনীবাবু?
কুঁতকুঁতে চোখ দুটো সুবলের মুখের ওপর স্থির করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন রজনীবাবু। ভুঁড়ির ওপর হাত বোলান।
আলটপকা কিছু বলে ফেলল নাকি সুবল? উনি কি দুঃখ পেলেন? নিজের ওপর ভারি রাগ হতে থাকে সুবলের। কবে যে একটু জ্ঞানগম্যি হবে ওর।
হঠাৎই হেসে উঠে, গদগদ স্বরে মস্করা মাখিয়ে রজনীবাবু বললেন, টাকার আবার কালো-সাদা কী রে, টাকা টাকাই।
মিত্রবাবু যে কালো-টাকার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছেন... সবাই বলছে...
আরে বাবা কালো-টাকা হল একটা বেড়াল।
বেড়াল?
হ্যাঁ। মাঝেমাঝে ঝুলি থেকে বের করো। পাবলিককে তার আদুরে ডাক শোনাও। আবার ঢুকিয়ে রাখো। ওই যে বলে না ‘সোনার পাথরবাটি’, আদতে হয় নাকি অমন কিছু? তেমনই। টাকার রং-টং হয় না। ধর কেউ খেটেখুটে কিছু জমাল, অমনি নজর পড়ে সরকারের। কেন রে বাবা, তোরটা নিয়ে তো আর জমাচ্ছি না, এ আমার খুন-পসিনা। এ-কথা ওই উঁচুতলার বাবুদের কে বোঝাবে। আসলে জিনিসপত্রের এত দাম বাড়ছে, তার ওপর বর্ডারে দেদার গোলাগুলি চলছে, গভারমেন্ট আর পারছে না বুঝলি। তাই তোর আমার কাছ থেকে চাঁদা তুলছে। এখন সরাসরি তো আর বাটি নিয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাই যত্ত ফিকির। কী, না—কালো-টাকা। ধুস।
টগবগে কথাগুলো মাথায় ভরে বেরিয়ে এল সুবল। একগাদা বক্তৃতা কিলবিলিয়ে দিলেন বটে রজনীবাবু, কিন্তু মিত্রবাবু যখন বলছেন নিশ্চয়ই একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে। এই কালো-টাকার পিছনে লাগতে গিয়েই তো ভরা বাজারে চোখের জল ফেলতে হল মানুষটাকে।
এই প্রথম মিত্রবাবুর ওপর একটু বেশিই বিশ্বাস হল সুবলের। অন্নদাতা রজনীবাবুর চাইতেও বেশি।
৪
বিকেলবেলা দুবাড়ি কাজের ফাঁকে একবার ঘরে যাওয়ার পথে আরতি দেখল একটা মিছিল বেরিয়েছে—ওই টাকাপয়সার ঝামেলা নিয়েই। সত্যিই খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে সব্বাই। পঞ্চাশ-একশোর নোট পুরো ডুমুরের ফুল। বহু পসারি ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। পাইকারের থেকে মাল তুলতে পারছে না, আবার বিকোতেও পারছে না তেমন। দোকান খুলে রেখে হবেটা কী? সুবলের সওয়ারিরও ভাটা পড়েছে। মাইনে বাবদ কটা একশো পেয়েছিল আরতি, আর গুটিকয় ছিল ওই কৌটোয়। হাত-টিপে চালিয়ে নিচ্ছে বটে, কিন্তু সে-ই বা আর কদ্দিন?
খবরের কাগজে, টিভিতে দেখাচ্ছে লম্বা লম্বা লাইন পড়ছে ব্যাঙ্কের সামনে। গঙ্গানগরে একটাই এটিএম—বাজারের কাছে। এমনিতে ফাঁকাই থাকে। এখন নাকি তার সামনেও পেঁচিয়ে উঠছে লাইন। এই তো কালই পাশের ঘরের সোনালি আর ওর ননদ গিয়েছিল এটিএম-এর লাইন দেখতে। ফিরে এসে আরতিকে বলে গেল—সাপের মতো বিশাল লাইন। জল-বাতাসা, ছোলা, মুড়ি-চানাচুরের ফিরিওলা ঘুরছে। সবাই একটা করে নোট পাচ্ছে—দুহাজারের। হেব্বি দেখতে মাইরি—টুকটুকে গোলাপি, ঠিক যেন লটারির টিকিট। তার ভেতর চুলের মতো সরু মেশিন বসানো। জাল করা যাবে না, কালো করা যাবে না, ঘুষ দেওয়াও যাবে না। এসব পাঁয়তারা মারতে গেলেই টপাটপ ধরা পড়ে যাবে।
দোকান-বাজারের চিন্তা নয়, আরতির সব ভাবনা শুধু লখুটাকে নিয়ে। এইবার ওকে ভর্তি না করালেই নয়। কিন্তু টাকাপয়সার কী বন্দোবস্ত হবে?
এক বুড়োবুড়ির বাড়িতে কাজ করে ও। সেই মেসো সব শুনে বললেন, একদিন ভোর-ভোর লাইন দিয়ে টাকাগুলো ব্যাঙ্কে ফেলে দাও। আগেতো ছেলেটার প্রাণ। জমা দিয়ে ফের তুলে নিতে হবে। কিন্তু চব্বিশ হাজারের বেশি তুলতে পারবে না। সব ফেলো না। সাড়ে চার হাজার টাকা বদলে দিচ্ছে। ন-খানা পুরোনো পাঁচশো বদলে নাও, বাকিটা এ্যাকাউন্টে ফেলো। তাহলেই মোটামুটি তিরিশ হয়ে যাবে। যেটুকু হল না, সেটা ওই পুরোনোতেই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। বলছে বটে হাসপাতালে পুরোনো নোট চলছে, কিন্তু সব খরচা তো আর ওখানে নয়। বাইরেও আছে। তাছাড়া, টিভিতে দেখছি কিছু কিছু হাসপাতালও নাকি বেগড়বাঁই করছে।
আরতির পক্ষে টপ করে যাওয়া মুশকিল। কাজের বাড়ি ছাড়াও লখুর দেখভাল আছে। খুঁজে-পেতে পাসবই বের করে সুবলকে একদিন টাকাপয়সা দিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেদিন জমা দিতে পারেনি সুবল। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে। ওকে দিয়ে হবে না। তাছাড়া ন্যালাখ্যাপা বরের হাতে টাকা-পয়সা দিয়ে একদম নিশ্চিন্ত হতে পারে না আরতি। নিজেই যাবে আরেকদিন।
লখুটার জ্বর এসেছে। আজকাল বারদিগরই আসে। যে ওষুধ পড়ে, তাই পড়েছে। কিন্তু এবারে ছাড়ছে না কিছুতেই। ছেলেটাকে একবার দেখতে আসছিল আরতি। মুখখানা থেকে থেকেই মনে পড়ে, কাজভুল হয়ে যায়। বুকের কষ্টে প্রায়ই রাতভর ছটফট করে বেচারা। ওকে চৌকিটা ছেড়ে দিয়ে, নিজেরা দুজনে মাটিতে শোয়। মাঝেমাঝে গিয়ে মশারিটা তুলে ছেলেটার বুকে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় আরতি। অন্ধকারে লখুর চোখ দুটো ধকধক করে।
এতদিন নয় রেস্তর সমস্যা ছিল। এখন, বলতে নেই, অনেকটাই জোগাড় হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন ঝামেলা এই নোট-বাতিল। চেনা নার্সদিদির সঙ্গে একবার দেখা করেছিল আরতি। ও বলল, হাসপাতালে পুরোনো নোট নিলেও ঝামেলা করছে কখনও। এছাড়া ওষুধের দোকান-টোকানগুলো তো নিতে চাইছেই না।
রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে মিছিলটাকে দ্যাখে আরতি। ওরা চেঁচাচ্ছে—মিত্রবাবু নাকি মিথ্যে বলছেন। সুবল একবার এসব শুনলে হয়। ও এখন বেশ তেতে আছে। মিত্রবাবু কোমর-বেঁধে লড়াই শুরু করছেন কালো-টাকার বিরুদ্ধে। তাকে দূর থেকেই সাথ দিচ্ছে গঙ্গানগরের রিক্সাওলা সুবল। রজনীবাবুর কৃপাধন্য সুবল সাধুখাঁ। আর লখুর বাবা সুবল সাধুখাঁ, তার কোনো দায় নেই বুঝি? দিনান্তে ফিরে সে তার ঠিকে-ঝি বউকে ব্যাখ্যান দিচ্ছে—এই প্রথম খুশিমনে লাইন দিচ্ছে গোটা দেশ, বুঝলে। কালো-টাকা সাফ করে ফেলতেই হবে। যারা যারা লাইনে দাঁড়াচ্ছে সব্বাই আসলে যুদ্ধু করছে। হ্যাঁ, লাইনে দিতে গিয়ে দু-একজন মরছেও বটে। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে বেজায় ঠান্ডার মধ্যে মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে থাকে না? তাদের জানের দাম নেই? কী পাহাড়ে কী এটিএম-এ—সব প্রাণই দেশের খাতিরে, বুঝলে!
হরবখত এসব শুনতে ভালো লাগে না আরতির। কাল তো মেজাজ হারিয়ে বলেই ফেলল, এই কালো-টাকার চক্করে যদি লখুটা মরে যায়, সেও কি দেশের জন্য যাবে? তখনও এমন থুড়িলাফ খাবে তো তুমি?
নিমেষে মিইয়ে যায় সুবল। আরতির বুকটাও মুচড়ে ওঠে। লখু শুনল কথাটা। সুবলের দিকে চেয়েও মায়া হয় খুব। ছেলেবেলায় নাকি একবার খুব জ্বর হয়েছিল ওর, সেই থেকে মাথাটা এমন।
এই যে মিছিলওলারা, ওরা কি জানে না পথেঘাটে চিল্লামেল্লি করে কিস্যু হবে না? জানে। তবু করছে। কারণ মিত্রবাবুর মতো ওরাও একটা হুজুক চায়। নইলে দিন কাটবে কেমন করে? উনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, এরা ওই কান্নার উল্টোবাগে চেঁচাচ্ছে। বলছে—গরিবের কষ্ট। ছোটো দোকানির কষ্ট। বুড়ো-হাবড়াদের ঝক্কি।আচ্ছা, যে বাড়ি থেকে পাঁচশো টাকার নোটে মাইনে আর লখুর চিকিৎসার জন্য ধার দিল ওকে, তাদেরও তো মিছিলে হাঁটতে দেখল আরতি; ওরা এইখানে কেন?
লেখাপড়া না জানলেও আরতি বোঝে—কালো-টাকা মানে ফাঁকির টাকা। গরিবের ভাত-মারা টাকা। কিন্তু এই ফাঁকিটা যারা মারছে, তারা পারছে কেমন করে? সেগুলো ধরতে পারছেন না মিত্রবাবু? কতদিন কত জায়গায় ও শুনেছে ওদের দেশ নাকি দিন-আনা দিন-খাওয়া লোকেদের। ওই কালো-টাকা না কী যেন, সেসব তারা পাবে কোত্থেকে? আজ যদি আরতির একটু কালো-টাকা থাকত, তাহলে কি চোখ মেলে অমনভাবে দেখতে হত শয্যাশায়ী ছেলেটাকে?
ভাসিমানুষের মতো ভেতর ভেতর হাত-পা ছোঁড়ে আরতি। চারদিক থেকে উঁচু দেওয়াল যেন এগিয়ে এগিয়ে আসছে, দমবন্ধ করে মেরে ফেলতে চায় ওকে। গঙ্গানগর থেকে কত দূরই বা ভদ্রবেড়ে। বাসে আধঘন্টা। সেইখানে ব্যাঙ্কে। আজ ওই রাস্তাটুকুও বড়ো অপার মনে হয় আরতির। সেই পথের শেষে ওর একমাত্র সন্তানের আরোগ্য। কবে ও ছুটি নিতে পারবে? কার কাছেই বা রেখে যাবে লখুকে? ওর জ্বরটা একটু না ধরলে যে যাওয়ার উপায় নেই।
৫
আচমকাই খুব বাড়াবাড়ি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হল লখুকে। ধুম জ্বর। নাকে অক্সিজেনের নল পরে এখন বেডে শুয়ে আছে ও। প্রেশারটাও ওঠাপড়া করছে। সব থিতু না হলে অপারেশন করবেন না ডাক্তারবাবু।
পঞ্চায়েত প্রধানকে ধরে-করে ব্যাঙ্কে বলে টাকাগুলো জমা করিয়ে দিয়েছেন রজনীবাবু। আরতিদের ছাব্বিশ, ওর চুয়াল্লিশ—দুটো একাউন্টে ভাগ করে। জমা দিয়েই চব্বিশ হাজার তুলে নিয়েছে আরতিরা। ঠিকই বলেছিল সোনালি—গোলাপি টুকটুকে নোট। কত সব জীবজন্তুর ছবি আঁকা। আরতি আর সুবল মিলে দুহাজার করে নোট বদলেও নিয়েছে। আগে বদলে দিচ্ছিল সাড়ে চার হাজার, এখন কমে দুই। আঙুলে ভোটের কালি লাগিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। এক লোকের দুবার বদলাবার উপায় নেই।
সমস্যাটা হচ্ছে অন্য জায়গায়। আরতি এখন শুধুই দুহাজারের নোটের মালিক। মাত্র দুখানা একশো আর একটা পঞ্চাশ পড়ে আছে। বাসে করে দেখতে যেতে হয় লখুকে, ভাড়া দেবে কেমন করে? একটা আয়া রাখতে হয়েছে। গোড়া থেকেই সে কড়ার করে রেখেছে—চার দিন অন্তর একশো-পঞ্চাশে তার টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।
মাঝরাত্তিরে মেঝের বিছানার ওপরে উঠে বসে আরতি। শব্দ করে শ্বাস ফেলছে সুবল। সারাদিন বড্ড খাটনি হয় মানুষটার। আজকাল ও টের পায় ছেলের জন্য বাপের ভাবনাও কম নয়, কিন্তু নিজের দুশ্চিন্তা বা মায়া প্রকাশ করবার উপায় জানে না মানুষটা। নইলে কাল অমন অদ্ভুত কথা কেউ বলে? অন্তত নিজের বউয়ের কাছে?
একফালি চৌকিটার ওপর এসে পড়েছে দুধসাদা চাঁদের আলো—ঠিক যেন লখু শুয়ে আছে! আরতির মনটা বড্ড কু গায়। চিন্তাটা সরাবার চেষ্টা করেও। সুবল কদিন থেকে থেকেই বলছিল, মিত্রবাবু চালটা যা চেলেছেন না, নাও ঠেলা বোঝো।
লখু হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে একেবারে চুপ মেরে গেছে।
কালো-টাকা সাদা-টাকা বাছবিচারের চৌহদ্দির বড্ড বাইরে এক স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীন পৃথিবীতে বেঁচে আছে আরতি সুবল সোনালিরা। ওদের এ টি এম কার্ড নেই, ব্যাঙ্কের খাতায় নিত্য লেনদেন নেই, নোটের মধ্যে মেশিন বসল কি না তাতে কিচ্ছুটি যায় আসে না। ওদের জীবন চলে খুচরোয়। চিমটের মাপে। আর তার চাকাটা ঘোরায় ভাত-রুটির দাউদাউ খিদে, ভোর ভোর উঠে এক-কাপ গরম চায়ের সুখ, শয্যাশায়ী সন্তানের জ্বলজ্বলে দৃষ্টির চাবুক। এখানে ভাঙতির বড়ো প্রয়োজন। বড্ড আকাল।
পাশে শুয়ে থাকা মানুষটাকে বোঝবার চেষ্টা করে আরতি। দুচোখ ভরে জল আসে। লখুর শোয়ার ভঙ্গিটা ঠিক ওর বাবার মতন। বড্ড সরল মানুষ সুবল। গঙ্গানগরের নিস্তরঙ্গ জীবনে আলেকালে দূরাগত কোনো ঢেউ এলে কেবল একটু ভিজতে চায়। এই তো দিন তিনেক আগে দিনান্তে বাড়ি ঢুকে তার সে কী দাপ—
রজনীবাবুর সব কালো টাকা, বুঝলে?
জানি তো।
লোকটাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না।
সে আবার কখনও যায় নাকি?
সুযোগ বুঝে কেমন আমাদের জনগণমন-য় টাকা ফেলে দিল!
দিল তো।
কিন্তু মিত্রবাবু সব খবর রাখেন। এর ব্যবস্থাও করেছেন উনি।
মানে?
উনি বলেছেন—যারা অন্যায়ভাবে অন্যে জনগণমন ব্যবহার করছে, তাদের টাকা ফেরত না দিতে।
না দিলে রজনীবাবু ছাড়বে?
কী করবে? মাথার ওপর মিত্রবাবু আছেন না?
বাৎসল্যের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে সেদিন চেয়ে ছিল আরতি। যেমন আছে এখন। সুবলের মাথার মধ্যে এখনও ছেলেবেলার জ্বর, বিপাকে পড়লে সে বুঝি জেগে ওঠে। বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দেয়।
কাল রাতে বাড়ি ফিরে বেশ গম্ভীর গলায় সুবল বলল, একটা কথা শুনলাম।
রুটি করছিল আরতি। বেলতে বেলতেই জবাব দিল, কী কথা?
না মানে... আমতা আমতা করছিল সুবল।
কী কথা শুনি?
চাটু নামিয়ে রুটিগুলো সেঁকতে শুরু করে আরতি। তার তিনটে, সুবলের পাঁচটা। লখুও খেত তিনটে। একটা কালু কুকুরের। ভুল করে রোজের মতো বারোটাই করে ফেলেছে আরতি।
বলবে তো নাকি।
না মানে... এখন অনেক ভাঙা টাকা দরকার...
হ্যাঁ, সে তো দরকারই।
শুনলাম...
কী শুনলে?—রুটিগুলো একে একে সেঁকে কৌঁটোয় চাপা দিয়ে রাখে আরতি।
শুনলাম, নিচুপটির দিকে নাকি খুচরো নোট পাওয়া যাচ্ছে। ওখানে সব চলছে। পুরোনো নোটও। যদি ওইখানে কাউকে গিয়ে একবার বলি, মানে লখুর কথা শুনে যদি বদলে দেয়...—এক-নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামে সুবল।
হাত শ্লথ হয়ে আসে আরতির। শরীর ছেড়ে দেয়। আঁচে-ধরা রুটির গায়ে কালো ছোপ ফোটে। থাক। কয়েকখানা রুটি বেশিই আছে। উপরি যা থাকে, সবই তো কালো। যাক, পুড়ে যাক।
ও সুবলকে বলতে চায়, নিচুপটি! শেষে ওই খারাপ মেয়েগুলোর পাড়ায় ছেলের চিকিৎসার টাকা ভাঙাতে যাবে তুমি!
ভদ্রঘরের লোকজনও-পাড়ার নাম পারতপক্ষে মুখেই আনে না। নিভু নিভু আলোর একটা গলি ফুটে ওঠে আরতির চোখে। হাসির ছর্রা উঠছে থেকে থেকে, জড়ানো গলায় খিস্তি-খেউড় করতে করতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষের দল। মরা প্রদীপের মতো শ্বাসরোধী ঘ্রাণ ভরে তুলেছে বাতাস।
কিন্তু বাক হরে যায় আরতির। লখুর মুখটা ভেসে ওঠে। গরম রুটির গন্ধ বড্ড ভালোবাসত ছেলেটা। বাসত কেন, বাসে। মনটা কেন যে এত কু গায়।
লখুকে কি শুধু আরতিই ভালোবাসে? ওর বাপ নয়? নেহাত আতান্তরে পড়ে ভেবেছে এমন। শরীরটা আচমকাই ঠান্ডা দিঘির মতো বড়ো আর গভীর হয়ে সব রোষ শুষে নেয়। পোড়া রুটিটা নামিয়ে নতুন একটা চাপায়। চোখে আটার গুঁড়ো পড়ল নাকি, কেমন কটকট করে। ওদের অনটনের সংসারে ওই একখানা রুটির পুড়ে যাওয়াই যেন আরতির সমস্ত উত্তর। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে সুবল। ওর এ রূপ বড্ড অচেনা।
কাল থেকে অনেক ভেবেছে আরতি। যত দিন গড়াচ্ছে সুবলকে বড্ড বড়ো মনে হচ্ছে ওর। রজনীবাবুর চেয়ে বড়ো, কাজের বাড়ির ওই দাদা-বৌদি যারা মিছিল করছিল—তাদের চেয়ে, এমনকি দেশের রাজা মিত্রবাবুর চেয়েও বড়ো। বালিশের নীচ থেকে লালচে নোটগুলো বের করে আরতি। বরকে কিছু না বলে কাল ও নিজেই নিচুপটির দিকে যাবে একবার। ওইখানে তো কালো-সাদা-লাল বলে কিছু নেই। সব শুনে যদি বদলে দেয় কেউ।