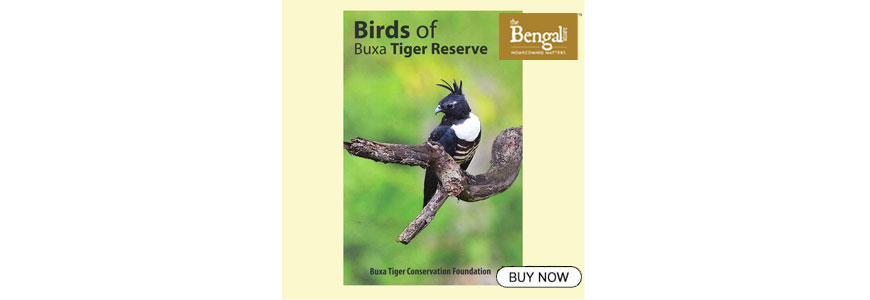মেরিকামায়া সাতকাহন : কার্বনডেলে আমার পিএইচডি প্রবল ঝড়ের মধ্যে ডিঙি নিয়ে পদ্মা পার হওয়া

নেকার্স বিল্ডিং, যেখানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি শিখেছিলাম
আমার মাস্টার্স ডিগ্ৰী যদি কামারের গনগনে লাল হাপরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, কার্বনডেলে আমার পিএইচডি প্রবল ঝড়ের মধ্যে ডিঙি নিয়ে পদ্মা পার হওয়া তো বটেই। এবং সে ঝড় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা ঝড়। পলিটিক্যাল ঝড়।
ডিপার্টমেন্টে আমার সম্মান তৈরি করেছি আমি নিজেই। প্ল্যান্ট বায়োলজি অর্থাৎ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ডক্টরেট ছাত্র হিসেবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক হিসেবে আমার একটা সুনামও গড়ে উঠেছে।
আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে একটু বলতেই হবে, না হলে অনেকেই বুঝতে পারবে না।
আমাদের দেশে পিএইচডি করতে গেলে সেই চার পাঁচ বছর বাধ্যতামূলক কোনো ক্লাস নিতে হয় না। শুধু রিসার্চ করলেই হলো। হয়তো ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার এটাও একটা ফেলে যাওয়া অবশিষ্টাংশ। আমরা এমএসসি পড়ার সময়ে যা ক্লাস নিয়েছি, তারপরে কোনো ক্লাস নিতে আমাদের বাধ্য করা হয়নি। ওখানে যে কয়েক বছর পিএইচডি’র কাজ করেছি আমেরিকায় চলে আসার আগে, সে সময়ে কোনো ক্লাস আমাদের নিতে হয়নি। আমাদের বললাম এই কারণে যে মুক্তি ওখানেই অধ্যাপক নির্মলেন্দু সমাজপতির কাছে পিএইচডির গবেষণা করেছিল, এবং শেষ করেছিল। আমি করিনি একাশি সালে সুন্দরবন হাজি দেশারৎ কলেজে চাকরি পেয়ে যাওয়ার কারণে।

আমি প্রথম প্লুটিউস মাশরুম পোর জার্মিনেট করার কৌশল আবিষ্কার করি ল্যাবরেটরিতে
মুক্তির পিএইচডি ডিগ্ৰী পাওয়ার গল্পটাও সংক্ষেপে এখানে বলতেই হবে। থিসিস জমা দেওয়ার পরে এক প্রাগৈতিহাসিক নিয়মের ফলে এক্সটার্নাল কোনো এক অধ্যাপকের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস পাঠানো বাধ্যতামূলক। যাঁকে নির্বাচিত করা হয় বিদেশ থেকে। এইভাবে তিনজন থিসিস ইভ্যালুয়েটরের মধ্যে একজন থাকেন অন্য দেশের। মুক্তির থিসিস দুবার দুজন বিদেশী স্কলারের কাছে পাঠানোর পরেও তাঁরা নানা কারণে সে কাজ করতে পারলেন না। সুতরাং, মুক্তি যখন ছিয়াশির আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলো, তখন বিরাট সমস্যা। থিসিস জমা দেওয়া হয়ে গেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু শেষ এগজামিনারের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বলে ডিগ্ৰী পাচ্ছে না।
এই অবস্থায় আমি আমার ডিপার্টমেন্টে বলে কয়ে রাজি করালাম ওর তৃতীয় পরীক্ষক যেন এস আই ইউ থেকে নির্বাচিত করা হয়, এবং ফাইনাল মৌখিক পরীক্ষা – দেশে যাকে বলে ভাইভা ভসি এবং আমেরিকায় যাকে বলে ওরাল ডিফেন্স – তা যেন এখানেই নেওয়া হয়। অনেক চিঠি লেখালেখির পর ওর থিসিসের একটি কপি শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছোলো, এবং আমাদের দু’জন অধ্যাপক সে থিসিস পড়ে ওকে একদিন ডেকে পাঠালেন ভাইভা পরীক্ষা করার জন্যে।
তারপর তিন ঘণ্টা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে ও যখন পরীক্ষকদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দেখে মনে হলো ওর বয়স তিন বছর বেড়ে গেছে। না, পরীক্ষায় পাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু যেসব প্রশ্ন ওকে করা হয়েছে, ওই যে আগেই বলেছি ক্রিটিকাল থিংকিং, সেসব আমাদের দেশে মৌখিক পরীক্ষা হলে ওকে নিশ্চিতভাবেই কখনো করা হতো না।
বায়োলজির পিএইচডি হতে গেলে শুধু যে বায়োলজি জানলেই চলে না, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, অঙ্ক, এনভায়রনমেন্টাল বিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক কিছুই জানতে হয়, শিখতে হয়, আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে কেবলমাত্র একটা ওরাল পরীক্ষা দিতে গিয়েই ও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলো। অথচ, মুক্তি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী, এবং আমার থেকে কেমিস্ট্রি ওর অনেক ভালো জানা ছিল। আমার কেমিস্ট্রির দৌড় হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত, আর অঙ্কে ফেল করতে করতে কোনোরকমে পাশ করে গিয়েছিলাম সে পরীক্ষায়।

প্রফেসর জন বাজোলা, যিনি আমাকে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি শিখিয়েছিলেন
আমাদের কোনো দোষ নেই। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বিশ্লেষণ শেখায়নি। শুধু মুখস্থ করতে শিখিয়েছে।
এসব কথা বললাম একটাই কারণে। পিএইচডি করার সাড়ে চার বছরের মধ্যে প্রথম আড়াই কি তিন বছর রিসার্চের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে একটানা হাজার ক্লাস আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছে। তার ওপরে জীবনধারণের জন্যে সপ্তাহে বাধ্যতামূলক কুড়ি ঘণ্টা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের কাজ তো আছেই।
কোনো ক্লাসই আবোল তাবোল ক্লাস নয়। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির মতো এখানে আমি সিনেমার ক্লাস, সাঁতারের ক্লাস এসব নেওয়ার কোনো ফুরসৎই পাইনি। পিএইচডি ছাত্র মানে এদেশে একদিকে যেমন খুব সম্মান, তেমনই আবার মাথার ওপর বিশাল বোঝা। সাবজেক্টকে অন্তর থেকে ভালো না বাসলে, এবং নিবেদিতপ্রাণ না হলে এদেশে পিএইচডি করা অসম্ভব।
রাত জেগে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কীভাবে চালাতে হয়, তা শিখলাম। একটাই বিরাট সুবিধে, চাবি থাকে সঙ্গে। নেকার্স বিল্ডিং আমাদের প্ল্যান্ট বায়োলজি বিল্ডিঙের পিছনের দিকে। রাত দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে নেকার্স। আগে থেকেই পাঁচ কিংবা ছ’জন স্টুডেন্টের রুটিন করা আছে – কে কবে সে জটিল মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করবে। রাত দুটো কিংবা তিনটে পর্যন্ত প্রোজেক্টের কাজ করে শুনশান রাস্তায় ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরে এসে তিন চার ঘণ্টা নিদ্রা। আবার আটটার সময়ে শিশুকন্যাকে তার ডে কেয়ারে নামিয়ে দিয়ে, মুক্তিকে তার ডিপার্টমেন্টে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে আসবো আমার চারশো এক নম্বর ঘরে – অর্থাৎ চারতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথম ঘর। নিজের ক্লাস আছে, পড়ানো থাকে সপ্তাহে দু তিন দিন। খাতা দেখা থাকে। তারপর সব শেষ হলে রিসার্চ নিয়ে বসা।

ড. রেমন্ড স্টটলার, বিখ্যাত ব্রায়োফাইট বিশেষজ্ঞ

ড. বারবারা স্টটলার, বায়োলজির অসাধারণ অধ্যাপিকা
এই করতে করতে অষ্টআশির জানুয়ারি থেকে নব্বইয়ের ডিসেম্বর পর্যন্ত কেটে গেলো। রেমন্ড স্টটলারের সেই ক্লাসের কথা আগেই বলেছি, যেখানে আমি একমাত্র ঢুলন্ত ছাত্র। সান্ডবার্গের অ্যাডভান্সড মাইকোলজি বা ছত্রাকবিদ্যার ক্লাস তো আছেই। তার লেকচার এবং ল্যাব। এবারে আরবানা-শ্যাম্পেনের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় থেকে টেনিওর না পাওয়া বছর পঁয়ত্রিশের ছোকরা অধ্যাপক ড্যানিয়েল নিক্রেন্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়ে এলেন। শুনলাম, তিনি নাকি মলিকুলার বায়োলজি শেখান। যদিও সান্ডবার্গ এসব ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে কখনো কোনো উৎসাহ দেখাননি, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। প্রফেসর ম্যাটেনের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমি নতুন প্রফেসরের মলিকুলার ট্যাক্সনমির ক্লাস নিয়ে ফেললাম, এবং তাঁর ল্যাবে সে সময়কার কাটিং-এজ টেকনোলজি আইসোজাইম, ব্লটিং ইত্যাদি শিখে ফেললাম। নিক্রেন্ট খুব খুশি। এলিট শ্বেতাঙ্গ প্রফেসর আমার সঙ্গে তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা এক কালো চামড়ার মানুষের সঙ্গে যতটা পরিহাস করা যায়, তাও করতে শুরু করলেন। আমাকে অবশ্য দেখাতে হলো তাঁর সে জোক আমি যথেষ্ট উপভোগ করছি।

কত প্রজাতির ছত্রাক। সান্ডবার্গ ও আর এক সতীর্থ – হাতে এক বিশেষ প্রজাতির শ্যানটারেল
রিসার্চ প্রোপোজাল তৈরি হলো, সে প্রোপোজাল ডিপার্টমেন্টে পাশ করানো হলো, এবং এবারে আমি পূর্ণ উদ্যমে গবেষণার কাজ শুরু করলাম। প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। সাড়ে চার বছর পরে ডিপার্টমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি আর কোনো আর্থিক সহায়তা দেবে না। অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ আর পাওয়া যাবে না।
ভাগ্য ভালো, শেষ বছরটা আমি আমার জমা দেওয়া সায়েন্টিফিক পেপার ও রিসার্চ প্রোপোজালের ভিত্তিতে এস আই ইউ থেকে একটা ডিসার্টেশন রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেলাম। তার ফলে শেষ একটা বছর আমাকে কোনো কাজ করতে হয়নি। শুধু মন দিয়ে গবেষণার কাজ করে গেছি।
রাজনৈতিক ঝড় এলো সান্ডবার্গের দিক থেকেই।
একদিন তিনি আমাকে ল্যাবে একা পেয়ে বললেন, “ইউ নো, টিম ইজ স্মার্টার দ্যান ইউ।” আমি তো শুনে হতবাক।
প্রথম থেকেই ভদ্রলোকের ধারণা ছিল, তাঁর শ্বেতাঙ্গ মাস্টার্স ছাত্র টিম বেগান আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। এই টিম ও তার গার্লফ্রেন্ড শ্যারনের কথা আমি আগেই লিখেছি। টিম খুব ভালো ছেলে, শ্যারন খুব ভালো মেয়ে, এবং আমার সঙ্গে তাদের খুব ভালো বন্ধুত্ব। কিন্তু তারা আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কিনা, এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে কখনো হতে হবে বলে ভাবিনি।

ড. লরেন্স ম্যাটেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, যিনি ছিলেন আমার আসল ফ্রেন্ড, ফিলোজফার ও গাইড
আমাদের দেশে এসব তুলনা আখছার হয়ে থাকে, এবং প্রকাশ্যেই একজনের সামনে আর একজনকে মাথায় তোলা বা নীচে নামানো, এসব আমি সেই ইস্কুলজীবন থেকেই দেখে আসছি। কিন্তু এদেশে এরকম হয় না – বিশেষ করে ভারতীয় কমিউনিটির বাইরে একেবারেই হয় না।
মাথাটা গরম হয়ে গেলো। কিন্তু মাথা যে করেই হোক ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কারণ এই লোকটার হাতেই আমার জীবন এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে। চেপে গেলাম।
তারপর দেখা গেলো আসল চক্রান্ত কী। সান্ডবার্গ আমাকে নিয়েছিল নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে। তার কোনো পিএইচডি ছাত্র ছিলো না কখনো, এবং সেই কারণে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে ফুল প্রফেসর পদে তার প্রমোশন হচ্ছিলো না। আমাকে নিয়ে দু বছরের মধ্যেই তার প্রমোশন হয়ে গেলো। তখন আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই তার সুবিধে, কারণ পিএইচডি ছাত্র থাকা মানে অনেক বেশি পরিশ্রম করা। তার ওপর আমার মতো একজন যে ইন্ডিয়া না কোথা থেকে এসে ডিপার্টমেন্টে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তৈরি করে ফেলেছে, এবং নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। আমি খবরের কাগজে কেন এতো লেখালেখি করি, এবং পড়াশোনার বাইরে, ফাঙ্গাস সম্পর্কিত পড়াশোনার বাইরে আমি আর কোনো আলোচনা কেন করি – সান্ডবার্গ-টাইপের প্রফেসররা কোনোকালেই তা পছন্দ করে না।

আমি প্রথম প্লুটিউস মাশরুমের টিস্যু কালচার করি সফলতার সঙ্গে। কিন্তু স্যান্ডবার্গ পেটেন্ট নিতে দিলেন না
ল্যারি ম্যাটেন, রেমন্ড আর বারবারা স্টটলার এরা না থাকলে আমার পিএইচডি ওখানে হতো না। আমাকেও সেই মঞ্জুলা আর মোস্তাফিজের মতো মাথা নীচু করে দেশে ফিরে যেতে হতো অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে।
ডিপার্টমেন্টে তখন কয়েকজন নতুন ইয়ং প্রফেসর এসেছেন। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের কেটি ক্লার্ক প্ল্যান্ট ফিজিওলজি পড়ান, এবং আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেছেন। তিনি আবার সান্ডবার্গের বান্ধবী, বোঝা যাচ্ছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকের যুবতী বান্ধবী – বৃদ্ধা স্ত্রী জ্যানেটের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছে। শেষ পর্যন্ত তাদের ডিভোর্সই হয়ে গেলো। এই কেটি ক্লার্ক আমার পক্ষে থাকায় শেষ পর্যন্ত সেই ডিঙি নিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পদ্মা মেঘনা ডাকাতিয়া আমি পার হতে পেরেছিলাম। আর অবশ্যই গুরু লরেন্স ম্যাটেন।
কম্প্রিহেন্সিভ পরীক্ষায় বসতে হলো। আমার রিসার্চ কমিটি তৈরি হয়েছে, এবং পাঁচজন প্রফেসর যেখানে থাকার কথা, সেখানে সান্ডবার্গ সাতজনকে নিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে। তিন দিন ধরে লিখিত পরীক্ষা দিলাম। ফল বেরোলো।
আমাকে ডেকে ম্যাটেন বললেন, “গুড নিউজ, অ্যান্ড ব্যাড নিউজ।” বলে, টাক মাথায় একটু হাসলেন।
বুক দুরুদুরু করতে লাগলো।
“ইউ প্যাসড সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ ইওর প্রিলিমস। ইন টু উইকস, ইউ উইল নীড টু টেক দ্য আদার থার্টি পার্সেন্ট।”
(চলবে)
*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে চলছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।
ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।
‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।