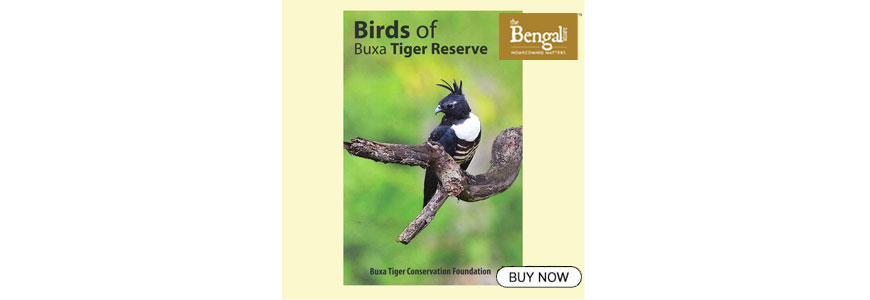মেরিকামায়া সাতকাহন : কে বাঁচালো আমাকে সে অন্ধকার রাতে নিশ্চিৎ মৃত্যু থেকে?

এমন এক রাস্তাতেই জীবন চলে যেতে পারতো সেদিন
সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু হতে পারতো।
পরে এই ঘটনা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু কখনো লেখার সুযোগ পাইনি। এই স্মৃতিকথায় লিখে রাখছি সে রাতের গল্প।
অনেকেই এসব কথা আর মনে করতে চাইবে না। তীব্র দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথা মানুষ যেমন মনে করতে চায় না, কারণ হৃদয়ের পুরোনো ক্ষতে নতুন করে রক্তপাত ঘটানোর কী দরকার? ঠিক সেইরকম, পুরোনো ভয়ের কথা, আতঙ্কের কথা, দুর্ঘটনার কথাও মানুষ মনে করতে চায় না। ভুলে যেতে চায়, ভুলে থাকতে চায়।
ইংরিজিতে একটা কথা আছে, “টাইম ইজ দ্য বেস্ট হীলার” – অর্থাৎ, সময় হলো দুঃখের, কষ্টের, ট্রমার সবচাইতে বড়ো প্রলেপ। আস্তে আস্তে মানুষ ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে। এই নতুন জীবন শুরুর রাস্তায় সময়ই তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু।
আমিও তাই করেছি। মায়ের অসময়ে ক্যানসারে মৃত্যুর কথাও স্মৃতির অনেক গভীরে ডুবে গেছে। ছোটোমামা বুদ্ধদেবের পিস্তলের গুলিতে খুনও তাই। শৈশবের বন্ধু সুব্রতর আত্মহত্যাও তাই। ভুলে যাইনি, কিন্তু মনকে শিখিয়েছি কেমনভাবে সেসব তীব্র দুঃখের কথাকে চেতনার খোলা শো-কেস আলমারি থেকে অবচেতনের গোপন সিন্দুকে জমিয়ে রাখা যায়।
খুব দরকার না হলে সে সিন্দুক খোলার আর কোনো প্রয়োজন নেই।
তেমনই দুর্ঘটনার স্মৃতিগুলো। সেই যে একবার দেশবন্ধু পার্কে আরএসএসের রুট মার্চ শেষ হবার পরে বাবার সঙ্গে হেঁটে ফিরছিলাম রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট দিয়ে। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা প্রাইভেট বাস ছুটে গেলো, আর দেখলাম তাতে বসে আছে আমার সে সময়কার সংঘী বন্ধু হরিশ চোপরা। আমি কোনোকিছু না ভেবে, বাবাকে কিছু না বলেই “হরিশ হরিশ” বলে দৌড়ে সেই দ্রুতগামী বাসে উঠতে গেলাম, এবং ভারী বুট পরা পায়ে চলন্ত বাসে উঠতে না পেরে রাস্তায় উল্টে পড়লাম। বাবা ছুটে এলো আমার দিকে। সেদিনও আমার জীবন চলে যেতে পারতো। আরএসএসের সেই হাস্যকর ঢোলা খাকি হাফপ্যান্টের একটা কোণা দিয়ে বাসের চাকাটা একটা কালো দাগ ঘষে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।
এই আবেগতাড়িত মনোভাব আমার জীবনের নানা ক্ষতি করে গেছে। অপূরণীয় ক্ষতি। যুক্তি নেই, সংহত চিত্ত নেই। শুধু আবেগ।
যাই হোক, আরএসএস ছেড়ে বহুকাল বেরিয়ে এসেছি, এবং জীবনটা তার পর থেকে একটু শান্ত, সংযত, বুদ্ধিপ্রভ হয়ে উঠেছে মনে হয়। সে সময়কার আমি আর আজকের আমি – একেবারেই আকাশ পাতাল তফাৎ।
এই বিশ্লেষণটা করার দরকার ছিল। জীবনকাহিনিতেই এই বিশ্লেষণ থাকার কথা।

আমি, মা, বাবা আর বোন
সে রাতের দুর্ঘটনা আমার এবং ল্যাব পার্টনার টিমোথি দুজনেরই জীবন শেষ করে দিতে পারতো। বিপদতারণ ঈশ্বরে কোনোকালেই বিশ্বাস করিনি, কারণ ওই যে মৃত্যুগুলো চোখের সামনে দেখেছি সারা জীবন ধরে – দেশে এবং বিদেশে – কোনো ভগবান আল্লাহ গডকে সে মৃত্যুগুলো বন্ধ করতে দেখিনি। ঈশ্বর আল্লাহ রাম থাকুন বা না থাকুন, মানুষের জীবন বাঁচাতে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। হিরোশিমা নাগাসাকির পরে আর কোনো সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশই আমাদের নেই। শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।
কিন্তু ধর্মের চতুর ব্যবসায়ীরা আমাদের সে কথা বুঝতে দেবে না। আজকের নয়া-ধর্মান্ধতার দিনে মানুষ আরো বেশি যুক্তিহীন, প্রশ্নহীন হয়ে পড়েছে।
কে বাঁচালো আমাকে সে অন্ধকার রাতে নিশ্চিৎ মৃত্যু থেকে?
গাড়িটা রাত এগারোটা কিংবা সাড়ে এগারোটার সময়ে মিসৌরি স্টেট লাইন পার হয়ে দক্ষিণ ইলিনয়ের জনশূন্য হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো। দারিদ্র্যপীড়িত এসব জায়গায় হাইওয়েতে পঞ্চাশ কি একশো গজ পর পর আলো নেই। অন্ধকার রাস্তা। গাড়ির হেডলাইট একমাত্র সম্বল।
আমেরিকা মানেই এ টেল অফ মেনি সিটিজ – এ কথা আগেও বলেছি। এই লেখার সময়েই বাফালো এলাকায় ভয়াবহ ব্লিজার্ডে অন্ততঃ ষাট সত্তর জন গরিব আমেরিকান মারা গেছে। বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে অনেক। তুষারঝড়ে গাড়ির মধ্যে আটকা পড়ে মারা গেছে আরো অনেক।

দক্ষিণ ইলিনয়ের গ্রামাঞ্চলের হাইওয়ে
টিভিতে এবং অনলাইন মিডিয়াতে এই ঝড়ের খবর ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন সব চিত্তাকর্ষক খবর প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সে নিউ ইয়র্ক টাইমসই বলুন, আনন্দবাজার-বর্তমানই বলুন, বা সিএনএন, ফক্স অথবা টাইমস নাও। সোশ্যাল মিডিয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। মিডিয়া মডেলটা একই সর্বত্র। কিন্তু কোনো জায়গায় একটাও আলোচনা হয়নি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতি-ধনী দেশে এই দুর্দশা। কেন এতোজন মানুষ মারা গেছে? তারা কারা? কীভাবে তারা আমেরিকায় থাকে? তাদের দারিদ্র্যদশা কতখানি তীব্র?
বাফালো হলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাবার ঠিকানা। লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে যায়, এবং ভারতীয় ও বাঙালিরা খুব বেশি যায়। কিন্তু কেউ বাফালোর দারিদ্র্য নিয়ে একটা কথাও বলে না। কারণ, ওসব নিয়ে কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই। মিডিয়াও এই মানসিকতা খুব চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছে। অথচ, সে আলোচনাটাই এই মুহূর্তে হওয়া উচিৎ ছিল। আমি বাফালোতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি সেখানে শহরের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, যাকে আমার বন্ধু ডাক্তার মাইকেল ইয়েহ নাম দিয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ডিভাইড। অর্থাৎ, এই রাস্তার একদিকে বাফালোর হতদরিদ্র লোকেরা ও তাদের পরিবারগুলো থাকে, আর অন্যদিকে বড়োলোকরা। এই তথাকথিত “ব্লিজার্ড অফ দ্য সেঞ্চুরিতে” বাড়ি গাড়ি জীবন সবকিছুর ধ্বংস হয়েছে – বুঝতেই পারছেন এই রাস্তার কোনদিকে। কিন্তু মূলস্রোত মিডিয়ার কাঁদুনি গাওয়ার দিনেও এই টেল অফ টু সিটিজ নিয়ে কোনো কথা নেই। অর্থাৎ, মানুষকে চিত্তাকর্ষক খবর বিক্রি করে মুনাফা করো, কিন্তু আসল খবরটা কখনো দিও না।
আমেরিকায় দশ লক্ষ মানুষ কোভিডে আজ মৃত – সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এখানেই মারা গেছে। সেখানেও সেই একই গল্প।
যাই হোক, সেদিনকার কথা বলি এখন অন্য প্রসঙ্গ রেখে।
রাস্তায় আলো ছিলো না, শিকাগো, নিউ ইয়র্ক কিংবা সেন্ট লুইসের মতোও রাস্তা চওড়া ছিলো না, এবং সারাদিনের কনফারেন্সের পর আমরা দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। তার মধ্যে সে সময়ে সেল ফোনও ছিলো না যে কারুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ড্রাইভ করবো। দূরপাল্লার ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা তেমন হয়নি তখনো। কেউ বলে দেয়নি রাতে গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে অবশ্যই জেগে থাকার জন্যে জল খাবে, গান শুনবে রেডিওতে, আর বিশেষ করে সঙ্গে যে আছে, সে যেন গল্প করে, কথাবার্তা বলে ড্রাইভারকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে।

এই রকমই এক প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপুজো থেকে ফেরার সময়ে
টিম এটিনজার আমেরিকায় বড়ো হওয়া ছেলে, কিন্তু দৃশ্যতই সে এই বেসিক নিয়মগুলো সম্পর্কে কিছু জানতো না। সে আমার পাশে বসে বসে ঢুলছিলো। আর আমি ক্লান্ত শরীরে একা একা মাঝরাতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কিংবা হয়তো টিম ভেবেছিলো, পাণ্ডা পার্থার হেল্প দরকার নেই। হয়তো আমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি সে একটু অতিরিক্ত আস্থা রেখেছিলো।
যাই হোক। দেশের কায়দায় অন্যকে দোষারোপ করে লাভ নেই। দোষটা আমার। আমি শুধু যে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলাম তাই নয়। নির্দোষ টিমের জীবনও সেদিন চলে যেতে পারতো। ওর মেক্সিকান-আমেরিকান বউ আবার সে সময়ে অন্তঃসত্ত্বা। আমার বাড়িতে স্ত্রী এবং শিশুকন্যা অপেক্ষা করে আছে।
পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাইল গতিবেগে গাড়িটা যাচ্ছিলো। দক্ষিণ ইলিনয়ের সেসব রাস্তায় তার থেকে বেশি জোরে গাড়ি যায় না। হয়তো সেটাও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিউ ইয়র্ক কিংবা শিকাগোর হাইওয়েতে সত্তর আশি মাইল স্পীডে গাড়ি যায়। ভাগ্যিস, ওখানে স্পীড লিমিট অনেক কম।
রাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ার সময়ে নিসান সেন্ট্রা উল্টে যেতে পারতো। কোনো গাছে প্রবল গতিতে ধাক্কা দিতে পারতো। রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে জলে ডুবে যেতে পারতো। কাদায় আটকে যেতে পারতো। আমার যদি আঘাত লাগতো মাথায়, তাহলে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকতো না।
কত কীই তো হতে পারতো। আমি বাংলা দেশে, কলকাতায় না জন্মে পাকিস্তান, সোমালিয়া কিংবা ব্রেজিলের বৃষ্টি অরণ্যের আদিবাসী হয়ে জন্মাতে পারতাম। বাংলায় কথা না বলে সোয়াহিলি কিংবা টোগালোগ ভাষায় কথা বলতে পারতাম।
কিন্তু আমি প্রবল মনের জোরে স্টিয়ারিং ধরে থেকেছি। গাড়িটা প্রবলভাবে এক পাক ঘুরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আবার। আমি সেই অবস্থাতেই রাস্তার ঢাল দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসে আবার হাইওয়ের ওপরে এনে দাঁড় করালাম আমাদের মেরুন রঙের নিসানকে। অবশ্য তার পরেও পিছন থেকে আর একটা গাড়ি বা ট্রাক এসে আমাদের পিষে দিয়ে যেতে পারতো।
কিন্তু ওই যে বললাম, কত কীই তো হতে পারতো জীবনে। হয়নি। এখনও বেঁচে আছি। ঈশ্বর, আল্লাহ, রাম, কৃষ্ণ, জিহোভা, বুদ্ধ ... অথবা, শুধু বুদ্ধি।
টিম আর আমি বাকী রাস্তাটা শান্তভাবেই কথাবার্তা বলতে বলতে কার্বনডেল ফিরে এলাম শেষ রাতে। না, টিম আমাকে স্যু করে দেয়নি। আমার সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টে রসালো গল্প জুড়ে দেয়নি। আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেনি। আমাকে একটাও খারাপ কথা বলেনি।
গাড়িটা রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায়নি। পরের দিন সকালে উঠে দেখলাম। একটা পাশে একটা বিরাট ডেন্ট।
মুক্তি বুঝেছিলো, আমি যে ফিরে এসেছি অক্ষত শরীরে, এই ঢের।
(চলবে)
_____________________
*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে চলছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।
ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।
‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।