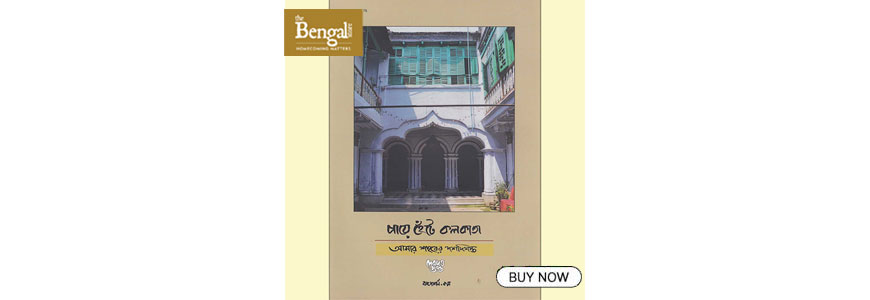মেরিকামায়া সাতকাহন : সারাদিন ঠাণ্ডায়, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভুল হয়ে গেল ভীষণ

আই এস ইউ ক্যাম্পাস
আমেরিকায় চুম্বন ও নগ্নতার গল্প? বলতেই হবে। তবে, না, সেসব কথা বলার আগে আরো কিছু কথা বলে ফেলি।
আত্মজীবনী যদি সম্পূর্ণ সত্য না হয়, তাহলে সে আত্মজীবনীর দাম কী? সুখের কথা বলতে হবে, দুঃখের কথা, স্বপ্নের কথা, ব্যর্থতা, হতাশার কথা – সবকিছুই বলতে হবে খোলাখুলি।
দেশের জীবনকাহিনি লিখেছিলাম অনেক যত্ন করে। দুহাজার পনেরো সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার অক্সফোর্ড বুক স্টোরে রীতিমতো সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল “ঘটিকাহিনি”। মিডিয়া, টিভি ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইটের ঝলকানি। রাবণ প্রকাশনার সোমাইয়া আখতার ও সৌরভ দাশগুপ্ত একটা জমকালো উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। সমরেশ মজুমদারের আসা শেষ মুহূর্তে হয়ে উঠলো না। তার বদলে এসেছিলেন ব্রাত্য বসু, বিখ্যাত সঙ্গীতকার দেবজ্যোতি মিশ্র, লেখক-লেখিকা দম্পতি অরুণ সেন ও শান্তা সেন, আর বইমেলার কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। ত্রিদিব আবার আমার সেই বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় থেকে অনুজপ্রতিম বন্ধু। ত্রিদিব, উদয়ন, কৃষ্ণ, মঞ্জু, হেলেন, মীনাক্ষী -- এরা সব আমাদের সঙ্গেই পিকনিক যেতো, রি-ইউনিয়নে নাটক করতো। সিন্ধি মেয়ে মঞ্জু ওয়াধওয়া কলকাতাতেই বড়ো হয়েছে। আমার গান ভালোবাসতো খুব।
 অক্সফোর্ড বুক স্টোরে ঘটিকাহিনির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে অধ্যাপক শূলপানি ভট্টাচার্য্য, রফিকুল ইসলাম, ও মতিয়ুর রহমান। আর সঙ্গে আছে আমার মেয়ে নন্দিনী
অক্সফোর্ড বুক স্টোরে ঘটিকাহিনির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে অধ্যাপক শূলপানি ভট্টাচার্য্য, রফিকুল ইসলাম, ও মতিয়ুর রহমান। আর সঙ্গে আছে আমার মেয়ে নন্দিনী
উদয়নের সঙ্গে এই সেদিনই কলকাতায় দেখা হয়েছে।
সমরেশ মজুমদার আর বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ঘটিকাহিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বুদ্ধদা পরেও আমার সে স্মৃতিকথা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, “পার্থ, ভাই তুমি তোমার বইতে সেই যেসব সেক্স টেক্স নিয়ে লিখেছো, সে কি সব সত্যি?” সব সত্যি, বুদ্ধদা, আমি সদ্য-প্রয়াত জিনিয়াস চিত্রকরকে আশ্বাস দিয়েছিলাম।
“একটা কথাও বানিয়ে লিখিনি, বুদ্ধদা। ইন ফ্যাক্ট, আরো অনেক লিখতে পারতাম। লিখিনি।” লিখিনি, কারণ সাহিত্যের সীমা, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারিনি।
জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিটি গল্পই ঠিক তেমনই একশো ভাগ রগরগে সত্যি। লিখতে গিয়ে অনেক সময়েই বুকের ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু লিখি, ছাপাই। কারণ জানুক, সবাই জানুক। আমেরিকার জীবন আসলে যে ঠিক কেমন, বুঝুক সবাই। আমেরিকা মানে হলিউড নয় শুধু। মায়ামি বীচের লাস্যময়ী অর্ধনগ্ন যুবতীরা নয় শুধু। আমেরিকা মানে টাইমস স্কোয়্যার নয়, ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে নয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সাবার্বের সবুজ ঘাসের গালিচাঘেরা প্রাসাদোপম বাড়ি নয়। নোবেল প্রাইজ নয়, আইনস্টাইন নয়, বিল গেটস নয়, বিল ক্লিন্টন আর বারাক ওবামা নয়।
এসব হলো অর্ধসত্য। মিডিয়ার পালিশ। ভেঙে পড়া পুরোনো দেউলিয়া দোকানের সামনে চকচকে দরজা জানালা আর নিওন লাইটের ঝকমকে সাইনবোর্ড। আসল আমেরিকার গল্প আমি জানি। ভালোও জানি, আবার ভীষণ নোংরা, অন্ধকার, রক্তাক্ত আমেরিকাও জানি।
নিজের জীবন দিয়ে সবকিছুই দেখেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি। মাটি ছুঁয়ে দেখেছি। একশো ভাগ সত্যি গল্প বলে যাবো একটানা।
ভুল হয়ে গেল ভীষণ। তখনকার এ্যাপ্রেন্টিস দেশি ইংরিজিতে বলতাম হয়তো, “আই মেড এ মিস্টেক, স্যার।” এখনকার ইংরিজিতে বলবো, “শিট, আই স্ক্রুড আপ বিগ টাইম।” যে প্রফেসরের কাছে রিসার্চ করবো বলে শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছিলাম সেই আই এস ইউ’তে, সেই এ্যান্থনি লাইবারটা সেদিন রজার অ্যান্ডারসনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ইট’স এ বিগ মেস।” সেই ডঃ অ্যান্ডারসন, যাঁর ইকোলজি ক্লাসের কথা আগেই বলেছি।
অ্যান্ডারসন দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, “ইয়েস, ইট ইজ।”
প্রথম সপ্তাহেই ঘা খেলাম একটা। সবেমাত্র দেশ থেকে এসেছি। আমার কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। মানসিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক। আমাদের একদলকে নিয়ে একটা বড়ো ভ্যানে করে দুই প্রফেসর লাইবারটা এবং অ্যান্ডারসন নিয়ে গেলেন ইউনিভার্সিটির নিজস্ব একটা ফার্মে -- ক্যাম্পাস থেকে প্রায় একঘণ্টা দূরে। কৃষিজমি। সেখানে লিটল ব্লুস্টেম বলে একটা জংলি আগাছা লাগানো হয়েছে ইকোলোজির পরীক্ষামূলক প্রয়োজনে। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি।
 ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্রীনহাউস
ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্রীনহাউস
আমি সবে দেশ থেকে এসেছি, এমনিতেই আমার শরীর মন কিছুই ভালো নয়। আগের সপ্তাহে প্রথম ক্লাসে দুই প্রফেসর বলে দিয়েছেন, বর্ষাতি নিয়ে এসো সঙ্গে। আমার বর্ষাতি নেই। ছাতাও নেই। একহাতে ছাতা নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। দুটো হাত ফ্রী রাখতে হবে। আমার পরনে ক্যাম্পাসের একমাত্র স্টেশনারি দোকান থেকে কেনা কমলা রঙের একটা প্লাস্টিকের পঞ্চো -- যা কেনা আমার সাধ্যের মধ্যে, তাও আবার ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা ধার করে। পঞ্চোতে কোনো বোতাম নেই -- সারা গায়ের ওপর একটা তাঁবুর মতো। তার চারদিক থেকে জল ঢুকছে। জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। জুতো মোজা ভিজে যাচ্ছে খুব বেশি।
একটু রিওয়াইন্ড করি। ডিপার্টমেন্টে প্রথম মুখ দেখানোর পর গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার ডঃ ডেরেক ম্যাকক্র্যাকেন হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, “ওয়েলকাম। সো, হাউ ডু ইউ প্রোনাউন্স ইওর নেম?”
তখন আমি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কল্যাণে মার্কশীটে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনো ভাবিনি, এই অতি নিরীহ নিষ্পাপ নামটা নিয়েও এতো বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। একগাল হেসে বললাম, “পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার।”
ম্যাকক্র্যাকেন আরো বেশি হাসতে যাচ্ছিলেন আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন বলে। হাজার হোক, সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে আমি এসেছি আমেরিকায় পড়তে। কিন্তু আমার নাম শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দেখে ফেলেছি, সাহেবের দাঁতের রং নীল। নীল দাঁত এর আগে আমি কখনো দেখিনি। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। অচেনা পরিবেশ। ঝকঝকে বায়োলজি ডিপার্টমেন্ট। অফিস। কলকাতার ধূলিধূসর ফাইল নেই। টাইপরাইটার নেই। ঝুল নেই, চায়ের দাগ নেই, নোংরা কাপ নেই, গন্ধ নেই কোনো। একজন মার্কিন লেডি সেক্রেটারি এক কোণে বসে আছেন তাঁর কম্পিউটারের সামনে। উজ্জ্বল আলো। সবকিছুই কেমন যেন অচেনা, অদ্ভুত। বাংলা ভাষা নেই।
সেই কলকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে একদিন দেড়শো টাকা খরচ করে এই ডিপার্টমেন্টেই ফোন করেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার অ্যাডমিশন কি চূড়ান্ত? এখান থেকেই কে যেন একজন ফোন ধরেছিলেন। কলকাতা থেকে আন্তর্জাতিক ফোন। সেই প্রথম। কোনো কথাই বুঝতে পারিনি। দেড়শো টাকা জলে গেল। সেসব দিনের বর্ণনা ঘটিকাহিনিতে লিখেছি।
ডিপার্টমেন্টের হেডের নাম ডঃ জর্জ কিডার। ম্যাকক্র্যাকেন ক্যানাডিয়ান। পরে জানালাম, ম্যাক দিয়ে নাম শুরু হলেই আসলে সে আইরিশ। ম্যাকডুগাল, ম্যাকফার্সন, ইত্যাদি ইত্যাদি। জর্জ কিডার বোধহয় ব্রিটিশ আমেরিকান। একটু একটু ব্রিটিশ উচ্চারণ বোধহয় ছিল। হাসিমুখ। কিন্তু ছ’ফুট তিন দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ। এই ডিপার্টমেন্টে ব্রিটিশ বা আইরিশ লোকজন থাকার জন্যে কি আমার শিকেটা ছিঁড়েছিলো? কে জানে! এখন আর জানার কোনো উপায় নেই।
তারপর সবচেয়ে বড়ো কথা, ছিলেন আমাদের কেরালাতে জন্মানো ও বড়ো হওয়া ডঃ ম্যাথু নাদাকাভুকারেন। এঁর কথা পরে আরো একটু বলতেই হবে। আমার চার বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা এঁদের খুব কাজে লেগেছিলো বলেই আমার মনে হয়। একজন একটু এক্সপেরিয়েন্সড টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এই ডিপার্টমেন্টে দরকার ছিল খুব। শিকেটা ছেঁড়ার এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কারণ।
লাইবারটা ইটালিয়ান আমেরিকান। দেশে থাকতে পিটারসন্স গাইড দেখে দেখে যখন এ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছিলাম, তখন ভেবেছিলাম, লিবারটা। আমরা ঐরকমই উচ্চারণ করি। যেমন, এখন সবাই প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে দেশে বলে বিডেন। খবরের কাগজেও এরকম অজস্র ভুল উচ্চারণ লেখা হয়। শুধরে দেবার কেউ নেই। ওরা নিজেরা ঠিকমতো জানার চেষ্টাও করে না। সবজান্তা মিডিয়া কিনা। ওদের আবার কোনো ভুল হতে পারে?
তা, সে যাই হোক।
ম্যাকক্র্যাকেনের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমাকে বললেন, “ও গশ, আই অলওয়েজ থট ইট ওয়াজ পার্থা ব্যানডিওপাডিয়াইই।” ওই যে, নামের শেষে ওয়াই এ ওয়াই জুড়ে দিয়েছে পর্ষদ। পিতৃদেব জিতেন্দ্রনাথ শুনলে মূর্ছা যেতেন। সেই কাশীর গণেশ মহল্লার বিশাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। ব্যানডিওপাডিয়াইই আর পার্থা – হুগলির দশঘরা গ্রামের বনেদি বংশের ছেলে কালাপানি পার হয়ে জাত তো খুইয়েছেই। এখন বংশের নামটাও খোয়ালো।
প্রপিতামহ রামদাস, পিতামহ কেদারনাথ, এই অধমকে ক্ষমা করুন।
সদাশয় প্রফেসর বললেন, “ইউ নীড সাম অ্যাডভান্স ফ্রম ইওর স্টাইপেন্ড?” আমি তো অবাক! পকেটে আছে শুধু দেশ থেকে আনা একশো ডলার। বোধহয় আরো কম।
তুমুল বৃষ্টিতে সারাদিন ভিজতে ভিজতে নির্দেশাবলী ভুল করে লিটল ব্লু স্টেমের শিকড়শুদ্ধু তুলে না এনে কর্দমাক্ত মাটি থেকে গাছের উপরের অংশটা কাঁচি দিয়ে কেটে এনে জমা করেছিলাম ভ্যানে। বিশাল ভুল। ওঁদের আমেরিকান ইংরিজি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আমিই একমাত্র অ-মার্কিন ছাত্র। লাইবারটার ল্যাবের অন্য ছাত্র বিল, আর অ্যান্ডারসনের কাছে দু’বছর আগে আসা মালয়েশিয়ার সম্পূর্ণ আমেরিকানাইজড ছাত্র শিবচরণ সিং ধীলন কোনো ভুল করেনি। শিবচরণ তার নাম লেখে শিবচর্ন ডিলিওন।
 লিটল ব্লুস্টেম – যা নিয়ে এতো কাণ্ড!
লিটল ব্লুস্টেম – যা নিয়ে এতো কাণ্ড!
আমার ভুলের মাশুল তারপর অনেকদিন ধরেই আমাকে দিতে হয়েছিল। লাইবারটার গুড বুকে আসার জন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমাকে।
এ্যান্থনি লাইবারটা রজার অ্যান্ডারসনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ইট’স এ বিগ মেস।”
অ্যান্ডারসন দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, “ইয়েস, ইট ইজ।” তারপর একটু ভেবে বলেছিলেন, “বাট, হাউ ডু উই ফিক্স ইট?”
(চলবে)
*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে চলছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।
ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।
‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।