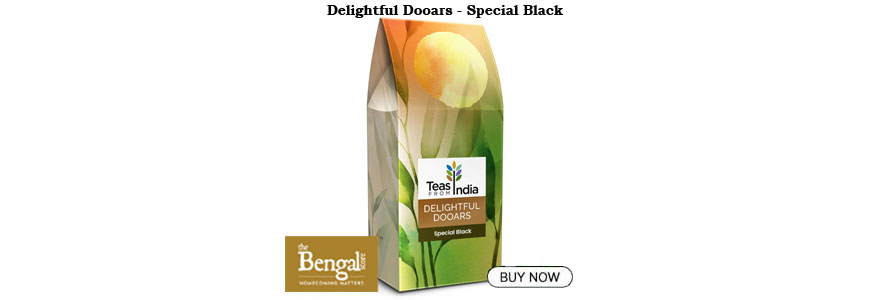মেরিকামায়া সাতকাহন : ১৯৮৫ সাল, জীবনে সেই প্রথমবার ভারতকে বিদায় জানালাম

ঊনিশশো পঁচাশি সাল। চোদ্দই অগাস্ট কলকাতা থেকে প্লেন ছাড়লো বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। দিল্লি বিমানবন্দর – রাত আটটা। ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই প্রথমবারের মতো। এয়ার ইন্ডিয়াতে দিল্লি। দিল্লি থেকে গভীর রাতে থাই এয়ারওয়েজ আমাকে পৌঁছে দেবে লণ্ডন। তারপর হীথরো এয়ারপোর্টে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ‘টি ডব্লিউ এ’ নামক এয়ারলাইন আমাকে নিয়ে যাবে সেই সুদূর শিকাগো।
দমদম বিমানবন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এতো বিরাট সংখ্যক আত্মীয় ও বন্ধু এসেছিলো যে নিজেকে মনে হচ্ছিলো যেন ভি আই পি। এক বন্ধু গুণে দেখেছিলো – সত্তর জন নাকি এসেছিলো আমাকে ‘সী-অফ’ করতে। তার মধ্যে আমার শ্বাশুড়ি ঠাকরুণের চোখে জল। বউয়ের চোখে জল। আমার মাসির চোখে জল। ট্যাক্সিতে আসবার সময়ে মাসি বলছিলো, “বুদ্ধদেব থাকলে আজকে কত খুশি হতো।” বুদ্ধদেব মানে আমার ছোটমামা বুদ্ধ, দু’বছর আগেই যে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়েসে মারা গেছে। কংগ্রেসের ভেতরকার পলিটিক্সের শিকার হয়েছিল ভীষণ উজ্জ্বল সেই ছ’ফুট লম্বা ছেলেটা। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিসে ওর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো রাত এগারোটার সময়ে।
আমার বাবার চোখে জল কেউ কখনো দেখেনি, সুতরাং সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমাদের দেশে মেয়েদের যেমন শেখানো হয়েছে সবসময়ে চোখের জল ফেলবে, ছেলেদের ঠিক তেমনই সমাজ শিখিয়েছে, কখনো চোখের জল ফেলবে না, কারণ তুমি পুরুষ, চোখের জল ফেলা বা দুঃখ প্রকাশ করাটা দুর্বলতার লক্ষণ।
সুতরাং আমার বাবাও আমাকে শৈশব থেকে শুধু কাঠিন্য প্রকাশ করতেই শিখিয়েছেন। আর আমিও ভান করতে শিখেছি যে আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক পুরুষ। আমি আবার চোখের জল ফেলবো কী? আমার মায়ের মৃত্যুর পর যখন আবার সেই বিরাট সংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয় শ্মশানযাত্রী হয়েছে, তখন মায়ের নিঃসাড় নিঃশব্দ দেহ কাঁধে করে হেঁটে হেঁটে নিমতলা শ্মশানের দিকে নিয়ে যাবার সময়ে সেকালের এক বন্ধু আমাকে বলেছিলো, “পার্থ, তোকে দেখে আশ্চর্য লাগে। তোর কী মনের জোর!” এখনো মনে আছে। প্রতাপের পাড়ার ছেলে ভোঁদা – ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বিকাশ।
মনের জোর না থাকলে শেষ হয়ে যেতাম। যেমন আমার পাঁচ বছর বয়েস থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠা বন্ধু সুব্রত শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুব্রত আমার মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও আসেনি। আমার মায়ের মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহস ওর ছিলো না।
আমার মনের জোর ছিল। দুঃসাহস ছিল। অচেনাকে চেনার, জয় করবার শক্তি আমার ছিল। চরম দুঃখ দারিদ্র্য হতাশা ব্যর্থতার মধ্যে থেকে উঠে এলেই হয়তো অনেকের মধ্যে সেই শক্তি ঈশ্বর জাগ্রত করেন। তার ওপরে, আমার সঙ্গে আজন্ম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন,
“অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টানবে অচিন-ডোরে।”
নয়াদিল্লি এয়ারপোর্টে থাই এয়ারওয়েজের প্লেনের জন্যে যখন অপেক্ষা করছি সুনীতা বোস আর আমি, তখন বিমানবন্দর শুনশান। দেখা হয়ে গেলো অনেকটা আচম্বিতেই বিখ্যাত অভিনেত্রী রোহিণী হাত্তাঙ্গাড়ির সঙ্গে। রোহিণী তখন অফ-বীট হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করে জনপ্রিয়। সারাংশ নামের ফিল্মে তাঁর অভিনয় দেখে অবাক হয়েছিলাম। তারপর তিনি গান্ধি, আরো অনেক ছবি করেছেন। কিন্তু তখন আমি দেশ থেকে অনেক দূরে।
 থাই এয়ারওয়েজ প্লেনেই জীবনে প্রথম আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা
থাই এয়ারওয়েজ প্লেনেই জীবনে প্রথম আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা
কীভাবে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো দিল্লি এয়ারপোর্টে, তা আর মনে নেই। আমিই বোধহয় যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম, এবং দেশ ছেড়ে পড়াশোনা করার জন্যে আমেরিকায় চলে যাচ্ছি আজ রাতেই, সে কথা তাঁকে বলেছিলাম। রোহিণী বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে গল্প করেছিলেন। উষ্ণ, আন্তরিক। বিখ্যাত অভিনেত্রী বলে কোনো অহঙ্কার নেই। ইগো নেই। অবশ্য, গল্প মানে আমার তখনকার অতি বাজে ইংরিজি আর ভাঙা ভাঙা হিন্দি মেশানো আর হাসি দিয়ে বাকিটা মেকাপ করে দেওয়া গল্প। আমি একাই ছিলাম সে গল্পে। সুনীতা তখন যথারীতি কোথায় যেন চলে গেছে চটি ফ্যাটফ্যাট করে। হ্যাঁ, এয়ারপোর্টেও চটি।
 রোহিণী হাত্তানগাদীর
রোহিণী হাত্তানগাদীর
রাত দেড়টায় প্লেন ছাড়লো দিল্লি থেকে। বিদায়, ভারতবর্ষ। না, চোখের জল ফেলার কোনো প্রশ্নই নেই আমার।
লণ্ডনের অতি বিশাল এয়ারপোর্টে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার অবস্থা। রাণী এলিজাবেথ তখনও রমরম করে রাজত্ব করে যাচ্ছেন, এবং আমাদের মতো কালো চামড়ার মানুষদের অমানুষ অথবা মনুষ্যেতর প্রজা বলে ভেবে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের মানুষ জানেই না, ব্রিটিশ শাসকদের জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ এবং বর্ণবিদ্বেষ কী মারাত্মক। আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের গল্প অনেকেই শুনেছে – মিডিয়ার কল্যাণে, এবং আজকের নতুন প্রজন্মের জনজোয়ারের কল্যাণে। যদিও অনেকেই বিশ্বাস করে না সেসব কথা। কিন্তু ওই দু’একটা নাম – এব্রাহাম লিঙ্কন, জন কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং – হলিউড আর এমটিভির মগজধোলাইয়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে অন্ধকার গরাদের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর মতো ছিটকে ছিটকে এসেছে।
কিন্তু ব্রিটিশদের কালো চামড়ার প্রতি ঘৃণা, এবং বিশ্বব্যাপী ত্রাসের কথা মানুষ ভুলে গেছে, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা দেখেছি। জীবনের এই অদ্ভুত, আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য যাত্রাপথে কতবার যে ইঙ্গ-মার্কিন বিদ্বেষ, বঞ্চনা, অবহেলা ও অবিচারের শিকার হয়েছি, তার হিসেব দিতে গেলে একটা আস্ত উপন্যাস লিখে ফেলতে হবে।
যাক, প্রবন্ধ লিখবো না এই সাতকাহনে। সত্যি কথা সহজ সরল ভাষায় লিখি। কবির কথাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে লিখি, “যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।”
 লণ্ডনের হীথরো বিমানবন্দর
লণ্ডনের হীথরো বিমানবন্দর
লণ্ডনের হীথরো বিমানবন্দরের অতি উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে, হাজার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের নাম পড়ে, হাজার নতুন নতুন ভাষার ও পোশাকের মানুষকে দেখে যখন প্রায় হারিয়ে যাচ্ছি, তখন ত্রাতা হাজির হলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কলকাতার সায়েন্স কলেজের আড্ডার বন্ধু মলয় ভট্টাচার্য্য। ছ’ঘণ্টার সাময়িক বিরতি – শিকাগোর প্লেন ধরবার আগে। পারের কড়ি যে কয়েকটা ডলার সঙ্গে এনেছিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তার মধুসূদন অফিসার মুক্তির মামাতো দাদা বাবুদার সাহায্যে, তার থেকে পাঁচটা ডলার ভাঙিয়ে হীথরো থেকে মলয়কে ফোন, এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের ছাত্র মলয়ের হাস্যমুখে আবির্ভাব। এবং তিরস্কার, কেন আমি দু’চার দিন লণ্ডনে ওদের কাছে থেকে গেলাম না। ওদের মানে ও এবং ওর সায়েন্স কলেজের বান্ধবী এবং এখন স্ত্রী শ্রীজা। তিরস্কারের জবাব দেওয়ার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ ওই যে আগেই বলেছিলাম, সম্পূর্ণ নাইভ – বাংলায় যাকে বলে গাড়োল – ছিলাম এসব ব্যাপারে। খুব সহজেই ওদের বাড়ি লণ্ডনে কয়েকদিন থেকে তারপর শিকাগো যাত্রা করতে পারতাম। কিন্তু সেসব পরামর্শ আমাকে কে দেবে? তাই, প্লেনের জানালা থেকে লণ্ডনের বিশাল এক পোস্টকার্ডের মতো ছবি দেখে, আর এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতায় আর একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিয়েই সেযাত্রা খুশি থাকতে হলো। আসল লণ্ডনকে, রাণির শহরকে আর সারা পৃথিবীর রক্ত চুষে তৈরি করা বাকিংহাম প্রাসাদ আর কোহিনুর চুরি করে আনা ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখার জন্যে আরো অনেক, অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।
মলয়কে বিদায় জানিয়ে উঠে বসলাম মার্কিন যাত্রীবাহী টি ডব্লিউ এ’র সাত-তিন-সাত বোয়িং বিমানে। মলয়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি।
ঊনিশশো পঁচাশি সাল। আগস্টের মাঝামাঝি। কালকেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হবে ভারতে। আমি কাটিয়েছি এক পরাধীন জীবন। গারদের আসামীর মতোই। বা বলা যায়, খাঁচার পাখির মতোই। অনেক চেষ্টায়, অনেক মনের জোরে, অনেক পরিশ্রমে কেবলমাত্র আমাদের দুজনের জেদে খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছি মুক্ত আকাশের নীলের স্বাদ পাওয়ার জন্যে। যে পাখি উড়তে শেখেনি, সে দুঃসাহস দেখিয়েছে অনেক উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়ার। মাঝপথেই উড়তে শিখে নিতে হবে। শিখতেই হবে, নাহলে নিশ্চিত মৃত্যু।
পিছনে ফেলে এসেছি প্রায় তিন দশকের আজন্ম পরিচিত ভালোবাসার দেশ, জাতি, ভাষা, সমাজ, দুঃখসুখ। ফেলে এসেছি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ, শরতের আলো – আমার রাত পোহালো, কাশফুল, চড়ুই পাখি, মহিষাসুরমর্দিনী, ঢাক, ঘন্টা, শাঁখের ধ্বনি। ফেলে এসেছি রকের আড্ডা, মিনার বিজলী ছবিঘর। ফেলে এসেছি রাজলক্ষ্মী হোটেলের ভাত আর মাছ, হর্তুকি বাগানের সেই আধো অন্ধকার ঘরটা, যেখানে গরিব মামার বাড়ির ওরা সবাই রোজ আমাকে একবার দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। আর ফেলে এসেছি সেই তিনের আটের মেজেনাইন ফ্লোরের আড়াইখানা ঘর, যেখানে আমার মা বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে ক্যানসারে শেষ হয়ে গিয়েছিলো।
যাক, আমাদের দেশের ছেলেরা চোখের জল ফেলে না। ফেলা বারণ।
“এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো না গো আর।”
টি ডব্লিউ এ নামক সুবিশাল বাজপাখি মাথা উঁচু করে উড়ে গেলো আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবে বলে।
(চলবে)
*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে চলছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।
ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।
‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।