ভারতীয় হিসেবে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করেন এই বাঙালি
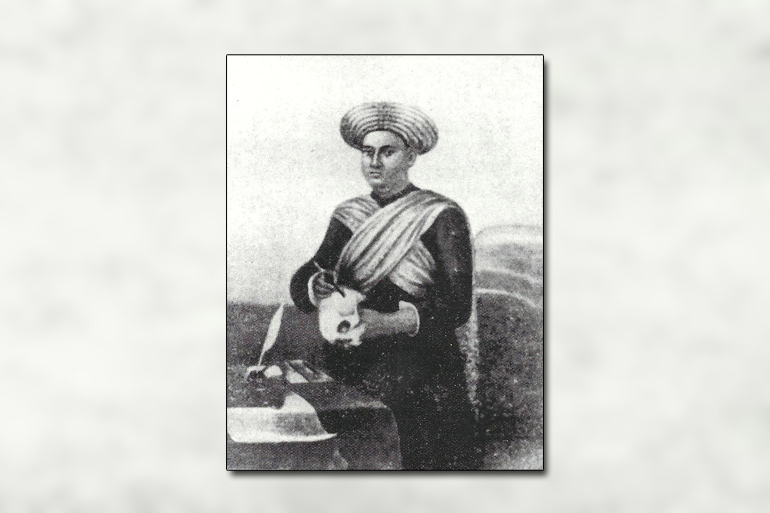
তখন সবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের ‘বৈদ্যক’ বা আয়ুর্বেদ বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হল। ওই বিভাগের ছাত্রেরা ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। তাঁদেরই এক সহপাঠী মধুসূদন গুপ্ত ডেমনস্ট্রেটরের পদে নিযুক্ত হন এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। এদিকে ডাক্তারি পাশ না করা সহপাঠীর ক্লাস করতে পড়ুয়ারা নারাজ। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানে, মধুসূদন ডাক্তারির বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ। তবুও ছাত্রদের অসন্তোষ কমানো দরকার। মধুসূদনকে কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল, তিনি যেন ডাক্তারি পরীক্ষায় বসেন। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন তিনি।
যেই বছর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়, সেই ১৮০০ সালে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি গ্রামের এক বৈদ্য পরিবারে জন্মেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। তাঁদের পরিবার নাম করেছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য। মধুসূদনের প্রপিতামহ ‘বক্সী’ উপাধি পেয়েছিলেন। পিতামহ ছিলেন হুগলির নবাব পরিবারের গৃহচিকিৎসক। ছোটোবেলায় মধুসূদন খুব দুরন্ত ছিলেন। পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। যে কারণে বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। যদিও পরে তিনি মন দিয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক বিভাগে ভর্তি হন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার – ইত্যাদিতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন। কাঠ ও মোমের তৈরি মানুষের হাড়গোড়ের মডেল খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। ছোটোখাটো জীবজন্তুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে কেবলরাম কবিরাজ নামের এক আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সঙ্গে রোগী দেখতে যেতেন গ্রামে গ্রামে। এভাবে হাতেকলমে দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।
সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগের অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ অবসর নেন ১৮৩০ সালে। প্রিয় ছাত্র মধুসূদনকে নিজের পদে নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। সহপাঠী মধুসূদন অধ্যাপকের পদ লাভ করলে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। যদিও মধুসূদনের পড়ানোর গুণে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তায় সেই বিক্ষোভ থেমে গিয়েছিল। ১৮৩২ সালে স্থানীয়দের চিকিৎসার জন্য কলেজের লাগোয়া এক বাড়িতে হাসপাতাল তৈরি হয়। সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার জ়ে গ্রান্ট এবং ডাঃ টাইটলার সেখানে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস নিতেন। তাঁদের বক্তৃতা নিয়মিত শুনতে যেতেন মধুসূদন। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে শারীরবিদ্যা ও শল্যবিদ্যা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে তিনি সেখানে যোগ দেন। ১৮৪০ সালে পরীক্ষা দিয়ে লাভ করেন ডাক্তারি ডিগ্রি।
তখন ভারতীয় ছাত্ররা কুসংস্কার ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতে চাইতেন না। অথচ ডাক্তারি শেখার জন্য মানুষের দেহের অভ্যন্তর ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। একদিন ডাঃ গুডিভ এক শবদেহ নিয়ে পড়ুয়াদের বোঝালেন ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ছাত্রদের মনে দারুণ ভয়। কিন্তু মধুসূদন চিরকালই ব্যতিক্রমী। ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি আধুনিক যুগের প্রথম ভারতীয় হিসেবে মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করলেন। ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন চিকিৎসক সুশ্রুতের পর মৃত নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হল এই প্রথম। হিন্দু সমাজে শুরু হয়ে গেল প্রবল তোলপাড়। উচ্চবর্ণের মাতব্বরা খেপে উঠেছিলেন। মধুসূদনকে জাতিচ্যূত করা হল। তাতে অবশ্য মধুসূদন থেমে যাননি। ইয়ং বেঙ্গলের নেতারা সমর্থন করলেন তাঁকে। তাঁর উৎসাহ এবং প্রেরণায় সেবছরের ২৮ অক্টোবর মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করলেন আরও চারজন – রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, উমাচরণ শেঠ এবং নবীনচন্দ্র মিত্র।
মেডিকেল কলেজের হিন্দুস্তানি বিভাগকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হলে তার সুপারিনটেনডেন্ট পদের দায়িত্ব পান মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৫২ সালে বাংলা বিভাগ খোলা হলে তারও সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োজিত হন। আমৃত্যু সেই পদে ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই বাংল্য অনুবাদ করেন তিনি। সংস্কৃত কলেজে পাঠরত অবস্থায় হুপারের লেখা ‘Anatomist’s Vade Mecum’ বইটির সংস্কৃত অনুবাদ করে ১০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।
তাঁর শরীরে ডায়বেটিস ধরা পড়লে চিকিৎসকরা শব ব্যবচ্ছেদে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু বারণ শুনতেন না। অন্যদের সাহস জোগাতে এই কাজ তিনি থামাননি। জীবাণুর সংক্রমণে ডায়বেটিক সেপ্টিসিমিয়ায় আক্রান্ত হলেন। যার ফলে ১৮৫৬ সালের ১৫ নভেম্বর প্রয়াত হন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে নতুন যুগের দিশারী মধুসূদন গুপ্ত।
তথ্যঋণ - উমা ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, অতনু চক্রবর্তী।































