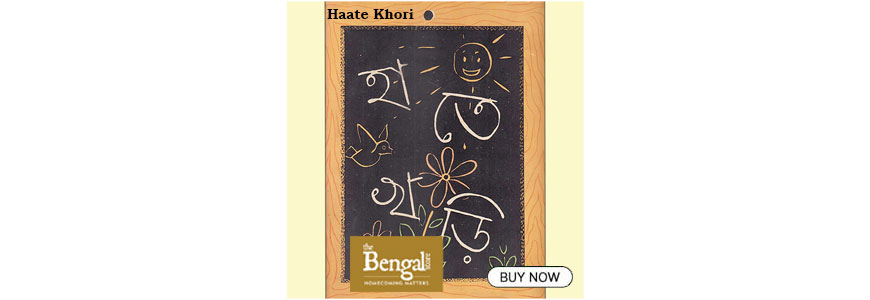‘মন’ নিয়ে আরও কথা হোক, তবেই দূর হবে ‘সামাজিক কলঙ্ক’
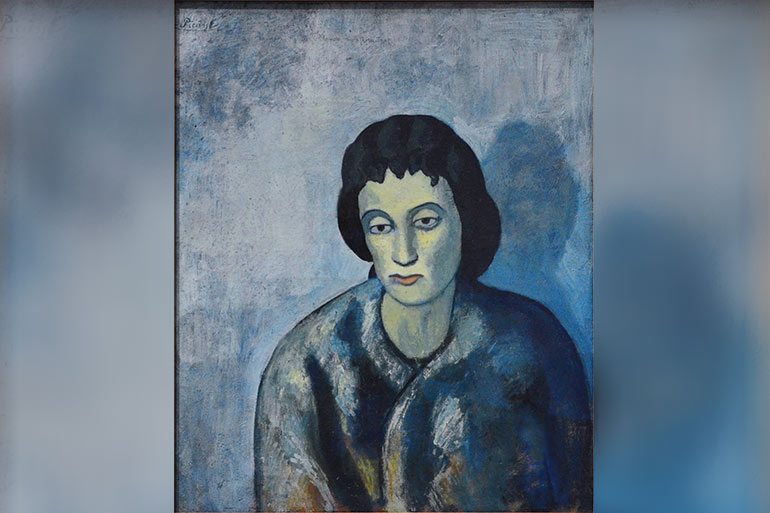
Image: Pablo Picasso, 1902, Woman with Bangs
“মৃত আত্মা বা শয়তান মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে নাকি মানসিক রোগ হয়” – খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। তখনও সমাজ কুসংস্কার আর অশিক্ষায় নিমজ্জিত। তখনও মানসিক রোগ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা সমাজকে আঁকড়ে ছিল। এখন যে এই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে, এ কথা কি জোর গলায় বলা যায়? কিছুদিন আগেও এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পরিবর্তে ওঝা, কবিরাজের কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র, তাবিজ ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন। এখনও মানসিক রোগ নিয়ে নানা ‘সামাজিক স্টিগমা’ রয়েছে, পরিণাম ভয়ংকর। তাহলে কি সমাজিক বোধের মাথায় গজাল মেরে বোঝানোর সময় এসেছে?
মানসিক রোগ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসাব্যবস্থাও আছে (যেমন ওষুধ, সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে)। সুতরাং মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর দ্রুত এর সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মানসিক রোগ অন্যান্য শারীরিক রোগের মতোই বাস্তবিক। এর প্রভাব শারীরিকভাবেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক উপাদানের অসামঞ্জস্যের কারণে ডিপ্রেশন হয়, যার ফলে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন ক্লান্তি বা মুডের পরিবর্তন, আত্মহত্যার প্রবণতা, উদ্যোগের অভাব, কাজে অনাগ্রহ প্রভৃতি, যা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটায়।
নিজেদের মানসিক অসুখ হলে? আমরা অস্বীকার করি, আমরা লুকিয়ে রাখি, আমরা চিকিৎসা নিতে চাই না, আমরা ভয় পাই, “লোকে কী ভাববে!” কারণ টিভিতে, সিনেমায়, সিরিজে মানসিক রোগীদের শুধুই থ্রিলার সিনেমার ‘সাইকোপ্যাথ’ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু মানসিক সমস্যা যে আর পাঁচটা অসুখের মতোই!
নিজেদের মানসিক অসুখ হলে? আমরা অস্বীকার করি, আমরা লুকিয়ে রাখি, আমরা চিকিৎসা নিতে চাই না, আমরা ভয় পাই, “লোকে কী ভাববে!” কারণ টিভিতে, সিনেমায়, সিরিজে মানসিক রোগীদের শুধুই থ্রিলার সিনেমার ‘সাইকোপ্যাথ’ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু মানসিক সমস্যা যে আর পাঁচটা অসুখের মতোই! যেখানে কিছু মানুষের অবসাদ হয়, কিছু মানুষের অতিরিক্ত উদ্বেগ, কারোর অবসেশন। আমাদের সমাজে এখনও মনে করা হয় মানসিক রোগী মানেই ভারসাম্যহীন, হিংস্র, হোমিসাইডাল। অথচ পরিসংখ্যান বলছে এমনকি সিজোফ্রেনিয়া রোগীরাও যত না বেশি হোমিসাইডাল, তার চেয়ে অনেক বেশি সুইসাইডাল।
সেভাবে দেখতে গেলে কিন্তু ডায়াবেটিস আর ডিপ্রেশনের কোনো ফারাক নেই, অথচ আমরা ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছি যত সহজে বলতে পারি, ডিপ্রেশনের ওষুধ খাচ্ছি বলতে আমরা সংকোচ করি! কারণ লোকে তো জানেই “ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস”, কিন্তু কেউ বলছে না, “ঘরে ঘরে ডিপ্রেশনও!” অথচ এটা এখন বাস্তব।
ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, ২০২০ থেকে ২০২১ সালে আত্মহত্যা বেড়েছে ৭.২ শতাংশ, ১.৬৪ লক্ষ মানুষ ২০২১ সালে আত্মহত্যা করেছেন। আর এই আত্মহত্যার পিছনে ৯০-৯৫% ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো মানসিক অসুখ রয়েছে, যে মানসিক অসুখের চিকিৎসা সম্ভব। মানসিক অসুখ নিয়ে আমাদের সমাজের এই স্টিগমা চিকিৎসার পথে অন্যতম অন্তরায়। এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অরুণিমা ঘোষ।
তিনি বলেন, “সামাজিক স্টিগমা এই রোগের চিকিৎসার পথে বড়ো বাধা। লোকের যখন মানসিক রোগ হয় অর্থাৎ সাইকোসিস বা ডিপ্রেশন প্রথম অবস্থায় আনট্রিডেড থাকলে, পরে চিকিৎসা করাতে এলে অসুবিধা হয়। যত তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্টের আওতায় আসবে, তত তাড়াতাড়ি ভালো রেজাল্ট হবে।”
মানসিক রোগ ব্রেনের কিছু নিউরো কেমিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেসের জন্য হয়। এটা অনেকেই আমরা জানি না। আমরা ভাবি মনের অসুখ। মন কথাটা ভেগ। মন বলে তো কোনও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই। মানসিক অসুখ ও শারীরিক অসুখকে আলাদা করে দেখার নয়। অন্য রোগ যেমন শরীরের অসুখ, তেমনি মানসিক রোগ বা ডিপ্রেশনও তো ব্রেনের অসুখ।
প্রাচীন সভ্যতায় মানসিক রোগের উল্লেখ ও চিকিৎসার বর্ণনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে অর্থাৎ প্রাক্ আধুনিক যুগে, মানসিক রোগকে জাদুকরদের শিকার মনে করা হত। ওই ধরনের মানসিক রোগীদের কারাগারে অথবা কিছুদিনের জন্য বেসরকারি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (তখন ‘পাগলাগারদ’) রাখা হত। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বন্য পশুর মতো মানুষকে চিকিৎসা করা হত কোথাও কোথাও। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নৈতিক চিকিৎসা আন্দোলন ধীরে ধীরে উন্নত হয়। শিল্প ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উনিশ শতকের প্রতিটি পশ্চিমা দেশে মানসিক রোগীর আশ্রয়ের সংখ্যা এবং আকারের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল এবং ‘মনোবিজ্ঞান’ শব্দটির (১৮০৮) প্রচলন হয়েছিল।
মানসিক রোগ ব্রেনের কিছু নিউরো কেমিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেসের জন্য হয়। এটা অনেকেই আমরা জানি না। আমরা ভাবি মনের অসুখ। মন কথাটা ভেগ। মন বলে তো কোনও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই। মানসিক অসুখ ও শারীরিক অসুখকে আলাদা করে দেখার নয়।
বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মনোবিশ্লেষণের বিকাশ ঘটেছিল, যা পরবর্তীকালে কেরেপেলিনের শ্রেণিবদ্ধকরণ স্কিমের সাহায্যে অগ্রগতি হয়। কয়েদি থেকে রোগী হিসেবে মনোরোগীদের দেখা হতে লাগল। মানসিক রোগীদের আশ্রয়স্থলগুলোকে পরবর্তীকালে হাসপাতাল হিসাবে নামকরণ করা হল। সময় যত অগ্রবর্তী হয়েছে, সমাজ যত আধুনিক হয়েছে, ততই মনোরোগ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক হয়েছে। ২০১১ সালে ইউরোপীয় সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (ইপিএ) মানসিক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকায় বলেছে যে, চিকিৎসার মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক অবস্থা প্রতিরোধ করা যেতে পারে এমন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।
২০১৬ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ মানসিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গবেষণা ক্ষেত্রে পুনরায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মানসিক রোগের জন্য একটি প্রধান চিকিৎসা হল সাইকোথেরাপি। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়। জ্ঞানীয় আচরণগত থেরাপি (CBT) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যা একটি নির্দিষ্ট ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত ধারণা এবং আচরণের নিদর্শন পরিবর্তন করার উপর ভিত্তি করে এই থেরাপি দেওয়া হয়। মানসিক দ্বন্দ্ব এবং প্রতিরক্ষার অন্তর্নিহিত মনোবিশ্লেষণ করে যে থেরাপি দেওয়া হয় তাকে বলে ডমিন্যান্ট স্কুল অফ সাইকোথেরাপি, যা এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। পদ্ধতিগত থেরাপি বা পারিবারিক থেরাপি কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়, যেখানে অন্যদের একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে থেরাপি দেওয়া হয়।
আজকের দিনে মানসিক অসুখের আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে। অথচ সিনেমা, সাহিত্য যে ছবিটা গড়ে তুলেছে, তা হল অস্বাস্থ্যকর, মানসিক অ্যাসাইলাম, যেখানে রোগীকে বেঁধে রেখে, মাথায় “শক” দেওয়া হচ্ছে, এই দৃশ্যের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। এ দৃশ্য শুধুই ভীতি প্রদর্শন করে, মানসিক রোগের চিকিৎসা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা দেয়। আজকের দিনে মানসিক অসুখের জন্য আছে অনেক ওষুধ, যেগুলো কিন্তু মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য নয়, মানসিক চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষকে একটা ‘প্রোডাকটিভ’ জীবনে ফিরিয়ে আনা। ওষুধের সঙ্গে রয়েছে সাইকোথেরাপি, রয়েছে নিউরোমডিউলেশন পদ্ধতি যেগুলোর একটা ইসিটি বা যেটাকে আমরা ওই “শক দেওয়া” বলে জানি। কিন্তু সেটাও আজকের দিনে অনেক উন্নত, আধুনিক ও মানবিকভাবেই প্রয়োগ করা হয়, টিভিতে দেখানো দৃশ্যের মতো হাত-পা-মুখ বেঁধে কোথাও মানুষের মাথায় শক দেওয়া হয় না। এমনটাই জানালেন সাইক্রিয়াটিস্ট অরুণিমা ঘোষ। তাঁর কথায়, “মিসলিডিং কিছু দেখানো হয়। চিকিৎসার যে অমানবিক দৃশ্য টিভি, সিনেমায় দেখানো হয়, সেটা ঠিক নয়। আজকের দিনে উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে কমিউনিটিতে রিহেবিলিটেট করা। এখন সাধারণ হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসা হচ্ছে। রোগী পাঁচ সাতদিন হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। মানসিক রোগের চিকিৎসা এখন অনেক বেশি মানববিক।”
ওঝা বা তুকতাক যেমন অপরাধ, তেমনি মানসিক রোগীকে সমাজের স্টিগমার আড়ালে লুকিয়ে রাখাও অপরাধ। তাই যে সমাজ মুখ তুলে আধুনিকতার গর্ব করে, তারা আজ মন নিয়ে কথা বলুক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আবর্তে।