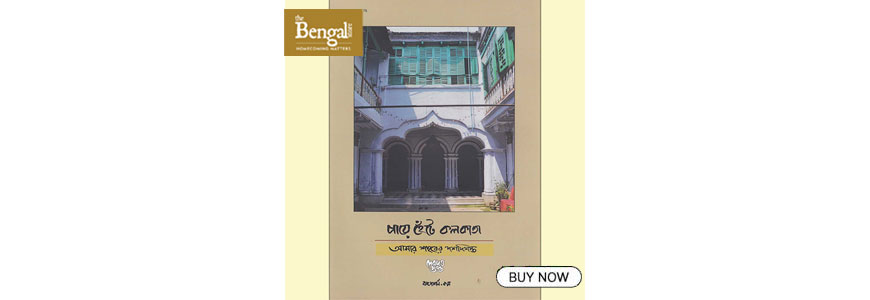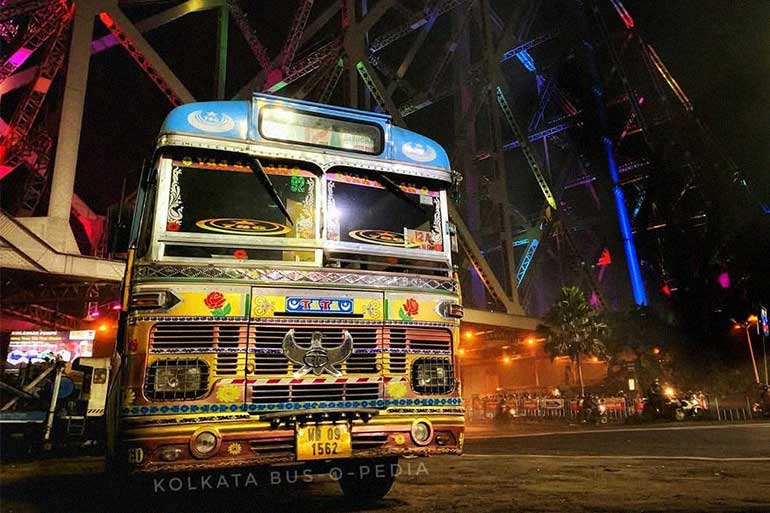দেশভাগের ৭৫ বছর পার, কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনি আজও মনে করায় যন্ত্রণার ইতিহাস

কলকাতার বহু কলোনি (Colony of Kolkata) আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। দেশভাগের (Partition) নির্মম যন্ত্রণা প্রভাবিত করেছিল কলকাতা শহরকে। ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছিল বৈকি! যার প্রমাণ মেলে আজও। দেশভাগের মর্মন্তুদ ছবি ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটক ‘সুবর্ণরেখা’ (Subarnarekha) ছবিতে। ওপার বাংলা থেকে চলে আসা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছিলেন বাগদি বউ ও তাঁর একমাত্র ছেলে অভিরাম। তারপর একসময় দুজন দুজনকে হারিয়ে ফেলেন। বিচ্ছেদ হয় মা-সন্তানের। বহু বছর পর মায়ের দেখা পান অভিরাম। ততক্ষণে মা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন এবং মারা যাচ্ছেন। দেশভাগের পোড়া দাগের এই ক্ষত আজও কেউ মেলাতে পারেনি।
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের আগমনে কলকাতা (Kolkata) ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৪৭-এর পর থেকে প্রায় কয়েক দশক ধরে অব্যাহত ছিল উদ্বাস্তুদের যাতায়াত। ১৯৫১ সালে আদমশুমারির সমীক্ষা অনুযায়ী, কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় ৪,৩৩,০০০ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু (Hindu Refugee) এসেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে বাড়তে থাকে এই সংখ্যা। উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কোনোরকমে ক্যাম্প বা বস্তি বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথা গোঁজার জন্য। কিন্তু এইভাবে কদ্দিন! বিনা পয়সায় কেউ থাকতে পারবে না। যতদিন না নিজেদের থাকার মতো একটা বাড়ি বানাতে পারবেন, ততদিন কলোনিতে থাকতে পারেন উদ্বাস্তুরা। কিন্তু বিনিময়ে দিতে হবে নামমাত্র অর্থ। জমি দখলের কোনো আইনি অবস্থান ছিল না। সরকারের সঙ্গে ক্রমশ সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে। কলোনিগুলো (Refugee Colony) হয়ে ওঠে ‘জবরদখল কলোনি’। এইরকম জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে মূলত দক্ষিণ কলকাতায়। শোনা যায়, যাদবপুর লাগোয়া বিজয়গড় ছিল প্রথম উদ্বাস্তু কলোনি। দেশভাগের ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠে বিজয়গড় কলোনি। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশে কলোনির সংখ্যা ছিল ১৪৯। পরবর্তী কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে আরও ১৭৫টি কলোনি তৈরি হয়।
.jpg)
আজকের কলকাতা শহর ধারণ করে আছে দেশভাগ ও কলোনির ইতিহাস (Partition and History of Colony)। যে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির নামকরণ হয়েছিল মূলত মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের নামে। বিজয়গড় কলোনি-লাগোয়া আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কলোনি দেখা যাবে আজও। বাঘাযতীন কলোনি (বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে), বাপুজি নগর (মহাত্মা গান্ধির নামানুসারে), নেতাজি নগর (সুভাষচন্দ্র বসুর নামানুসারে), আশুতোষ কলোনি (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে), সুচেতা কলোনি (সুচেতা কৃপালিনীর নামানুসারে), সূর্য নগর (মাস্টারদা সূর্য সেনের নামানুসারে), কাটজু নগর (কৈলাশ নাথ কাটজুর নামানুসারে) ইত্যাদি। এর পাশাপাশি নেতাদের নামে না রাখা কলোনিগুলো ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছে আজাদগড়, রামগড় (বিজয়গড়ের মতোই) নামে। যদিও ‘গড়’ নামের আড়ালে রয়েছে ইতিহাস।
কলকাতার উদ্বাস্তু উপনিবেশে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (অবশ্যই বাংলা মাধ্যম)। উদ্বাস্তু শিশুদের পড়াশোনার সুবিধার্থে বিদ্যালয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল। পড়াতেন স্থানীয় শিক্ষিত বাসিন্দারাই।
গড় অর্থে দুর্গ। অবৈধভাবে দখলকৃত জমিতে কলোনি গড়ে ওঠায় জমির মালিক ও সরকার যৌথভাবে দখলদারদের অপসারণের চেষ্টা করে। উদ্বাস্তু ও স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। এমনকি শরনার্থীরা তাদের উচ্ছেদ করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ করে। বিজয়গড়, আজাদগড় বা রামগড়ের মতো শরনার্থী এলাকাগুলি নিজেদের দুর্গ ধরে রাখার সাফল্যকে চিহ্নিত করছে। প্রতিরোধের স্মারকচিহ্ন হিসেবে আজও এই এলাকাগুলির নাম অক্ষত রয়েছে।

এই লেখা লিখতে গিয়ে দারুণ এক তথ্য পেলাম নানা জায়গায়। কলকাতার উদ্বাস্তু উপনিবেশে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (অবশ্যই বাংলা মাধ্যম)। উদ্বাস্তু শিশুদের পড়াশোনার সুবিধার্থে বিদ্যালয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল। পড়াতেন স্থানীয় শিক্ষিত বাসিন্দারাই। এমন প্রামাণ্যচিত্র দেখতে পাওয়া যায় ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে। সেখানে উদ্বাস্তু কলোনির শিক্ষক ছিলেন হরপ্রসাদ (বিজন ভট্টাচার্য)। শ্রীঘটক এই চরিত্রের মধ্যে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান এবং সমাজ গঠনের কারিগরকেই বুঝি দেখাতে চেয়েছিলেন। বর্তমান কলকাতার কলোনি অঞ্চলে সেই সময়ে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়গুলির মাহাত্ম্য হ্রাস পেয়েছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলি প্রাধান্য দিচ্ছেন ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিকে। তাই আজ আর বাংলা মাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে না। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একাধিক বিদ্যালয়। উদ্বাস্তু অঞ্চলগুলি হয়ে উঠেছে এ শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য (বলা ভালো দামী) জায়গা। প্রতি বছর বেড়ে চলেছে জমি বা ফ্ল্যাটের দাম। পাশেই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস এবং মেট্রো রেলের দীর্ঘ লাইন। কলোনি অঞ্চলগুলির দাম তাই আকাশচুম্বী হয়েছে। বেড়েছে শপিং মল, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, সুপার মার্কেট। কমেছে পঞ্চাশের দশকে গড়ে ওঠা সাধারণ পাঠাগারগুলির গুরুত্ব।
এর মধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটে। হিন্দু উদ্বাস্তুরা জমি দখল করতে শুরু করলে মুসলমানরা ক্রমশ এলাকা ছাড়তে থাকেন। অনেকেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে চলে যান, যেখানে তাঁদের সহধর্ম মানুষের সংখ্যা তুলনায় বেশি। মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা কলকাতা ছেড়ে যাননি বা ছাড়তে চাননি, তাঁরা চলে যান শহরের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার সেলিমপুর অঞ্চলে। নাম শুনলেই বোঝা যায় যে, একসময় এই অঞ্চলে মুসলিমদের দাপট ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর এইসব অঞ্চলে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠলে কবরস্থানগুলি ক্রমশ শিশুদের খেলার মাঠে পরিণত হয়। বর্তমানে সেলিমপুরে হাজার হাজার হিন্দুর বাস, তুলনায় স্বল্প সংখ্যক মুসলিম পরিবার বাস করে।
বিজয়গড় কলোনি ঘেঁষা নেতাজি নগরে রাস্তার এক মোড়ে দেশভাগের যন্ত্রণাকে স্মরণ করতে নির্মিত হয়েছে মূর্তি। সেখানে লেখা, “এই মূর্তিটি অঞ্চলের উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতীক, সৌজন্যেঃ নেতাজি নগর বাস্তুহারা সমিতি”।
দেশভাগের ভিত যদি হিন্দু-মুসলিম জাতির সংঘর্ষ থেকে হয়েও থাকে, তবে কিছু অংশে এখনও তা অব্যাহত আছে। ভারত এবং বাংলাদেশ – দুই দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যেই খেলা করছে সাম্প্রদায়িকতা। এ ঠান্ডাযুদ্ধের হয়তো শেষ নেই। তবুও আজ কলকাতার কলোনিগুলো যন্ত্রণার কথা বলে। পড়শিরা স্মৃতিচারণ করেন ফেলে আসা দেশের বন্ধুদের। কেউ কেউ মনে করিয়ে দেন বন্ধুর কোনো জাত নেই। ১৯৪৮ সালে নির্মিত বিজয়গড় কলোনি আজ মাছের বাজারে পরিণত হয়েছে। আবার কিছু শরনার্থী শিবির হয়ে উঠেছে মন্দির বা ক্লাবঘর। বিজয়গড় কলোনি ঘেঁষা নেতাজি নগরে রাস্তার এক মোড়ে দেশভাগের যন্ত্রণাকে স্মরণ করতে নির্মিত হয়েছে মূর্তি। সেখানে লেখা, “এই মূর্তিটি অঞ্চলের উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতীক, সৌজন্যেঃ নেতাজি নগর বাস্তুহারা সমিতি”।
তাই দেশভাগের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধারণ করেছে কলকাতা। প্রবীণ বাসিন্দারা ‘এক কাপড়ে ভিটে ছাড়ার’ স্মৃতিচারণ করেন। চোখের কোণ ভিজে যায় আজও।