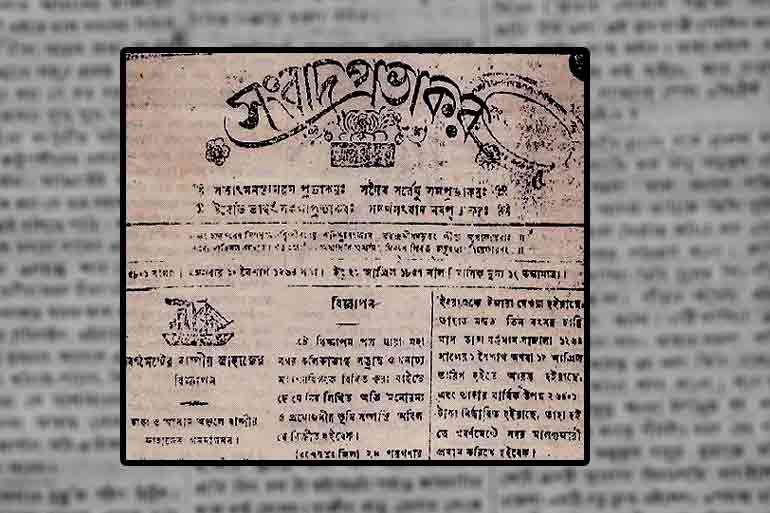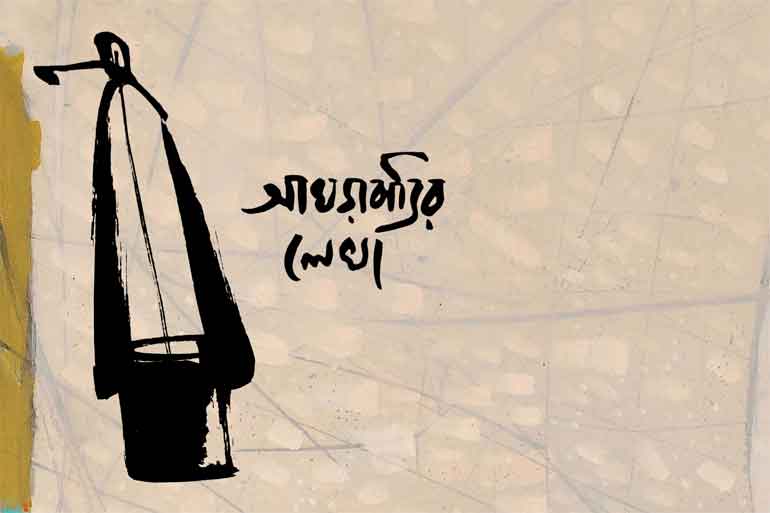কলকাতার পুজোর পালাবদল

‘ভেবেছিলাম অকালবোধন নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকবে!’ ক্যামেরার সামনে থেকে উঠতে উঠতে বললেন অভয় ভট্টাচার্য্য। বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজোর পুজোর এই ২০১৭ সালের ভাইস প্রেসিডেন্ট। (আমরা মানে, আমি, শৌর্য, পৃথা, আকাশ, রনজয়-রা মিলে কলকাতার পুজো নিয়ে তথ্যচিত্র বানাচ্ছিলাম বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত একটি দৈনিকপত্রের জন্য। প্রধানত বাগবাজারের প্রতিমার সাজ নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম অভয়বাবুর কাছে। উত্তর মিলেছিল যথার্থ কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছিলেন হামেশাই ‘আমরা বাগবাজার’ এই শব্দবন্ধ।) বাগবাজারের পুজো এবার নিরানব্বই বছরে পড়ল। তাঁদের দাবি, উনারাই কলকাতার সর্বপ্রথম বারোয়ারি পুজো। সঙ্গত কারণও আছে তার। সে সব প্রসঙ্গে পরে আসছি।
ইতিহাস সাক্ষী রেখে বলতে পারি কলকাতার প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো কিন্তু ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট স্ট্রিটের ‘সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা’র দুর্গোৎসব। প্রমাণিত তথ্য এই যে এদের কাছ থেকে দশকর্ম ভাণ্ডারের ফর্দ নিয়ে বাগবাজারের ১৯১৮-র পুজোর বাজার শুরু হয়। আদিগঙ্গা সংলগ্ন ঘাটটি গোবিন্দপুরের সতীস্থল বলে চিহ্নিত। আজও সেখানে বিদ্যমান সেই সাক্ষ্যবহনকারী ফলকটি। মজে যাওয়া আদিগঙ্গার সংলগ্ন পুজোস্থলের অনতিদূরেই সতীপাঠ, কালীঘাট। ফলে স্থানমাহাত্ম্যে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানিই। কিন্তু উদাসীনতার কারণেই হোক বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই হোক এই বারোয়ারি পুজো গুরুত্ব হারিয়ে ঐ মজে যাওয়া আদিগঙ্গারই রূপ নিয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে স্থানমাহাত্ম্যের সামাজিক গুরুত্ব হেতু বাগবাজার কিন্তু শততম বছরের দ্বারপ্রান্তে এসেও জৌলুসহীন হয়ে পড়েনি। বারোয়ারি পুজোর আয়োজন একরকম বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বৈকি। প্রাথমিক ভাবে যুবসমাজকে উদ্ধুদ্ধ করার কাজে এই পাঁচদিনের পুজো আয়োজনের ভূমিকা ছিল বিরাট। ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা পুজোর প্রধান কর্ণধার রূপে অবতীর্ণ হতেন। বাগবাজার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শুরু করে দক্ষিণের সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল সঙ্ঘশ্রী, সঙ্ঘমিত্র, সহযাত্রী, মুক্তদল, ফরওয়ার্ড ক্লাব, যুবমৈত্রী - সর্বত্রই চিত্রটা একইরকম ছিল। আজও বাগবাজারে ধুমধাম করে বীরাষ্টমী পুজো হয়, গ্রামীণ মেলা বসে, লাঠি খেলা ইত্যাদির প্রদর্শন নিয়ম করে হয়। এই যে পুজোর ছলে যুবসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ করে রাখা এও একপ্রকারের থিম আর সেই থিমকে ঘিরে আচার অনুষ্ঠান এবং পুজো আবহ নির্মাণ – ব্যাপারটা এখনও চলছে।
পৃথিবীতে কোনও ভাবনা বা বিষয়চিন্তার উদ্ভব হতে যেমন দীর্ঘ সময় লাগে, তেমনই তার পালনকালের ইতিহাসও দীর্ঘতর। ফলত বারোয়ারি পুজোভাবনার উদ্ভব থেকে শুরু করলে তার পালনকালের এক দীর্ঘ ইতিহাস পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে এক অতিদীর্ঘ পরিসরের প্রয়োজন। বর্তমান এই আলোচনায় ইতিহাসের কিছু আন্দাজ দিলেও ঐতিহাসিক রচনার অভিপ্রায় নেই আমার। তাই এক লাফে বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে আসি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতার বারোয়ারি পুজোর ক্ষেত্রে একধরনের নতুন আঙ্গিক চোখে পড়তে শুরু করল। সে ব্যাপারে একটু আলোকপাত করা যাক।
কালের নিয়মে অভয় ভট্টাচার্য্যরা পিছু হঠতে থাকে। মর্ডান ডেকরেটার্সদের স্থলাভিষিক্ত হল একঝাঁক আর্ট কলেজের থেকে পাশ করা শিল্পীর দল। তাঁরা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে পুজো পরিবেশ রচনা করে দেখিয়ে দিলেন।
একটা সময় এসেছিল ৭০এর শেষ এবং ৮০-র দশকের শুরুতে, যখন পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেল পাহারা দিত ঢাকীর দল আর পাড়ার গুটিকয় বুড়োবুড়ি। সঙ্গী তাঁদের তারস্বরে সাউন্ড বক্সের বজ্রনির্ঘোষ- “কাঁহা সে আয়া, ম্যায় হু কৌন-”। অতি বুদ্ধিমানেরা তখন পুজোয় সিমলা, কুলু, মানালির পথে। ঐ শিল্পীরা পালটে দিয়েছিল সেই সমাজচিত্র। সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বেশকিছু কর্পোরেট পুরস্কারের হাতছানি। উত্তরোত্তর বদলাতে লাগল পুজো শিল্পের চেহারা - অমর সরকার, তরুণ দে, পুণেন্দু দে, ভবতোষ সুতার, সুশান্ত পাল, শিবশঙ্কর দাস, সনাতন দিন্দা প্রভৃতিদের হাতযশে। কলকাতার পুজোয় হাত পাকিয়েছিলাম আমিও এবং যারপরনাই এই খোলামাঠের কাজের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছি। বর্তমান চিত্রটা একেবারেই অন্যরকম। সিমলা, কুলু মানালির পথে এখন পুজোর ভিড় কমে গেছে। ‘ম্যায় হু ডন’-এর জায়গায় এখন থিম মিউজিক। সবুজ টিউবের পুজো মাঠে প্রবেশ নাস্তি। তা শুধুই ভোটের ফলের পরে পাড়ার ক্লাবের সামনেটা আলোকিত করে। এখন ডিজাইনার আলো। তাতে অন্ধকারই বেশি অবশ্য। আর আছে ডিজাইনার পোশাক। তবে সপ্তমীর রাত পোহালেই সব ম্লান। পুরস্কার ঘোষণা হয়ে গেলেই ঝলমলে পুজো শ্রাদ্ধবাসরে পরিণত হয়।
এভাবেই চলে বছরের পর বছর। বিসর্জনের পরেই আবার যে কে সেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় বাছাই প্রতিমার শোভাযাত্রা যায় রেড রোডে। পুজো কমিটির খরচের খাতায় নতুন সংযোজন ‘বিদায়বেলার ট্যাবলো’। এবছর এক পুজো কমিটির বাজেট কম করার আবদারে বলেছিলাম পুজোর নকশাটা ভাবছি ষোলচাকার ট্রেলারের উপর করব; পুজো আর বিসর্জন একসঙ্গেই করা যাবে, খরচও বাঁচবে - খুশি হননি তারা। যাইহোক না কেন, পুজোর প্রাক্কালে পুজোশিল্পী, থিম, পুরস্কার এসব নিয়ে যে প্রচণ্ড লেখালেখি চলে তাতে আম আদমির মগজে প্রচুর শিল্পভাবনা ঢুকে যায় সন্দেহ নেই - যেমনটা একটা গানের রিয়েলিটি শোয়ের বিচারকদের সঙ্গীত বিশ্লেষণের গুণে বাংলার ঘরে ঘরে সঙ্গীত প্রভাকর জন্মে গেল রাতারাতি তেমনই থিমের দৌলতে আম আদমি দৃশ্যকলার মারপ্যাঁচ জেনে গেল অচিরেই। ফলে নতুন করে বুদ্ধি বিচার নাইবা করলাম। আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করি এই লেখায়। যেমন -
১) বর্তমান থিম পুজোর প্রাক্কালে কুমোরটুলির জগৎ মুখার্জী পার্কে অশোক গুপ্ত ছিলেন অবিনাশ কবিরাজ বাড়ির ছেলে। বাড়ির অমতে প্রতিমা বানানোর কাজ শিখতে গিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং প্রখ্যাত ভাস্কর সুনীল পালের কাছে আশ্রয় নেন। সুনীলবাবু সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষক ছিলেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্থাপত্য নকশায় ওনার অসামান্য কৃতকর্মের নিদর্শন আমরা দেখি। বর্তমানে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর বাইরে করা তাঁর ভিত্তিচিত্রটি, নতোন্নত ভাস্কর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সন্দেহ নেই।
২) এই বাংলায় দুর্গার একচালি-কে পাঁচচালিতে ভেঙে দেন গোপেশ্বর পাল। ১৯১৭ সালে কুমারটুলি সার্বজনীনের পুজোয় এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি ওনার বানানো।
৩) কুমারটুলির কাছে, উল্টোডাঙার গায়ে তেলেঙ্গাবাগানে আছে প্রদীপরুদ্র পাল-দের পাঁচটি ঠাকুরঘর। ওঁরা বলেন কারখানা। ঐ জায়গা পাবার জন্য প্রদীপকে অঞ্চলের তেলেঙ্গাবাগান ক্লাবের কর্তারা বলেছিলেন তাঁদের পুজোটা কেমনভাবে গুছিয়ে করা যায়, সেটা করে দিতে। শর্তসাপেক্ষে প্রদীপ তা করে এবং তার বিনিময়ে ওইখানে বড় জায়গার লিজ পায় প্রদীপ। এই তেলেঙ্গাবাগানের পুজো কলকাতার থিম পুজোর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।
৪) বকুল বাগান সার্বজনীন ১৯৭৫ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের দিয়ে প্রতিমা বানায়। ১৯৭৫-এর প্রতিমা ছিল নীরদ মজুমদারের করা।
৫) সংঘশ্রী ক্লাব(ভবানীপুর) পুজোকে একটা নাটকীয় আবহে পেশ করত। প্রতিমা শিল্পী ছিলেন জিতেন পাল। আর সিনারি আঁকা হত কালী স্টুডিওতে।
৬) বাগবাজারের প্রতিমার মুকুট বানানো কৃষ্ণনগরের বাচ্চি মুখার্জি নামে এক শিল্পী। ১৯৯৯ থেকে ঐ কাজ করে আসছেন। তিন থাকের মুকুটের উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট। এ বছর বাগবাজার ৯৯ বছরে পা দিল।
৭) জার্মান শিল্পী গ্রেগর স্নাইডার প্রথম কলকাতায় পুজোর মাঠে কাজ করেন। একডালিয়া এভারগ্রীন ক্লাবের পুজোয়। খুব কিছু জমেনি সেবার। পরে বিদেশী শিল্পী বলতে ট্রেসি লী স্ট্রাম, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসে হাত লাগান কাজে। সঙ্গে ছিলেন এদেশের শিল্পীবন্ধু দীপ্তেশ ঘোষদস্তিদার ও শান্তনু মিত্র। অপূর্ব হয়েছিল পুরো কাজটা। ফলে দুর্গাপুজো শিল্প বিদেশেও সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে যেতে লাগল। যদিও পুরো কাজটাই ভিড়ের অভিরুচির উপর নির্ভরশীল, তাই একা শিল্পীকে নতুন নতুন ভাবনায় পরিসর দিতে হয়।
৮) থিমের নাম দেওয়া থেকে শুরু করে থিমের গান রচনা – সবগুলোতেই শিল্পী নিজে দায়িত্ব নিতেন, কিছু এসব এখন বিভাগীয় এক্সপার্টরা দায়িত্ব নিয়ে নেন।
৯)থিমের কাজের এখনও অবধি তিন ধরনের নিদর্শন দেখি - অ) স্থাপত্যের অনুকরণ, আ) নতুন স্থাপত্যের রচনা ও গ) মাধ্যম নির্ভরতা। বর্তমান পুজোর মাঠের কাজের আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সূর্যোদয় দেখে ফেলছি সবাই অতি সহজেই।
১০) শুধুমাত্র দৃশ্যশিল্পীরাই নন, পুজোকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কলাশাখার মানুষ এসে যোগ দিচ্ছেন। যেমন আলোর ডিজাইনার, শব্দের কারিগর সঙ্গীতের ব্যাক্তিত্বরা।
যে কাজ জন্মমাত্রেই বিসর্জিত হবার জন্য নির্ধারিত তাকে পাবলিক আর্টের রেফারেন্স হিসাবে ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতের লাভ। সংগঠন এবং শিল্পী, এই দুয়ে মিলে যে একটা সামগ্রিক সমাজচিত্রের জন্ম দেবে। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমরা ভবিষ্যতের আশ্রয়ে রইলাম।