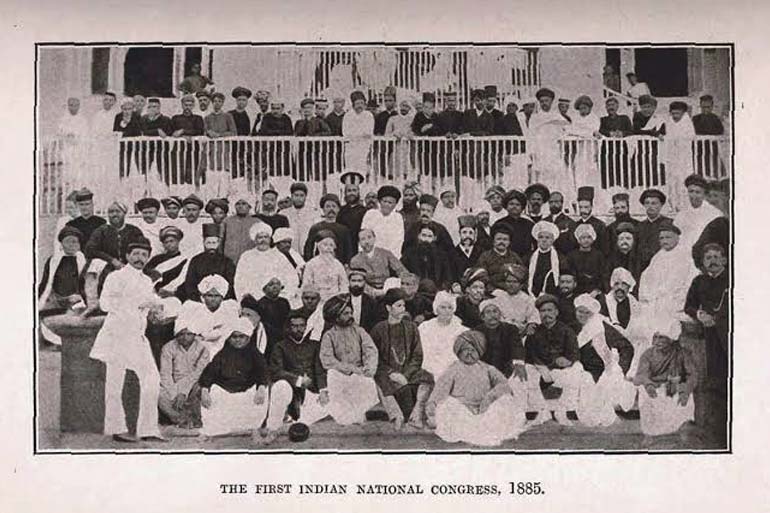রাধাকৃষ্ণনের তত্ত্বাবধানে অক্সফোর্ড থেকে ‘ডি-লিট’ উপাধি পেলেন রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষক দিবস (Teachers Day) ও রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন— দুটি প্রসঙ্গ এখন মিলেমিশে এক। রাধাকৃষ্ণন (Sarvepalli Radhakrishnan) ছিলেন এক অন্যতম রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক। জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন তিনি। মহীশূর কলেজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও পিকিং, মস্কো, বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। ‘স্যার’ উপাধি পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান রয়্যাল অ্যাকাডেমির সদস্য হয়েছিলেন। ইউনেস্কোর ভারতীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণন। বক্তৃতার জন্য ঘুরে বেরিয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে— টোকিও, কলম্বিয়া, হনলুলু, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। দেশবিদেশের অনেক মনীষীর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল রাধাকৃষ্ণনের হৃদ্যতা। রবীন্দ্রনাথ তখন সেরা ব্যক্তিত্ব। রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে পরিণত হবে।
সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণন। বক্তৃতার জন্য ঘুরে বেরিয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে— টোকিও, কলম্বিয়া, হনলুলু, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। দেশবিদেশের অনেক মনীষীর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল রাধাকৃষ্ণনের হৃদ্যতা।
রবীন্দ্রসাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণনের রবীন্দ্রনাথের (Rabindranath Tagore) সঙ্গে প্রথম আলাপ। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর অনেক লেখার অনুবাদ হয়। রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথের অনূদিত সাহিত্য পড়েছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময় রাধাকৃষ্ণণ সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েছিলেন। জীবনে দারিদ্র্য এবং কঠিন মানসিক জটিলতার মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছিলেন যখন রাধাকৃষ্ণন, তখন অনেক রকম দর্শন পাঠ করেও শান্তি পাচ্ছিলেন না। এইসময় তিনি পড়েছিলেন, গীতাঞ্জলির অনুবাদ। গীতাঞ্জলির দর্শন মুগ্ধ করে রাধাকৃষ্ণনকে। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে বহন করে নিয়ে চলেছেন, এই বিশ্বাস হয়েছিল রাধাকৃষ্ণনের। তিনি নিজে একজন দার্শনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলেই মনে করতেন। ‘কোয়েস্ট’ পত্রিকায় রাধাকৃষ্ণনের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল— রাধাকৃষ্ণনের অধ্যাত্মবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ লেখাটি পড়েন এবং মুগ্ধ হয়ে রাধাকৃষ্ণনকে পত্র লেখেন। এই প্রথম দুই মনীষীর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সেতু তৈরি হল।
এই পত্র পেয়ে রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং আরও আরও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ খোঁজ করে পড়তে থাকেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবনা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের নিজস্ব বোধ তৈরি হল। ‘থটস অফ টেগোর’ নাম দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ম্যাকমিলান কোম্পানি ‘ফিলোসফি অফ ট্যাগোর’ নামে এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে বই প্রকাশ করতে চান। রাধাকৃষ্ণন প্রস্তাবিত এই বইটির পাণ্ডুলিপির একটি কপি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে প্রশস্তি লিখতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তবে রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধে ১৯১৮ সালে বইটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকা-সহই। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের সাক্ষাৎ হয় মহীশূরে গিয়ে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের পরিচিতি বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রাধাকৃষ্ণনের আক্ষেপ ছিল তিনি বাংলা ভাষা না জেনে রবীন্দ্রনাথ পড়েন। এরপর যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন রাধাকৃষ্ণন, তখন তাঁর রবীন্দ্রচর্চা আরও গভীরতা পেল। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসও নির্মাণ করলেন। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণন। প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। রাধাকৃষ্ণন তখন শান্তিনিকেতনে কবির আতিথ্য গ্রহণ করলেন।
রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের সাক্ষাৎ হয় মহীশূরে গিয়ে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের পরিচিতি বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রাধাকৃষ্ণনের আক্ষেপ ছিল তিনি বাংলা ভাষা না জেনে রবীন্দ্রনাথ পড়েন।
সৃজনশীল দর্শনচর্চা নিয়ে আলোচনা হল দুজনের। রবীন্দ্রনাথ কবীর, দাদূ, বাউল এবং মধ্যযুগের সব ধর্মীয় কবিসম্প্রদায়ের সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনকে বলেন। এইসব কবিদের কবিতা তর্জমা করে শোনান। এরপর ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধ গ্রহণ করে সভাপতিত্বের প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাষণটি ‘ফিলজফি অফ আওয়ার পিপল’ নাম দিয়ে ‘মর্ডান রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জন্মদিনে, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধ রাখতে পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে আবার রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন রাধাকৃষ্ণন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুন্দর মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করেন ‘পরিশোধ’ নাটক। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হয়, তার অন্তরালে ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি হিসেবে রাধাকৃষ্ণনই এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সাম্মানিক ডি-লিট তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের হাতে। এই ছিল তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ।
এরপর জীবনে আরও অনেকটা পথ এগোবেন সর্বপল্লী শ্রীরাধাকৃষ্ণন। তাঁর অন্তরে পবিত্র অগ্নির মতো সবসময় আলো দেখাবে রবীন্দ্রনাথের দর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়েই থাকবেন আমরণ।
__________
সহায়ক প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণন, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব, তাপস ভৌমিক (সম্পা), কোরক, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা