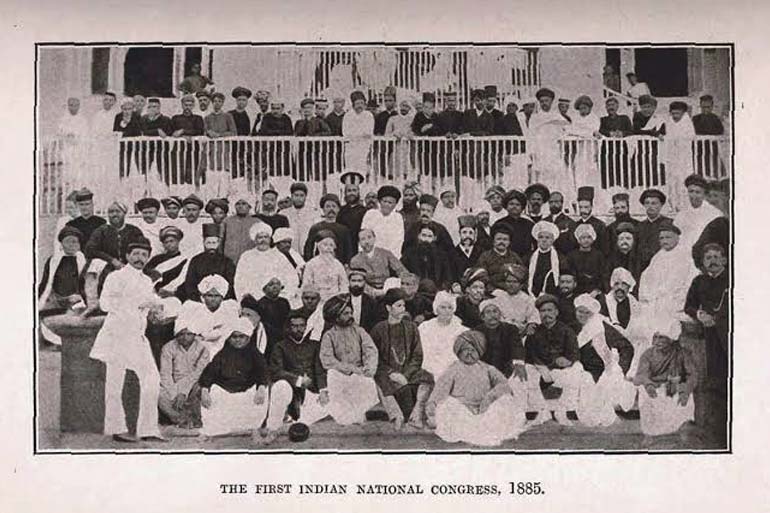ইন্দিরাদেবীর পারিবারিক খাতায় রবিকাকার দিনলিপি

জীবনের গতি ঠিক নদীর মতো। মোহনার দিকেই তার গন্তব্য। ধন, মান, প্রেম, অহংকার কিচ্ছু থাকে না। থাকে শুধু স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি ইন্দিরাদেবীর অনেকগুলি সংগ্রহের খাতা ছিল। সেগুলিতে গান, রান্না, পারিবারিক ঘটনা সবটাই লেখা থাকত। ভবিষ্যতের মূল্যবান নথি হিসেবে সেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও পরিবারকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন ইন্দিরাদেবী। তিনি নিজেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড্ড আপন।
ইন্দিরাদেবী লিখেছেন, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেমন, বড়ো ছেলের বিধবা বিবাহ দেওয়া, বড়ো মেয়ের যে শ্রেণির ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তা কুটুমদের পছন্দ হয়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা জোটে। ইন্দিরাদেবী শুনেছিলেন, অতিনিকট কটুমবাড়িতেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার নিমন্ত্রিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মেয়ের বিয়েতেও অনেক কুটুম পরিবার যোগ দেননি। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতোই চলেছেন। ব্রাহ্মসমাজের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না তিনি। বেলার বিয়ের সময় ইন্দিরাদেবীরা শরৎকে নয়, তার ভাইকে বেলার বর বলে ঠাউরেছিলেন। কারণ শরতের পরের ভাই বেশি সুদর্শন ছিলেন। অবশ্য পরে এই নিয়ে কোনো আপশোস ছিল না। কারণ বেলার প্রতি শরৎ খুব অনুরক্ত ছিলেন। বেলার মৃত্যুর পর ইন্দিরা তাঁর শ্রীরামপুরের বাড়ি গিয়ে দেখেছিলেন বেলার একটি বড়ো ছবির তলায় শরৎ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। রবীন্দ্রনাথের আরেক মেয়ে রানির মৃত্যুর পর তার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথকে ডাক্তারি পড়তে বিলেত পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি সেখানে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মেজো মেয়ে রানির অসুস্থতার সময়ও প্রাণপণ যত্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হাওয়া বদল, চিকিৎসা, আদর সব! যানবাহনের ঝাঁকুনিতে রানির কষ্ট হয়। সেজন্য রানিকে ডুলিতে চড়িয়ে আলমোড়া থেকে নীচের রেলওয়ে স্টেশনে অতটা পথ সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলেন। ছোটোছেলে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুও বড়ো বেদনার মতো বেজেছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। শমী একটি বৃক্ষলতা রোপণ করেছিল। শমীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ রোজ নিজে সেই লতায় জল দিতেন।
ইন্দিরাদেবী লিখেছেন, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেমন, বড়ো ছেলের বিধবা বিবাহ দেওয়া, বড়ো মেয়ের যে শ্রেণির ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তা কুটুমদের পছন্দ হয়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা জোটে। ইন্দিরাদেবী শুনেছিলেন, অতিনিকট কটুমবাড়িতেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার নিমন্ত্রিত ছিলেন না।
ইন্দিরাদেবী লিখেছেন, “রবিকাকার পারিবারিক স্মৃতি লিখতে বসে প্রথমেই একথা মনে না হয়ে যায় যে, অতুল প্রতিভা ও বিশ্বব্যাপী খ্যাতি যিনি পেয়েছিলেন, পারিবারিক জীবনে তিনি অনেক দুঃখও পেয়েছিলেন।” তবু তিনি রবীন্দ্রনাথ! আলোর অপর নাম।

ইন্দিরাদেবীর তরুণবেলায় রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন সকলের স্টাইল আইকন। তাঁর লম্বা কোঁকড়ানো চুল অনেক যুবকের কাছে অনুকরণীয় ছিল। পরে তাঁর ঋষিতুল্য চেহারাও। ছোটোবেলায় তাঁকে মা, দিদিরা সকলে কালো বলতেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় আশ্চর্য জেল্লা ছিল। শরীরচর্চা করতেন নিয়মিত। খাবার নিয়ে চলত তাঁর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা। রুটিতে রেড়ির তেলের ময়ান দেওয়াতেন। যাতে আহার আর স্বাস্থ্যরক্ষা দুটোই একসঙ্গে হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভরসা করতেন। অনেককে নিজে ওষুধও দিয়েছেন। মৃণালিনীদেবীর অসুস্থতার সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ধরেছিলেন। মৃণালিনীর মৃত্যুর পর অনেকে এই নিয়ে তাঁকে অভিযোগও করেন।
রবীন্দ্রনাথের সেবাগুণ ছিল অতুলনীয়। ইন্দিরাদেবীর স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথা আসে। তাঁর স্ত্রীর নাকি এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি চোখ বুজে থাকলেও তাঁর চোখের উপর বই রেখে দিলে তা তিনি পড়তে পারতেন। মীরাদেবীরা এই মহিলাকে জ্যাঠাইমা ডাকতেন। ছোটোবেলায় ইন্দিরাদেবীরা ‘প্রমারা’ বলে একটি পয়সার খেলা খেলতেন। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন এসব সাধারণ খেলায় যোগ দেননি। তিনি খেলতেন ও খেলাতেন মুখে মুখে পালা করে গল্প তৈরির খেলা। ‘মেরি সার্কেল’ নামে এক ইংরেজি বই দেখে ঘরে বসে খেলার কথা জানা যেত। মূকনাট্য বা ডাম্বশারাড খেলাও খেলাতেন রবীন্দ্রনাথ। এই খেলার নেশায় ছোটোরা প্রায় সামাজিক বাক্যালাপ উঠিয়ে দিয়েছিল। কাজেই সে খেলা বন্ধ করা হয়। কিন্তু ডাম্বশারাডের স্মৃতি রয়ে গেছে ইন্দিরাদেবীর পারিবারিক স্মৃতি সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে যে সামান্য ঈর্ষা করতেন, সেকথা জানিয়েছেন ইন্দিরা। কারণ কাদম্বরীদেবী পশমের আসন বুনেছিলেন বিহারীলালের জন্য।
ইন্দিরাদেবীর তরুণবেলায় রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন সকলের স্টাইল আইকন। তাঁর লম্বা কোঁকড়ানো চুল অনেক যুবকের কাছে অনুকরণীয় ছিল। পরে তাঁর ঋষিতুল্য চেহারাও। ছোটোবেলায় তাঁকে মা, দিদিরা সকলে কালো বলতেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় আশ্চর্য জেল্লা ছিল।
রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের খুব ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় ইন্দিরাদেবীদের হাসাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক রঙ্গভঙ্গ করে হিন্দি ও ইংরেজি গান গাইতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ির আরো অনেকের মধ্যে আদিম শিশু মনটি চাপা পড়েছিল। তাই বুঝি তাঁরা অত সরস ও সজীব ছিলেন। মৃণালিনীদেবীর রান্নার কথাও পারিবারিক খাতায় লেখা। রাঁধতে আর খাওয়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। মৃণালিনী নিজগুণে সকলের প্রিয় হয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে বেলার গায়ের রং ছিল ধপধপে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি মজা করে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “রবি তোমার রং তো তেমন সাফ নয়, ছোটো বৌয়ের রংও শ্যামলা, তবে বেলার অমন রং হল কী করে?” তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “মেজদা, আপনার কি মেজোবোঠানেরও রং তেমন সাফ নয়, তবে সুরেন বিবির রং এমন হল কী করে?” ইন্দিরাদেবীর স্মৃতিচারণায় একটা খুব খাঁটি কথা আছে। তখনকার দিনে পুরোনো দাসীর পছন্দের উপরেই পাত্রী নির্বাচনের রেওয়াজ ছিল। সুন্দরী মেয়ের চাহিদা আর সামাজিক চাহিদা সবসময় মিলত না। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিশ্রুত কবি না হলেও কবি, সুপুরুষ ও ধনীর সন্তান তো ছিলেনই। কিন্তু গুরুজনে তাঁর জন্য যে পাত্রী পছন্দ করেছিলেন, তাঁকে প্রসন্ন চিত্তে বিয়ে করা ছাড়া যে আর কোনো স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা যেতে পারে তাঁর সম্ভাবনাও ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মনে আসত না। স্ত্রী বিয়োগের পরেও তারা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। ইন্দিরাদেবী লিখছেন, “তাঁদের তুলনায় তাঁদের স্ত্রীরা প্রায়শ বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণে অনেক নিরেস হলেও তাঁরা যোগ্য সম্মান ও প্রীতিলাভে কোনোদিন বঞ্চিত হননি।”
ইন্দিরাদেবীর খাতাভরা স্মৃতির হিরেমাণিক! তার কতটুকুই বা স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের গল্প চলতে থাকুক মনে মনে। গল্পের আড়াল থেকে আবির্ভূত হোক মানবিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে দেবতা বা গুরুদেব বানানোর প্রয়াসের প্রতিকূলে রয়ে যাক তাঁর দুঃখ সুখে ভরা সংসার আর একলা কবির অবয়ব। ইন্দিরাদেবীর পারিবারিক খাতার সাধ্য নেই তাঁকে ব্যাখ্যা করার।
____
সহায়ক গ্রন্থ
রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী