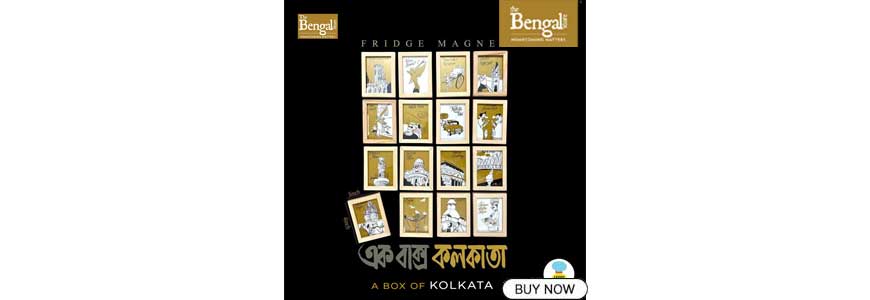বাঙালির রুচিবোধে যৌনতা বা যৌনদৃশ্যের ঠাঁই আজ কতটুকু?

সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে ছবিতে স্বাতীলেখা-সৌমিত্রর চুম্বন দৃশ্য
সিনেমার যৌনদৃশ্য দেখে যে দর্শক নিজে পুলকিত হচ্ছে, আবার সেই দর্শকই অনেকসময় বিশেষ কোনো দৃশ্য লিক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিচ্ছে। ‘পুরুষতান্ত্রিক ভদ্র বাঙালি’ যে যৌনতাকে প্রত্যাখান করল, তা কি ফিরিয়ে আনতে পারছে?
বাঙালি ও তার যৌনভীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে, প্রথমে যা বলতে হয়, তা হল বৃহত্তর ক্ষেত্রে বর্তমান বাঙালির রসবোধের অভাব। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলার তন্ত্র’ বইয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক ও বৈদিক পরবর্তী বেশ কিছু যুগ অবধি কাম ও যৌনতাকে দেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে যে ধারণা পাওয়া যায়, তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, এই অতীব স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যে ক্রমশ মানবিক বিকার ঘটেছে বা ঘটে চলেছে, তার জন্য বুঝি বর্তমানে বাঙালির মাতৃ ভাষার পাঠ, পাঠ্য ও বর্ণের প্রতি অনুনাশিকতা এর জন্য দায়ী। কীভাবে এই ফাঁক তৈরি হল এবং আদৌ বর্তমান বাঙালির মননে রসবোধের সঞ্চার সম্ভব কিনা বোঝার জন্যই এই লেখা। এ ক্ষেত্রে বাঙালি জনজীবনের বিবর্তন নিয়ে এই লেখার সূচনা করা প্রয়োজন এবং ক্রমে ক্রমে আমরা ফিল্মের জগতে পদার্পণ করে বোঝার চেষ্টা করব যে রসহানী কোথায় ও কেন ঘটছে এবং তার কোনোরকম প্রতিকার করা সম্ভব কিনা!
বামপন্থী ধারণা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত বৈষম্যে বিভাজিত হল এই বঙ্গসমাজ। যেখানে জয়দেব-চণ্ডীদাসের কাব্যরসের আরোহণ রীতিমতো হীন রূপে দেখা হল।

উপমহাদেশের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় বাঙালি জনজীবনে ইংরেজি শিক্ষার প্রকাশ বহু আগে ঘটে গিয়েছিল। এই উল্লেখ পাই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ বইতে। বঙ্গপ্রদেশে মুঘল সাম্রাজ্য যখন চূড়ান্ত ডামাডোল ও দুর্নীতিতে আক্রান্ত, ঠিক সে সময় ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে বিস্তার করছে তাদের সাম্রাজ্য। তার সমসাময়িক অবস্থানে তখন এই রামতনু লাহিড়ীর মতো বেশ কিছু মানুষ এবং তাদের পরিবার ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী হতে শুরু করেন। সেভাবে দেখতে গেলে তাঁরাই ভদ্র বাঙালি কেরানি সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হিসেবে গণ্য। যদিও তখন তাঁরা পাশ্চাত্যের আদব কায়দায় নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও, নিজেদের সংস্কৃতিকে একেবারে জলাঞ্জলি দেননি। কিন্তু বর্তমানে বাঙালির শিল্প ও সাংস্কৃতিক মনোভাব যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তা দেখলে বিহার প্রদেশের কথা মনে পড়ে। মাগধীয় সময়ে বিহার হয়ে উঠেছিল পাঠ ও পঠনের কেন্দ্রবিন্দু। সেখান থেকে বর্তমানে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের যে সামাজিক অবক্ষয় দিনে দিনে হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলার সার্বিক ক্ষয়ের একটা সমতা আছে – এই কথা বোধহয় বলাটা খুব একটা ভুল হবে না। কিন্তু জরুরি হয়ে দাঁড়ায় অন্য একটি বিষয়। যে প্রোলেতারিয়ান কালচার ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিল, তাকে কতটা রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক ভাবে দেখা বা পড়া হয়েছে তা সন্দেহ আছে।

রনি সেনের বহু প্রশংসিত ছবি ক্যাট স্টিকস
ফিরে আসি রামতনু লাহিড়ী ও তাঁর মতো কেরানিকূলের ইতিহাসে। কারণ সেখানেই বোধহয় লুকিয়ে আছে বর্তমান বাঙালির কামবোধের অবক্ষয়। উনিশ শতকের মাঝামঝি সময়ে এই কেরানিকূল ক্রমে বাংলার বুকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। তাদের হাত ধরেই আমরা আবার এক ধরনের চিন্তা ও শিক্ষার প্রসার দেখলাম। যার মধ্যে পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও শিল্পের রুচির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। উপমহাদেশে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের ধারণা একটা বিশেষ স্থান তৈরি করতে আরম্ভ করল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র – ইতিহাসের এই পথ ধরে এগোলে সেই জাতীয়তাবাদের একটা পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের এই ধারণা তৎকালীন সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও তাকে অনেকটাই যত্ন নিয়ে ভারতীয় (বৈদিক) দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রবাহিত করা হল। যদিও এই ভাবনা ও তার উগ্র প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনোদিনই একাত্ম্যবোধ করেননি। কিন্তু একটা ধারণা নিশ্চয় সঞ্চারিত হতে শুরু করল, যে প্রাচীন উপমহাদেশীয় দর্শন মূলত প্রাচীন এবং পূর্ব আধুনিক। বামপন্থী ধারণা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত বৈষম্যে বিভাজিত হল এই বঙ্গসমাজ। যেখানে জয়দেব-চণ্ডীদাসের কাব্যরসের আরোহণ রীতিমতো হীন রূপে দেখা হল। সব রকমের লৌকিক সংস্কৃতিকে বোঝবার চেষ্টা না করেই একটি বিদেশীয় বামপন্থী ভাবনাকে বলপূর্বক চাপিয়ে বঙ্গীয় সমাজে শিক্ষা ও মেধার একটি অদ্ভুত অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করা হল। এইখানেই আমরা একটা মজার সূত্রে উপনীত হতে পারবো, যা বর্তমান বাঙালির যৌন সুড়সুড়ির প্রতি আকর্ষণকে বুঝতে সাহায্য করবে।
‘আইডিয়াল ভদ্র বাঙালি’-র ওপরেই যেন দায়িত্ব বর্তালো বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার। এই সংস্কৃতি সবার আগে অনাবৃত যৌন ভাবাবেগকে স্তিমিত করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হল। কিন্তু তাই বলে তার উদযাপন কি তারা দমিয়ে রাখতে পারলেন?
রুশ বিপ্লবের অধিনায়ক লেনিনের বহু লেখায় নতুন সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে প্রোলেতারিয়ান সংস্কৃতিকে পড়া ও বোঝার গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়। ঋত্বিক ঘটকের ‘অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট’ লেখাটিতেও এই পড়াশোনার গুরুত্বের কথা উল্লিখিত আছে। এই বক্তব্য এখানে উত্থাপন করার কারণ হল, পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে প্রোলেতারিয়ান সংস্কৃতিকে বোঝার প্রায় কোনো চেষ্টা না করে তাকে অস্বীকার করে এবং শিল্প চেতনার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এমন একটি বিভাজনের সৃষ্টি করল যা চট করে ভরবার নয়। তার ফলে বঙ্গ সমাজে সব অর্থনৈতিক শ্রেণিতেই মানবিক কামনা বাসনার যে রসবোধের ধারণা প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, তা ক্রমে বিলুপ্ত হল। এই বিলুপ্তির ফলে যে বিশাল ফাঁক তৈরি হল, তা অচিরেই পূর্ণ করল মার্কিন পপ কালচার। কিন্তু বাঙালি জাতির বড়ো দোষ, তারা কোনো জিনিস সম্পূর্ণতার সঙ্গে না পারে গ্রহণ করতে, না পারে প্রত্যাখান করতে। এবং এই মধ্যপন্থা এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ির জন্ম দেয়।

পরিচালক কিউ-র সবচেয়ে বিতর্কিত ছবি গান্ডু, যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই কঠিন বামপন্থী ভাবাবেগ এক বিশালাকায় ‘যৌন-জুজু’-র সৃষ্টি করল। বাঙালি সমাজ সেই যে যৌনতাকে প্রত্যাখান করল, এখনও যেন কোনোভাবেই তা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বামপন্থী আমলে শুরুর দিকে অনেক মহিলাদেরই পরনে থাকত সাধারণ একরঙা পাড়ের সাদা বা ধূসর তাঁতের শাড়ি, টেনে বাঁধা তৈলাক্ত চুল, পায়ে মামুলি চামড়া বা রাবারের চটি। এই মূর্তিকেই বোধহয় ভদ্র ‘বামাশক্ত’ বাঙালি পুজো করতে আরম্ভ করলো। দ্বন্দ্বের শুরু এখানেই। পুরুষতান্ত্রিক ভদ্র বাঙালি সমাজ। আরাধ্যা দেবী কালীর ধ্যানমন্ত্রে যে মাতৃকল্পনার প্রকাশ দেখা যায়, তা বীভৎসরকম ভাবে কমনীয় ও কামাসক্ত এক নারী মূর্তির কল্পনা। যে কল্পনাকে মান্যতা দিতে বাঙালির কুণ্ঠাবোধ এই ফাটল সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়।
এবারে আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই ভদ্র কেরানিকূলের ইতিহাসে। কারণ কোথাও গিয়ে সেই রামতনু লাহিড়ীদের উত্তরসূরি যারা বামচিন্তায় নিমগ্ন হলেন, তারাই হয়ে দাঁড়ালেন ‘আইডিয়াল ভদ্র বাঙালি’। তাদের ওপরেই যেন দায়িত্ব বর্তালো বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার। এই সংস্কৃতি সবার আগে অনাবৃত যৌন ভাবাবেগকে স্তিমিত করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হল। কিন্তু তাই বলে তার উদযাপন কি তারা দমিয়ে রাখতে পারলেন? উত্তরটা বোধহয় নেতিবাচক। এখানেই আমাদের আলোচনায় গুরুত্ব পাবে সিনেমা। একদিকে যেখানে বাংলায় ‘বামপন্থী ভদ্র কালচার’ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে, সত্তর-আশির দশকে ঠিক সেই সময় হিন্দি সিনেমাতে ‘ভ্যাম্প গার্ল’-দের উদযাপন বেড়ে গেল। সেই আঁচ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ওই বাঙালির ছুৎমার্গ! সেই রামতনু লাহিড়ীরা যে যৌনতা বিযুক্ত ভদ্র বাঙালি সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন, তার আঁচ এসে পড়লো ছায়াছবির জগতেও। যদিও চল্লিশের দশকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেবীকা রানির চুম্বন দৃশ্য বীভৎস সারা ফেলেছিল সেই সময়। আবার সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্যে পাওয়া যায় নর-নারীর প্রেমের ভিতরে উগ্র যৌনতাকে স্তিমিত রেখে তাকে ছায়াছবিতে প্রকাশ করার কথা। সেই কারণেই হয়তো তিনি ‘অপুর সংসারে’ এই শালীনতার পাঠকে শিরোধার্য করে অপু ও অপর্ণার অন্তরঙ্গতাকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। তাতে মন শান্ত হয়েছিল কি মানিকবাবুর? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, ‘ঘরে বাইরে’ ছবিতে, যেখানে সন্দীপ আর বিমলার প্রেমের উষ্ণতাকে অগ্রাহ্য করতে পারল না সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা।

হইচই-এর জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ দুপুর ঠাকুরপো
শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ হওয়ার পরে যেকোনো বস্তুই পন্য এবং এক্ষেত্রে যৌনতা সহজেই ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী। সেই কারণেই বাংলার বাজারে যেখানে বাঙালি স্তিমিত কামনা বাসনা নিয়ে বাঁচতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল, সেখানেই আঘাত করল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বলশালী প্রযোজনা সংস্থাটি। দুপুর ঠাকুরপোর সঙ্গে নব বিবাহিত বৌদির খুনসুটিই হোক বা নতুন যুগের শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর উষ্ণতায় মোরা প্রেম – সমস্তটাই চরম বালখিল্যতা ও রুচিশীলতার অভাবের পরিচয় দেয়। কিন্তু সেখানেও একটা বড়ো গণ্ডগোল আছে যা নিয়ে সচারাচর খুব বেশি কথা বলা হয় না।
এ রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে নগ্ন নাচের প্রদর্শনী হয় (মূলত গ্রাম্য অঞ্চলগুলিতে) এবং সেখানে বিভিন্ন বয়সের মানুষ এসে আদিরসাত্মক আনন্দ উপভোগ করেন। বহু ক্ষেত্রে এ-ও শোনা যায় যে, বর্তমানে বাংলা সিনেমা ও সিরিজে যে যৌন প্রদর্শন দেখা যায়, তা নাকি আসলে গ্রাম্য অঞ্চলের মানুষদের জন্য বানানো। এখানেই শ্রেণির প্রতি সচেতনতার অভাব লক্ষ্যনীয়। মুঠোফোন আসার পরে আলাদা করে মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি দেবার প্রয়োজন আছে কিনা – এই প্রশ্ন সহজেই ওঠে।

অমিতাভ চক্রবর্তীর কসমিক সেক্স, যে ছবি ঘিরে তৈরি হয় নানান বিতর্ক
রবীন্দ্রনাথ বহু লেখায় ‘ডিকলনাইজেশন’-এর কথা উল্লেখ করেছেন। শান্তিনিকেতনের মূল ভিত্তিই হয়তো এই ডিকলনাইজেশনের উপর ভর করে। কিন্তু কী এই ডিকলনাইজেশন? কবি বলবার চেষ্টা করেছেন, উপমহাদেশিকদের যদি আধুনিক হতেই হয়, তাহলে তা নিজেদের মতো করেই হওয়া ভালো (অর্থাৎ নিজের দেশজ সংস্কৃতিকে পড়ে, বুঝে ও মান্যতা দিয়ে)। বিদেশীয় ধারণা বা দর্শনকে গা-জোয়ারি ভাবে চাপিয়ে দিয়ে নয়। কিন্তু সেই পাঠ সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হয়েছে। তাই বাঙালি আজ কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই সহসা অনুকরণের পথে অগ্রসর হয়েছে। বিদেশী জাতীয়তাবাদকে আত্মস্থ করার মধ্যে যে গোলমাল, বিদেশি ছায়াছবির যৌন আবেদনকে দেশীয় চলচ্চিত্রে আত্মস্থ করার গোলমালও বোধহয় একইরকম। এই অনুকরণ এবং দেশজ সংস্কৃতির বিস্মরণই বোধকরি বাংলা ছবি ও ওয়েব কন্টেন্টের এই বালখিল্য যৌন প্রকাশের জন্য দায়ী।
____
*মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়।