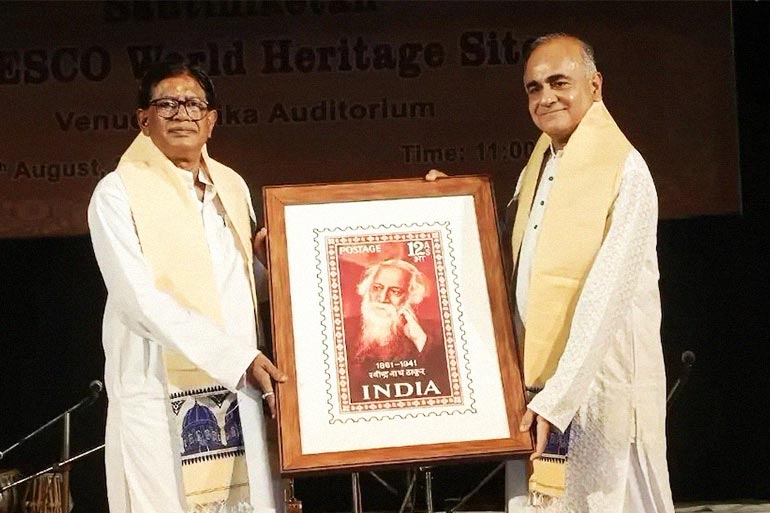কেমন আছে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সেই ‘ছোটনদী’?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী’। আঁকাবাঁকা বয়ে চলা কোপাই সত্যিই এমন এক জলধারা যার মোহে ধরা দেন স্বয়ং কবিগুরুও। বোলপুরের লালমাটিকে সাক্ষী রেখে, তরুবিরল অঞ্চলের সিঁথি হয়ে যুগ-যুগ ধরে বইছে এই নদী। কোপাই যে নদীটির উপনদী, সেই ময়ূরাক্ষী নদীতে বইছে ত্রিকুট পাহাড়ের প্রাণোচ্ছলতা। আঁকাবাঁকা চলনে বহু মানুষের জীবনযাপনের শরিক হয়ে কোপাই শান্তিনিকেতন, লাভপুর আর কঙ্কালীতলা দিয়ে নিজের গতিপথ এঁকেছে।
আঞ্চলিক নাম শাল। কিন্তু, এক অদ্ভুত প্রেমময়তার জন্যে, কোপাই নামটি বহুল ব্যবহৃত। গ্রীষ্মে শান্ত, লাজুক মেয়ের মতন এই নদী স্বল্পবাক। ‘আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে / বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে’ –কোপাইকে নিয়েই লেখা এই পদ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাস-জুড়েও কোপাই নদী বয়ে চলেছে নিরন্তর। ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’-র বাঁকটি কিন্তু কোপাইয়েরই। মনে পড়ে, বাঁশবাদি গ্রামের কন্যেদের? কোপাই ঠিক তাদের মতো। আপাত শান্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে বন্যা আসে খাতে। সব ভাসিয়ে কোপাই তখন নিজের খেয়ালে ভাঙতে থাকে চারপাশ। এই ভাঙনের সময় না এলে চেনাই সম্ভব না কোপাইকে। ১৯৬২ সালে সেই উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই সিনেমা বানিয়েছিলেন তপন সিন্হা। যে সিনেমা জুড়েও ছিল কোপাইয়ের খাত, চলন।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের, তারাশঙ্করের কোপাই আর ভালো নেই। ক্রমে শুকিয়ে আসছে সে। ফটিকস্বচ্ছ স্রোত আর নেই তার। নদীর গতিপথে বহু জায়গায় বালির চর স্থায়ী হয়েছে। আগে বর্ষাকালে কোপাইয়ের রূপ দেখে শিউরে উঠত সবাই। প্রায় বন্য পরিস্থিতি হতো আশেপাশের গ্রামগুলিতে। এখন বর্ষার সময়ে তার সেই ক্রোধ কিছু মাত্রায় স্তিমিত হয়েছে, যা একপ্রকার ভালো, কিন্তু তার কারণ নদীর সংস্কার নয়। নদীর মরে আসা।

কোপাইয়ের খাত নিয়ে একটি গবেষণায় জানা গেছে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে কয়েক বছরের মধ্যেই নদীটির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। এই বিষয়ে প্রথম সমীক্ষাটি করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫-জন গবেষক, ১৯৯১ সালে। নদীপথ ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার গতিবিধি, নদী-পাশের গাছগাছালি ও জীববৈচিত্র, জনবসতি ইত্যাদি মাপকাঠিকে কেন্দ্র করে চলেছিল গবেষণা। তারপর, ফের ২০১৬ সাল। মাঝখানে কোপাই বয়ে গেছে পঁচিশটি বছর ধরে। সেই বিশ্বভারতীরই পঞ্চাশজনের একটি টিম একই বিষয়ে গবেষণার ভার নেয়। আড়াই দশকের এপার-ওপার দুটি সমীক্ষাই লিড করেছিলেন বিশ্বভারতীর ভূগোলের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ মলয় মুখার্জী। সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল-- নদী, আশেপাশের প্রকৃতি ও আঞ্চলিক মানুষদের সমন্বয় রক্ষা করা। নদীর সংস্কার ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিকগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরাই ছিল এই গবেষণার মুখ্যতম কাজ।
আরও পড়ুন
যে নদীকে জয় করা যেত না একদিন
মলয়বাবুরা সমীক্ষায় যা পেলেন, তা একবারেই আশাপ্রদ নয়। বেশ কিছু বছর আগে পর্যন্তও কোপাই এবং আঞ্চলিক বসবাসকারীদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল, তাতে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। আজ মানুষ জীবন যাপনের জন্যে কোপাইয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। বলা ভালো, তাদেরকে নদীর সঙ্গে লেপ্টে থাকা জীবনযাপন ত্যাগ করতে একপ্রকার বাধ্য করা হয়েছে। অবহেলায় নদীর জলে দূষণ বেড়েছে। রুদ্ধ হয়েছে তার স্বাভাবিক গতিপথও। যে কোপাইকে নিয়ে সাধারণ মানুষেরা বছরের নানান সময়ে উৎসবে মেতে থাকতেন, আজ সেই প্রাণে কিছুটা স্তিমিত হয়েছে আলোর উচ্ছলতা। কোপাইয়ের ধারে অসংখ্য ইটভাটা তৈরি হওয়ার ফলে বিপুল প্রভাব পড়েছে তার জীববৈচিত্রে, ফ্লোরা ও ফনায়, পলিমাটির প্রকৃতিতে। নদীর দু'ধারেই বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ ভয়াবহরক বেড়েই চলেছে। এরই সঙ্গে সমস্যা আরও গভীর করেছে নদীর ওপরে বাঁধ, যা নদীর সংস্কারের কাজ ব্যাহত করেছে। চারিপাশের পরিবেশ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আঞ্চলিক মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, সবাইকেই সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

এতকিছুর পরেও মলয়বাবুরা অবশ্য আশাবাদী, যে কোপাই আবার পুরনো দিনের মতন নিজস্ব নৃত্যভঙ্গিমায় বইবে। সমীক্ষা ও গবেষণার ওপরে ভিত্তি করে প্রফেসর মুখার্জী ও তাঁর দল নদী-সংস্কার সংক্রান্ত কিছু পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন। সরকারি সাহায্যে তা বাস্তবায়ন হলে, এ'কথা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে কোপাই আবার ফিরে পাবে তার কলকল শব্দ, তার হারিয়ে যাওয়া তরঙ্গের গান। অঞ্চলের মানুষেরাও এমন প্রকল্পে সহযোগিতা করার জন্যে রাজি। সাহায্য তো করতে হবেই। যে নদী আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় নেই আমাদের?