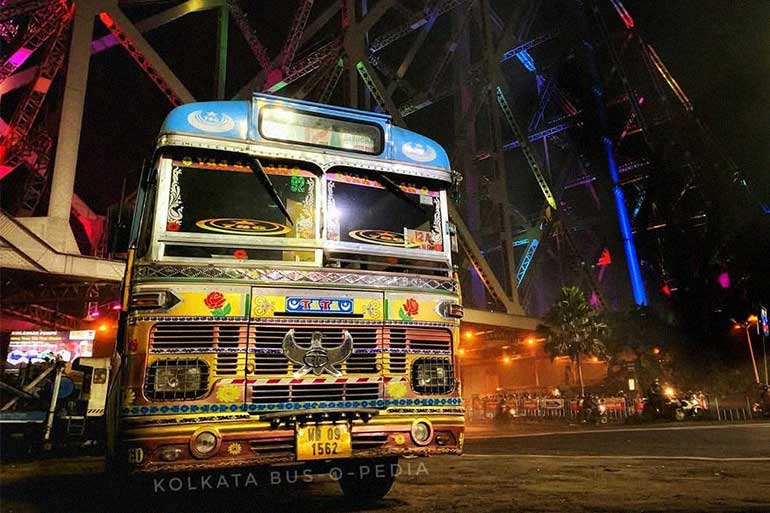মাটির তলার কলকাতা

মিসেস বারওয়েল কোথায় থাকেন জানেন? লুসিয়ার বাড়িটা কোনদিকে? নিদেন পক্ষে স্যাম খুড়োর ঠিকানাটা জানলেও চলবে। এনারা সব থাকেন কাছাকাছিই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এনারা সব সংসার পেতেছেন মাটির তলায়, কোলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রিতে। কোলকাতার ‘ওল্ড ডেড’দের বহুদিনের এই বাসভূমি এই ২৫শে অগাস্ট ২৫০ বছর পূর্ণ করল( ২৫.০৮.১৭৬৭-২৫.০৮.২০১৭)। এই ‘গ্র্যান্ড ওল্ড ডেড’দের হাল–হকিকত জানতেই গিয়েছিলেম সেদিন।
মার্কিন সাহিত্যিক আর্থার সি ক্লার্ক, তাঁর উপন্যাস ‘2001: A space Odyssey’ তে লিখেছেন- “Behind every man now alive stand thirty ghosts, for that is the ratio by which the dead outnumber the living.” কলকাতার মাদার টেরেসা সরণী সংলগ্ন, সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রিতে এলে, ‘dead outnumber the living’ এই শব্দবন্ধটির যথার্থতা মালুম হয়। কবরের বন এক্কেবারে। BACSA প্রকাশিত ‘South Park Street Cemetery, Calcutta: Register of graves and standing tombs from 1767’ এই বইটির হিসেব বলছে, এখানে প্রায় ১৬০০ সমাধি রয়েছে। কত রকমের সমাধি! চ্যাপ্টা মতন মাটির সাথে প্রায় লেপ্টে থাকা কবর, গম্বুজ আকারের কার্ন(cairn), অসাধারণ ভাস্কর্য মণ্ডিত স্যাক্রোফ্যাগি। কোনটা আবার একতলা বাড়ির মতো, চার থামওয়ালা। রোদ-জলে তার ভিতর দিব্যি আশ্রয় নেওয়া যায়। এছাড়াও আছে পিরামিডের মতো ওবেলিস্ক(Obelisk), লালমোহন বাবুর ‘বোরখা পরা ভূত’। উলিয়াম জোন্সের ওবেলিস্কটি পেল্লায়। প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। ফেলুদা বলে, ওর থেকে উঁচু সমাধি, কলকাতায় আর একটিও নেই। জন ক্লেভেরিং, এডওয়ার্ড কুক, ‘ক্ষ্যাপাটে’ স্টুয়ার্ট প্রমুখ হোমড়া-চোমড়াদের নিয়ে একই সাথে থাকেন ডিরোজিও, বোটানিস্ট রবার্ট কিড, অখ্যাত কোনো স্কুল মাস্টার, পোস্ট মাস্টার, কোম্পানির কেরানিরা তাদের বউ, তিন বছরের মেয়ে আর ছ’মাসের ছোট্ট ছেলেটি। পদমর্যাদার দাম্ভিকতা, অহংকার এসব শুধু জীবিতদের জীবনে। মৃতেরা সবাই সমান। এরা সবাই বুকে ধরে আছে একটুকরো মার্বেল ফলক। তাতে আছে কয়েক টুকরো জীবনকথা। মৃত্যু যেন বুকে আগলে রাখে একটুকরো জীবনকে। কী বৈচিত্রময় সে সমস্ত জীবন! হাসি, কান্না, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, বিচ্ছেদের রঙে রাঙানো। আছে, জীবনের নির্মম পরিহাসের গল্পও। এ সত্য অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব (William Wilson Hunter) । তাই তিনি এই সিমেট্রিকে শুধুমাত্র Graveyard বা গোরস্থান বলতে নারাজ। তিনি বলতেন-“ Calcutta underground”। মাটির তলার তিলোত্তমা।
প্রথমে বরং লুসিয়ার গল্পটাই বলা যাক। লুসিয়া এখানে আছেন প্রায় ২৪৫ বছর (Grave no. 820)। বড় সুন্দর লুসিয়ার বাড়িটি। চার থামওয়ালা বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রিয়তম রবার্ট। এই বাড়ির চাতালে বসে জেন ওয়াইয়ের দুই আত্মবিস্মৃত নরনারী যখন প্রগাঢ় চুম্বনে রত থাকেন, লুসিয়ার কি তখন হিংসে হয়? লুসিয়াও তো একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এমন দীর্ঘ মায়াময় দাম্পত্যের। লুসিয়া যখন কোলকাতায় আসেন, তখন তিনি বছর একুশের তরুণী। ইংল্যান্ডের নর্থহ্যাম্পটনের অভিজাত স্টোনহাউস বংশের মেয়ে তিনি। তাই কলকাতায় তাঁর সঙ্গীর অভাব হল না। কোনো এক সান্ধ্য পার্টিতেই, প্রথম দেখা রবার্টের সঙ্গে। রবার্ট অবশ্য লুসিয়ার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়, কিন্তু তাতে কি! সুদর্শন রবার্ট প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেলেন লুসিয়ার। লুসিয়ারও মনে ধরল রবার্টকে। তারপর বছর ঘুরতেই সাত পাকে বাঁধা পড়লেন ওরা। শুরু হল ছোট্ট সংসার। রবার্টের সমস্ত ঔদ্ধত্য বশ মানল লুসিয়ার নারীত্বের কাছে। কে বলবে, এই রবার্টই ছিলেন মহারাজা নন্দকুমার হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী! কিন্তু এই দাম্পত্যসুখ বেশদিন সইল না। মৃত্যু ছিল তাঁর শিয়রে। রোগে ভুগে একদিন তিনি রবার্টকে ছেড়ে চললেন পরপারে। তাঁর জন্য রবার্টের অশ্রু আজও ঝরে তাঁর সমাধির দেওয়ালে-
“...What needs the emblem, what the plaintive strain,
What all the arts that sculpture e’er expresse’d,
To tell the treasure that these walls contain?
Let those declare it most who knew her best.
The tender pity she would oft betray
Shall be with interest at her shrine return’d,
Connubial love, connubial tears repay,
And Lucia lov’d shall still be Lucia mourn’d…”
মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরেও লুসিয়া হারিয়ে যাননি। তাঁকে জীবন্ত করে রেখেছেন সাহিত্যিক কিপ্লিং সাহেব ( Rudyard Kipling) । তাঁকে বানিয়েছেন ‘ The city of Dreadful Night’ গল্পের নায়িকা ( দ্রষ্টব্য- The city of Dreadful Night, chapter -8 ; ‘Concerning Lucia’) ।
সিমেট্রির প্রবেশপথ দিয়ে কয়েক পা এগোলেই বাঁ দিকে যে ওবেলিস্কটির (Grave no. 794) দেখা মেলে, তার তলায় চিরনিদ্রিত বছর কুড়ির রোজ উইথাট এলমার (Rose Whitworth Aylmer)। সে জানে তাঁর প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসের কাব্য। তাঁর প্রেমিকটি যে সে লোক নয়। ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল কবি ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডর। ওদের প্রেম কাহিনীর শুরু সেই সুদূর ওয়েলসে। ল্যান্ডর তখন বছর চব্বিশের উঠতি কবি। রোজের সঙ্গে হল ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বছর দেড়েক পর পরিস্থিতির ফেরে রোজকে চলে আসতে হল কোলকাতায় তাঁর মাসি বাড়িতে। মেসো স্যার হেনরি রাসেল, কোলকাতা হাইকোর্টের নামকরা জজ। এখানে আসার বছর দুয়েকের মধ্যেই কলেরায় মারা গেলেন রোজ। রোজের মৃত্যু সংবাদে স্তব্ধ ল্যান্ডর সেদিন লিখেছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ এলেজিটি। যা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা এলেজিও বটে। ল্যান্ডরের সেই দীর্ঘশ্বাস ফুটে রইল রোজের সমাধিতে-
“ Ah! What avails the sceptred race?
Ah! What from the divine?
What every virtue every grace?
Rose Aylmer all were thine
Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep but never see.
A night of memories and of sighs
I consecrate to thee.”
ডাকসাইটে সুন্দরী মিস এলিজাবেথ স্যান্ডারসন যখন কলকাতায় পা দিলেন, তখন তিনি বছর কুড়ির তরুণী। পোশাকের দিক থেকেও তিনি আধুনিকা। সাহেবদের মেয়ে বউরা যখন মাটিতে লুটানো লম্বা ঝুলের গাউন ছেড়ে বেরোতে পারেননি, এলিজাবেথের পরনে তখন হাঁটু পর্যন্ত ঘেরওয়ালা স্কার্ট। বুড়ো থেকে ছুঁড়ো সব সাহেব তখন তাঁর প্রেমান্ধ। তাঁর প্রতি পুরুষদের এই দুর্বলতাকেই তিনি কাজে লাগাতেন নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে। একবার, তিনি তাঁর প্রতি প্রেমান্ধ এমন ষোলোজন পুরুষের প্রত্যকের কাছে গোপনে আবদার জানালেন - ওমুক দিনের ওমুক পার্টিতে তাঁর পছন্দ মত মেয়েলি পোশাক না পড়ে আসলে, তিনি তাঁদের সাথে নাচবেন না। নির্দিষ্ট পার্টিতে পৌছে, একে অপরের একই রকম পোশাক দেখে ষোলোজনই বেকুব বনে গেলেন। মিস স্যান্ডারসন অবশ্য তখন নাচতে ব্যস্ত অন্য কোনো সুদর্শনের সঙ্গে। জীবনও কিন্তু মস্করা করল এলিজাবেথের সাথে। এলিজাবেথ সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়লেন ওয়ারেন হেস্টিংসের বন্ধু রিচার্ড বারওয়েলের। তারপর রিচার্ডকে বিয়ে করে হলেন এলিজাবেথ বারওয়েল। সংসার পাতলেন খিদিরপুরে। এবারে প্রকাশ পেল স্বামী রিচার্ডের আসল রূপ। রিচার্ড ছিলেন সে সময়কার কুখ্যাত জুয়াড়ি, নেশাখোর। মাঝে মাঝেই তাঁর সন্ধান মেলে গণিকালয়ে। জুয়ার নেশায় সর্বস্ব খোয়ালেন রিচার্ড। এলিজাবেথ তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায়। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন গনোরিয়া। প্রচন্ড অর্থাভাবে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন এলিজাবেথ। এলিজাবেথের সমাধিটি খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সিমেট্রির পেল্লায় ওবেলিস্ক গুলোর অন্যতম (Grave no. 814B)।
আরও পড়ুন
অজিরো মাইলের ফলক
স্যাম খুড়োর জীবনটাই কি কম আশ্চর্যের! স্যাম খুড়োর পুরো নাম- স্যামুয়েল ওল্ডহ্যাম। সিমেট্রির বেশিরভাগ সমাধির মার্বেল ফলকেই ছোট্ট করে স্যাম খুড়োর নাম লেখা আছে- ‘S.O. fecit’। অর্থাৎ স্যাম খুড়ো ছিলেন সে সময়কার নামকরা মৃত্যুকারবারি বা undertaker। সে সময় কোলকাতায় এসে মুড়ি মুড়কির মতো মরছেন ইংরেজরা। স্যাম খুড়োরও ব্যবসা উঠছে ফুলে ফেঁপে। শহরে স্যাম খুড়োকে নিয়ে তখন ছড়ার ছড়াছড়ি- ‘ In a very few days, you are released from all cares. If the Padre’s asleep, Mr. Oldham reads prayers’. কিন্তু মৃত্যু রেহাই দেয় না, মৃত্যুকারবারিকেও। একদিন স্যাম খুড়োকেও তাঁর তৈরী কফিনে বন্দি হয়ে আসতে হয়েছিল এই সিমেট্রিতে। ওনার সমাধিটি সংরক্ষণের অভাবে নিশ্চিহ্ন। তবে, মার্বেল ফলকটি রক্ষিত আছে, সিমেট্রির দ্বার রক্ষীদের ঘরের দেওয়ালে।
এনারা তবুও সৌভাগ্যবান। ইতিহাস, সাহিত্য এদের নিয়ে কিছু শব্দ খরচ করেছে। অনেকের কপালে এটুকুও জোটেনা। যেমন ধরুন, grave no. 363। লেখা নেই এনার কোনো পরিচয়। শুধু লেখা- ‘A virtuous mother’। বা পাঁচ মাসের সেই শিশুটির সমাধি, যার একমাত্র সম্বল, তার ঠাকুমার লেখা শোকগাঁথাটি? এরাও তো জীবনের গল্প বলতে চায়। তাঁদের গল্প ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমরা সে কান্না শুনতে পাই না। সে কান্নার ভাষা বোঝে, সমাধির উপর কান পেতে থাকা ফার্ণের দল । কান্নারা শান্ত হয় ফার্ণদের কোমল সবজে আদরে। আমরা যারা মাটির উপর দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি, যাদের বুকের ভিতর যন্ত্রটা এখনও ধুকপুক করছে, এদের সাথে ওদের পার্থক্য কোথায়? ওদের শুধু জীবনের অহংকার নেই। জীবিতদের মৃত্যু নিয়ে কত না ফ্যান্টাসি! কবি লেখেন- ‘মরণ , তুঁহু মম শ্যাম সমান’। প্রেমিকার হৃদয় পেতে গলা সাধি- ‘এমন চাঁদের আলো/ মরি যদি সেও ভাল/ সে মরণ স্বরগ সমান...”। কি করলে, টেঁসে গিয়ে স্বগগেও ফূর্তি মারতে মারতে পারব, সে নিয়ে আমাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ! আমাদের যত ভাবনা পরলোককে নিয়ে। আর মৃতেরা শোনায় জীবনের গল্প!
দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামে। গাছ গাছালির মধ্যে দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ্দুর, আলো ছায়ার জাফরির চাদরে মুড়ে দিয়েছে সমাধিদের। এখানে মৃত্যুর বীভৎসতা নেই। জীবন এখানে নিরন্তর খেলা করে মৃত্যুর কোলে, ছোট্ট শিশুটির মতো। যেমন শেষ বিকেলের রোদ্দুর খেলে গাছের পাতায়।
ঋণ স্বীকার-
1.Echos from old Calcutta- H.E. Busteed
2. The Bengal Obituary – Edited by – W. Thacker & Co. ( 1851 edition)
3. South Park Street Cemetery, Calcutta: Register of graves and standing tombs from 1767, Pbulished by BACSA (British Association for Cemeteries in South Asia) , 1992 edition
4. Calcutta old and New – H.E.A. Cotton
5. কলকাতা- শ্রীপান্থ ( আনন্দ পাবলিশার্স)