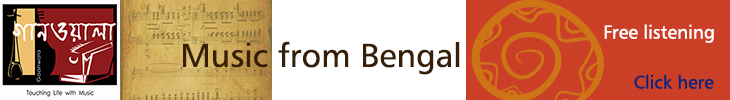গিঁট সুতোর ট্যাটিং

কলকাতার ব্যস্ত রাস্তাঘাটে আমরা যখন তখন ধরি শাটল ট্যাক্সি। কিন্তু শাটল কথাটা সব বাঙালি ব্যবহার করে কেবল এটুকু জেনেই, যে সব গাড়ি অনেককে এক সাথে নিয়ে যায় এক যায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কিন্তু এই শাটল শব্দের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে ইউরোপের তাঁতি পাড়ায়। আসলে শাটল কথাটা এসেছে মূলত ইউরোপের তাঁতি পাড়া থেকে। শাটল হল নৌকার মতো দেখতে কাঠে তৈরি একটি জিনিস, তাতে জড়ানো থাকে সুতো। আর তাঁতের এপার ওপার সুতো টেনে নিয়ে যাবার কাজ করে ওই শাটল। আমাদের বঙ্গ-মহল্লায় অবশ্য শাটল শব্দটা নেই। আমরা ওই যন্ত্রটাকে বলে থাকি মাকু। কাপড় বোনার তাঁতে প্রত্যেকটা পর্বের শুরুতে সুতো একবার ডানে আরেকবার বামে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। এইটাই তাঁত বোনার সময় আর শাটল মাকুর কাজ। সুতোকে একবার এদিক, একবার ওদিক নিয়ে চলা। এই অর্থেই গাড়ি সওয়ারি নিয়ে যায় আবার আসে, তাকে আমরা বলি শাটল। ইংরেজি তাঁতি পাড়ার শব্দ জড়িয়ে জাপটে যায় বিলেতের মতো আজকের বাঙালির জন-জীবনেও।

এবার খানিকটা সে যুগের ইউরোপের কথা। গোটা ইউরোপ জুড়ে সেই এক কালে শাটল মাকুর ব্যবহারে কি অসম্ভব সব নক্সা বোনা হত সুতোর পর সুতোর টানে। সেই শিল্প পাশ্চাত্য দেশে বা বিলিতি পাড়ায় আজ ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ হয়ে গিয়েছে। আসলে হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে পিছিয়ে নেই ইউরোপের শিল্পী সমাজ। তাঁরা দেখলেন যুগ গিয়েছে বদলে, আভিজাত্যের ফ্যাশনেও এসেছে বহু ধরনের অদল বদল। তাই আর ছোট্ট মাকুর কাজের লেসের নক্সা হয়তো জামা কাপড়ে জুড়ে নিয়ে এস্থেটিক লুক দেওয়ার চলটি দেখতে শুনতে সুন্দর হলেও সমকালীন নয়। কিন্তু শিল্প তো সময়ের সাথে পা ফেলতে জানে। বিশেষ করে ক্র্যাফট এর বিবর্তন তো সে ভাবেই হয়। তাই আজ আবার ইউরোপীয় দেশগুলি নতুন করে ভাবনা সুরু করেছে ছোটও মাকুর যাদুতে তৈরি মন ভরান গিঁট সুতোর নক্সা নিয়ে। আজ ওখানকার সেলিব্রেটেড ডিজাইনাররা সময় উপযোগী কস্টিউম জুয়েলারি তৈরিতে বেছে নিয়েছেন এমন সুতোর কাজকে। শুধু কি তাই? হাতের গ্লাভস কিম্বা পায়ের জুতো তৈরিতেও গিঁট সুতোর ট্যাটিং এর কাজকে তাঁরা প্রবল ভাবে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আধুনিক জন সমাজে এর আদর কদরও এখন দেখার মতো।
এবার বাংলা মুলুকের প্রসঙ্গ। গ্রাম-বাংলার তাঁতিদের হাতে যে মাকু ঘোরে টানা পোড়েনের ছন্দে, সেই মাকুই আবার অন্য তাল পায় নদী নালা এলাকার জেলে পাড়ায়। অদের বিরাট বিরাট বাঁশের মাকু জাল বোনার কাজে লাগে। মাছ ধরার জাল। কিন্তু আজ আমাদের কথা বলাবলির বিষয়টা খানিকটা অন্য পথের। এ বঙ্গের বা নিদেন পক্ষে কলকাতার অভিজাত মহিলা বা বাড়ির মেয়েদের নরম ছোট হাতের সাইজেরও মাকু দেখা যেতো। সেই মাকুটার কি হল? কোথায় হারালো সে? এই কলকাতার বুকে সবচেয়ে চলতি ক্র্যাফট সাপ্লাইয়ের এর দোকান একসময় ছিল শ্যামবাজারের ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোরস। এই দোকানে তিন দশক আগেও সহজেই পাওয়া যেতো জ্যোতি শাটল। ডি এম সি সুতো। গেল কোথায়? বেশির ভাগ মিশনারি স্কুলগুলোতে শেখানো হতো শাটল লেস বোনা। সে সবের চর্চা কি উঠে গেল দেশ থেকে? ফিরিয়ে কি আনা যায় না আমাদের মা কাকিমাদের হাতে বোনা লেসের কাজকে একটু অন্য ভাবনাতে? এমনটাই ভাবেন আজকের একজন লেস মেকার শিল্পী এন. নবীনা। তাঁর চোখ লেস খুঁজে বেড়ায়। নবিনা জানালেন- ‘ক্রোশে’ আজও তবু হচ্ছে। একটু আধটু সরকারি সাহায্য পাচ্ছে বলেই হয় তো। কিন্তু শাটল লেস উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের অন্দরমহলে আটকে থাকতে থাকতে সবার অলক্ষ্যে হুট করে হারিয়ে গেল বাংলা থেকে। বা আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল এই শিল্পের কথা। আবার অনেকে মনেও রেখেছেন। সেটা টের পাওয়া যায় তখনি, যখন ট্রামে বাসে লোকে আমাকে শাটল লেস বুনতে দেখে লোকে বলেন –‘কী সুন্দর, জানেন আমার মা-দিদিমারাও করতেন। ছোটবেলায় বাড়িতে দেখেছি, এ দিয়ে তৈরি ফ্রকও পড়েছি’।

কিন্তু কেন হারিয়ে গেল এমন কাজ? যন্ত্রের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক কাঠামো বদল নাকি টিকে থাকার লড়াই – কিসের জন্য এই শিল্প হারিয়ে গেল? ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে মনে করেন সুতো ও শাটল বাজারে সহজে না পাওয়াটা একটা কারণ। পাশাপাশি এই লেস বোনার বিভিন্ন টেকনিক শেখার সুযোগ নেই আজ, সেটাও কারণ হতে পারে। কারণ আজকের ইস্কুল সিলেবাসে এই শিল্প শেখানোর কোনও উপস্থিতি নেই। হাজার রকমের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস যদি নেওয়া যায় তবে তার মধ্যে এই অভিজাত শিল্পটির প্রসঙ্গেও একটু ভাবনার প্রয়োজন। বাংলার মা বোনেদের হাতে কিম্বা শিল্পীদের হাতে এই শিল্পের সমকালীন উপস্থাপনা বেড়িয়ে আসতে পারে এক লহমায়। স্বনির্ভরতা, কাজের সংস্থান এবং শিল্পকলাতেও নতুন মাধ্যম চর্চার কারিকুরি। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেল বন্ধনে বাংলাও অবদান রাখতে পারে এই শিল্পে।