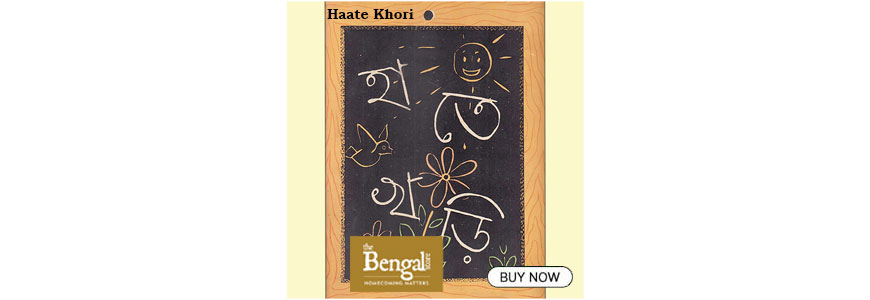ফাদার গাস্তঁ রোবের্জ : কলকাতার চলচ্চিত্র চর্চার পথিকৃৎ কেন্দ্র ‘চিত্রবাণী’র জনক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে কিছু বই পেয়েছিলাম। বইগুলো বই-বাজারে চোখে পড়ে না অথচ প্রতিটিই চলচ্চিত্র-অধ্যয়নের জেন্দ আবেস্তা, এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তার মধ্যে অন্যতম, সিনেমার কথা। যা মুখ্যত ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখা। লেখক, গাস্তঁ রোবের্জ (Gaston Roberge)। ১৯৮৪ সালে বাণীশিল্প প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় (Satyajit Ray), যে লেখার শুরু থেকে শেষ অব্দি ছিল নিজের অভিজ্ঞতার কথা, আক্ষেপের কথা, একান্ত মতামত। লিখেছিলেন, “বছর দশেক আগেও এ-ধরনের কাজ অর্থহীন বলে মনে হতে পারতো। সিনেমা সোসাইটিগুলি যে আন্দোলন করেছে তার কল্যাণে আজ আমাদের দেশের যুবসম্প্রদায়ের সিনেমা নিয়ে আগ্রহ প্রচুর বেড়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা যে শুধু ভারতবর্ষেই ঘটেছে তা নয়। এই বইয়ের ভিতরে যে টীকা যুক্ত পত্রের কী বিপুল সম্ভার না আজ সাজানো আছে! আমার যৌবনে, যখন আমি ফিল্মের কাজে নামি, তখন ইংরেজি ভাষায় ডজনখানেকের বেশি উল্লেখযোগ্য বই এ-বিষয়ে ছিল না। …রোবের্জ-এর বইতে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল এর ব্যাপকতা। কাজটা সহজ নয় …পরিচালক, প্রযোজক, সমালোচক এবং শিক্ষকদের পক্ষে পায়ের তোলা থেকে সরে যাওয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়।”
চলচ্চিত্রের এই গোলকধাঁধার ভিতর ভ্রাম্যমান গাঁস্ত রোবের্জ প্রশংসনীয় ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেকথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি সত্যজিৎ। তিনি আশা করেছিলেন বইটি ভারতীয় তরুন-তরুণীদের সিনেমার প্রতি উৎসাহী করে তুলবে। ‘সিনেমার কথা’ পড়েছি বলে শুধু নয়, এ প্রজন্মের একজন সিনেপ্রেমী হিসেবে বলতে পারি সত্যজিৎ রায়ের বিচক্ষণতা ভুল ছিল না। যখন বইটি প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসের রেফারেন্স বই হিসেবে পড়ছি, গাস্তঁ রোবের্জ-এর বিষয়ে অতশত জানা ছিল না। এমনকি জানা ছিল না তাঁর নামের আগে বসে ‘ফাদার’ শব্দটি। শুধু জানতাম তিনি একজন চলচ্চিত্রবেত্তা। পরে ধীরে ধীরে জেনেছিলাম এই ‘ফাদার’ শব্দটির ভাবার্থ তিনি আজীবন কীভাবে লালন করে গেছেন।
 সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে
সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে
ফাদার গাস্তঁ রোবের্জ সমগ্র পূর্ব ভারত তথা কলকাতার প্রাচীনতম সংযোগমাধ্যম, চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিত্রবাণী-র (Chitrabani) জনক। সিনেমা-চর্চার প্রসারের কথা ভেবে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সংযোগ-মাধ্যম গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ ছিল যন্ত্রনির্ভর তিনটি গণমাধ্যম, ফটোগ্রাফি, রেডিয়ো আর সিনেমা নিয়ে শিক্ষা, গবেষণা আর হাতে-কলমে কাজ। আস্তে আস্তে আরও নানা ক্ষেত্রে শাখা বিস্তার করেছে এই প্রতিষ্ঠান— গ্রাফিক্স নিয়ে চর্চা হয়েছে, হয়েছে লোক সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা। টেলিভিশন নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে আশির দশকে, যেখান থেকে ১৯৮৮ সালে জন্ম নিল টেলিভিশনে সম্প্রচারযোগ্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরির প্রতিষ্ঠান ইএমআরসি। সংযোগের কোনও ক্ষেত্রই অচ্ছুত ছিল না চিত্রবাণী-তে, স্বাধীনতা ছিল যে-কোনও ক্ষেত্র নিয়ে নিজের মতো কাজ করার। সত্যজিৎ রায় ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরামর্শদাতা এবং পথ দেখানোর জন্য আসতেন দীপক মজুমদার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, বা জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখরা। তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, হিরণ মিত্র, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়রাও। ছিল ঈর্ষা করার মতো এক গ্রন্থাগার। মাধ্যম আর সংযোগ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম বইপত্র খুঁজে নিয়ে আসতেন রোবের্জ, যোগ্য সঙ্গত করতেন সুনেত্রা ঘটক। ছিল অসম্ভব ভাল রেকর্ডিং স্টুডিয়ো। ছিল গ্রাফিক ডিজ়াইনের স্টুডিয়ো। আর ছিল আর্কাইভ— মূলত ফটোগ্রাফির, কিন্তু ছিল উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্রও, বিশেষ করে তথ্যচিত্র। ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এক দল মানুষ, যাঁদের রোবের্জ লালন করতেন পরিবারের কর্তার মতো। এঁদেরই কল্যাণে ১৯৯০-এর আগে এই শহরে মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে ‘চিত্রবাণী’, যা এখনও রয়ে গিয়েছে ৭৬ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড-এ। তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারা ছিল গর্বের ব্যাপার। চিত্রবাণীর আমন্ত্রণে মাসব্যাপী চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ-এর প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদও।
 মৃণাল সেনের সঙ্গে
মৃণাল সেনের সঙ্গে
‘চিত্রবাণী’ নামে বিখ্যাত একটি বইও লিখেছিলেন রোবের্জ। চল্লিশের দশকের শেষদিকে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলো প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এদেশে ভালো ও মৌলিক ছবি তৈরি করার চেষ্টার সপক্ষে এবং সিনেমার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষে একটা সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে যখন পুনায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট (পরে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট) অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মাদ্রাজে আরেকটি চলচ্চিত্রবিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ-ও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চলচ্চিত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা হয়েছিল ‘চিত্রবাণী’। রোবের্জ তখন ভারতে চলচ্চিত্র শিক্ষাদানে নিয়োজিত। সেই সময়ই তিনি অনুভব করেন যে ভারতীয় ছাত্রদের প্রয়োজনানুগ কোনো বইই বাজারে নেই। চলচ্চিত্র পড়াতে গিয়ে নিজস্ব একটি নোটস তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। সেই নোটস্-এর পনেরোটি পরিচ্ছেদ ‘মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যান’ নামে ১৯৭১-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এই ‘নোটস্’-এর আরো বিস্তৃত রূপ হিসেবে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় ‘চিত্রবাণী’। মূল ইংরেজি থেকে হিন্দিতে ভাষান্তর হওয়ার পর বাংলায় অনুদিত হয় বইটি, যার নাম ‘সিনেমার কথা’।
মাদার টেরিজ়ার (Mother Teresa) পথ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের কাজে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একুশ বছর বয়সি রোবের্জ। কলকাতায় আসা ১৯৬১-তে। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজের তরুণ ছাত্রটির সেই থেকেই নিরবচ্ছিন্ন ঠিকানা এই শহর। ভালোবেসে বাংলা ভাষাও আত্মস্থ করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “বাংলা কিভাবে শিখলেন?” তাঁর উত্তর ছিল-
“আমি যখন কলকাতায় আছি তখন বাংলা শিখবো না! আমি তো কলকাতায় অনেক দিন ধরে আছি, সেই ১৯৬১ থেকে। …প্রথম দিন থেকে আমি বাংলা শিখতে শুরু করি। আমি সিনেমা সম্পর্কে কথা বলতে অনেক দিন ধরে ঢাকা আসি। রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির আমন্ত্রণে আমি একবার গ্যেটে ইন্সটিটিউটে এসেছিলাম। তখন একজন বললো, আরো ভালো বাংলা বলা উচিত। আমি মনে করি কথাটা ঠিকই বলেছে।”

এই সময়ে আমাদের মতো কয়েকজন ছাড়া তাঁকে চেনার-জানার প্রয়োজন পড়ে না কারো। পুরোনো কলকাতার সিনেমাপ্রেমী মানুষরা ফাদার রোবের্জকে চেনেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সিনেমার প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, অভিজ্ঞ চিত্রসমালোচক ও চলচ্চিত্র-তাত্ত্বিক হিসেবে। সিনেমা-চর্চার প্রসারে শুরু করেন প্রতিষ্ঠান ‘চিত্রবাণী’, লিখেছেন চলচ্চিত্র-বিষয়ক বহু বই, ১৯৯৮-এ পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। মাদার টেরিজার স্নেহধন্য মানুষটি সেবাব্রতীও— এডস সচেতনতার প্রচারক থেকে দুঃস্থের আশ্রয়। ঋদ্ধ এই জীবন নিয়েই ফিল্মস ডিভিশন-এর প্রাক্তন অধিকর্তা কে জি দাস বানিয়েছেন তথ্যচিত্র ‘মাস্টার প্রিচার অব ফিল্ম থিয়োরি’।
‘চিত্রবাণী’-র লক্ষ্য হিসেবে লেখা হত পাঁচটি ইংরেজি শব্দ— ‘আ হিউম্যান টাচ ইন কমিউনিকেশন’। এই বাক্য ব্যবহার করে রোবের্জ বলতে চেয়েছিলেন, সংযোগ হোক মানবিক, গণসংযোগমাধ্যমের ব্যবহার হোক মানুষের কল্যাণে। বলতেন, ‘গণমাধ্যম’ থেকে যেন ‘মানুষ’-এর বহুধাবিস্তৃত পরিচিতি আর সেই সব পরিচিতির সঙ্গে মানানসই স্বর হারিয়ে না যায়। চেয়েছিলেন ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ, সামাজিক মানুষ, আন্তর্জাতিক মানুষ— সবার স্বরই মর্যাদা পাক যন্ত্রনির্ভর ‘গণমাধ্যম’-এর জগতে। এখানে মানুষ আসুক সজীব, সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী হিসেবে।
গণমাধ্যমের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সুলুক-সন্ধান জানতে আগ্রহের অন্ত ছিল না তাঁর। কিন্তু গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতির প্রধান উৎস অগণিত বক্তৃতা, প্রায় পঁয়ত্রিশটি বই আর বেশ কিছু অগ্রন্থিত লেখা। সে সবের হদিশ নিলে বোঝা যাবে, শুধু সিনেমার আলোচনাতেই নিজেকে আটকে রাখেননি রোবের্জ। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি গণমাধ্যমের বিবর্তন, বিস্তার আর বিস্ফোরণের বিভিন্ন পর্যায় খুব মন দিয়ে লক্ষ করেছেন। লেখা আর বলার ক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচিত বিষয়ের আপাত ‘বৈচিত্র’ আসলে এক অন্তর্লীন ‘ঐক্য’-কেই ধারণ করে আছে। গণমাধ্যমের ব্যাপক সংযোগক্ষমতার ভালমন্দ নিয়ে নিরলস আলোচনা জারি রেখে মানুষের কাছেই পৌঁছতে চেয়েছিলেন তিনি— নিজের মতো করে।

১৯৭০ থেকে ১৯৯৬, এই ছাব্বিশ বছরের জার্নি তৈরি হয়েছিল মূলত ‘চিত্রবাণী’ আর কিছুটা ইএমআরসি-কে ঘিরে। পরের চব্বিশ বছর এদের কোনওটির সঙ্গেই তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। ২০১৫ সালে শেষবার পা রেখেছিলেন চিত্রবাণী-তে, কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে। ২০২০-র ২৬ অগাস্ট, ৮৫ বছর বয়সে প্রয়াত হন বিদগ্ধ চলচ্চিত্রবিদ, তাত্ত্বিক তথা জেসুইট ধর্মযাজক গাস্তঁ রোবের্জ।
তথ্যঋণ:
হিরণ মিত্র, সিনেমার কথা : গাস্তঁ রোবের্জ, চিত্রবাণী আর্কাইভ, তথ্যচিত্র ‘মাস্টার প্রিচার অব ফিল্ম থিয়োরি’, চলচ্চিত্রযাত্রা : তারেক মাসুদ