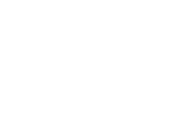‘নিম্বকাঠ’-এ গড়ে ওঠা শ্রীচৈতন্যের প্রথম দারুমূর্তি

নিমগাছের কত না উপকার, সে গল্প অবশ্য বনফুল আমাদের শুনিয়েছেন। তবে এই ঘটনা নিমগাছেরও খানিক দেবত্বপ্রাপ্তির মতো। শ্রীচৈতন্যদেব জীবিত থাকতেই তাঁর বেশকিছু মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশই ছিল নিমকাঠের। এমনকি শোনা যায় সেই সুপ্রাচীন দারুমূর্তিরা নির্মিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের স্বপ্নাদেশেই।
চৈতন্যদেবের প্রথম দারুমূর্তিটির পিছনে এক মনোরম কাহিনি প্রবহমান। বিষ্ণুপ্রিয়া ও পদাবলি-রচয়িতা বংশীবদন চৈতন্যকে না-দেখে যখন আকুল, তখন তাঁদের দু’জনকেই স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। বলেছিলেন, তাঁর জন্মস্থানেই যেন তাঁর মূর্তি নির্মিত হয়। সেই মূর্তির সেবাতেই দুঃখমোচন হবে তাঁদের-
“আমার আদেশ করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিল মোর স্তন
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্তি নির্ম্মাইয়া
সেবন করহ তার আনন্দিত হইয়া।।”
আরও পড়ুন
ভুলে যাওয়া নদী বিদ্যাধরী
এই আদেশ লাভের পর বংশীবদন অবিলম্বে মূর্তি তৈরির তোড়জোড় শুরু করেন। বংশীবদনের আরেকটি পরিচয় ‘চট্টের কুমার’ নামে। তিনি ছিলেন, চৈতন্যভক্ত মাধবদাস বা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র৷ তাঁর মূর্তি-নির্মাণকে ঘিরে জনশ্রুতি কম নেই। চৈতন্য গৃহত্যাগের সময় ফেলে গিয়েছিলেন তাঁর একজোড়া খড়ম। তাকে সামনে রেখে বিষ্ণুপ্রিয়া, মাধবাচার্য ও ঈশানচন্দ্র আনত হয়ে প্রার্থনা জানাতেন, চাঁচর-চিকুর সহ, যজ্ঞসূত্রধারী রূপে দর্শন দেওয়ার জন্যে। সেই প্রার্থনায় নাকি সাড়া দিয়েছিলেন গৌরাঙ্গদেব৷ তাঁর আজানুলম্বিত বাহু দ্বারা মাটি থেকে তোলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। আর তারই কাঙ্ক্ষিত রূপে আবির্ভূত হন। সেই রূপেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন বংশীবদনকে। আর আদেশ করেছিলেন জন্মস্থানে নিমকাঠের মূর্তিনির্মাণ করতে। বংশীবদন তখন নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দাঁইঘাটার এক বিখ্যাত শিল্পী নবীনানন্দ আচার্যকে তিনি এই মূর্তি নির্মাণের অনুরোধ করেন। এইভাবে চৈতন্যের জন্মভিটেতেই তাঁর প্রথম মূর্তিটি তৈরি হয়ে যায়। বীর হাম্বীর নাকি, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবৎকালেই এক কালো পাথরের মন্দির নির্মাণ করেন সেখানে এবং সেখানে নবীনানন্দের মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হিসেবে নবীনানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রথম মূর্তিকার।
কারো কারো মতে ১৫১২-১৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল মূর্তিটি।
তবে এই সময়পর্বে চৈতন্যদেবের অন্য বেশকিছু মূর্তির কথা শোনা যায়। আর প্রতিটি মূর্তি ঘিরেই কাহিনিমালা। যেমন সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌরাঙ্গদেব অম্বিকা কালনায় কিছুদিন কাটান। সেখানে গৌরীদাস গৌরাঙ্গদেবের আশ্রয় সর্বক্ষণ পেতে চাইলে তাঁকেও নাকি মূর্তিনির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। আবার কুলাই গ্রামের যাদব কবিরাজ মহাপ্রভুকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাপ্রভু তাকে বলেন – “এই নিম্ববৃক্ষে বিগ্রহ করহ নির্মাণ। / মনুষ্যরূপে বিশ্বকর্মা করিবে বিধান। /ছোটোবড়ো তিন ঠাকুর বানাইলা। সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা...”
নিমকাঠের সেই মূর্তি নাকি আজও রয়ে গেছে শ্রীখণ্ডে।
গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরিতে নিম কাঠ ব্যবহারের অবশ্য বিশেষ একটা অর্থ আছে। প্রথমত, সেই কাঠ সহজে পোকায় ধরে না। আর দ্বিতীয়ত নাকি গৌরাঙ্গদেবের ‘ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডল’ নিমকাঠেই সবথেকে ভালো খোলতাই হয়। তাঁর আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ কাঠামোর দেহ নাকি নিমগাছ ছাড়া অন্য কোথাও তেমন ভালো নির্মিত হতে পারে না।
মূর্তিনির্মাণের এই কাহিনিগুলি বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্যের একটি সাধারণ ব্যাপার। তবে সেসব সরিয়ে রেখেও আমরা বলতে পারি, বাংলার শিল্পতে গৌরাঙ্গদেবের ভূমিকা অপরিসীম। একে তো শূদ্র মানুষ বেঁচে থাকার নতুন দিশা পেয়েছিল, পাশাপাশি বাংলার রূপদক্ষ নামের শিল্পী গোষ্ঠীসহ আরো নানান শিল্পীজীবনেই নতুন জোয়ার এসেছিল, তা বলা বাহুল্যই। আজকের পরিবেশেও কোথাও চৈতন্যদেবের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কমেনি।
ঋণ: ‘বঙ্গশিল্পে চৈতন্যপ্রভাব’, অঞ্জন সেন।