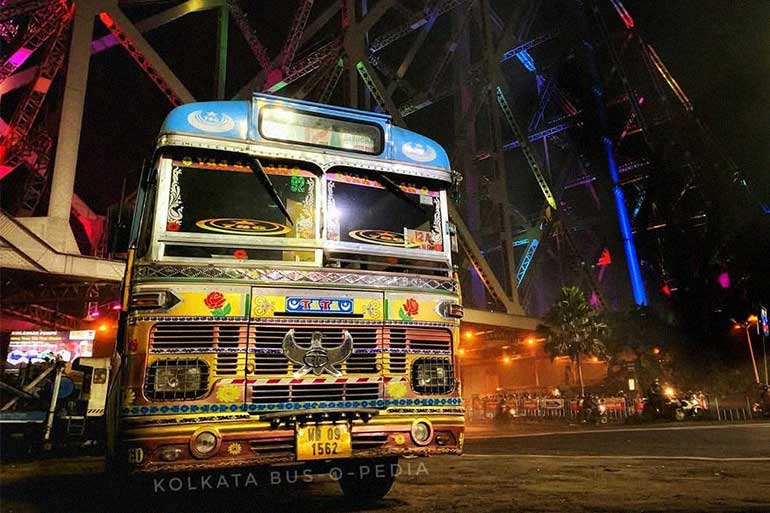কলকাতার প্রথম দোভাষীর গল্প

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকার্য সামলাচ্ছেন মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান। এমন সময় ১৬৮০ সালে গড়গোবিন্দপুরে কুঠি স্থাপন করল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর সেই থেকেই ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দেশীয় অর্থাৎ তৎকালীন প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যমণি বাঙালি বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত। সেকালের বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বসাক ও শেঠরাই ছিলেন প্রসিদ্ধ। মনে করা হয়, এঁদের সঙ্গেই ইংরেজ বণিকরা সর্বপ্রথম ব্যবসায় লিপ্ত হন।
তবে ১৬৭৯ সালের আগে কোম্পানির কোনো বাণিজ্য-জাহাজ গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করতে পারত না। তখনো বালেশ্বরই ছিল ইংরেজদের বাণিজ্য-জাহাজ নোঙর করার প্রধান বন্দর। তবে ১৬৭৯ সালে ইংরেজদের বাণিজ্য-জাহাজ “ফ্যাকন্” কলকাতার বন্দরে প্রবেশ করে। গঙ্গাবক্ষে প্রবেশকারী এটিই তাঁদের প্রথম বাণিজ্য-জাহাজ, এবং এর সাথেই বাংলায় ইংরেজদের বণিকবৃত্তির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই জাহাজের কলকাতা বন্দরে নোঙর করার সঙ্গে ছোট্ট একটি গল্পও জড়িয়ে আছে।
আরও পড়ুন
গড়িয়ার সঙ্গে জুড়ে আছে চৈতন্যদেবের স্মৃতি
কিংবদন্তি অনুসারে, জাহাজটি বর্তমান গার্ডেনরিচে নোঙর করলে জাহাজের ক্যাপ্টেন স্ট্যাফোর্ড সাহেব এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন। সেটি হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা, কারণ তিনি এদেশের কোনো ভাষাই জানতেন না – ফলে তিনি যা বলেন, দেশীয় লোকেরা বোঝে না। আবার দেশীয় লোকেরা যা বলেন, তা তিনি বুঝতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে অনেক ভেবে স্থির করলেন যে, তিনি গোবিন্দপুরের শেঠ-বসাকদের কাছে সাহায্য চাইবেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন তাঁরা কিছু হলেও ইংরাজি বুঝতে পারেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, ক্যাপ্টেন সাহেব বসাকদের কাছে একজন লোককে দিয়ে বলে পাঠালেন, যদি তাঁরা অনুগ্রহ করে একজন “দুবাস” কে জাহাজে পাঠাতে পারেন তা হলে তাঁর খুবই উপকার হয়। আসলে “দোভাষী”-কে মাদ্রাজিতে “দুবাস”বলে, তিনি সেটিই জানতেন।
এদিকে বাঙালিরা তখনো ইংরাজি ভাষা রপ্ত করে উঠতে পারেননি, অন্যদিকে মাদ্রাজিও জানতেন না তাঁরা। ফলে ইংরেজদের সাথে ইশারায় বা “ইয়েস”, “নো”...“ঠিক-ঠিক” প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমেই মনের ভাব আদান-প্রদানের কাজ চালাতে হত। ব্যবসায়ী বসাকবাবুরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই ক্যাপ্টেন যে কীসের জন্য তাঁদের কাছে লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সাহেবদের তুষ্ট করে তাঁদের অনুগ্রহভাজন হতে পারলে ব্যবসার উন্নতি আর ঠেকায় কে! তাই তাঁরা ঠিক করলেন যে কোনো উপায়ে ক্যাপ্টেনের কথা রাখতেই হবে। কিন্তু সমস্যা একটাই,“দুবাস” শব্দের অর্থ কিছুতেই তাঁদের বোধগম্য হচ্ছে না।
বসাকরা ছিলেন জাতিতে তন্তুবায়, তাই সমস্যা সমাধানে জাতভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তাঁরা এক সভার আয়োজন করলেন। তবে কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেক ভাবনাচিন্তা করেও শব্দের অর্থ বুঝে ওঠা গেল না। সবাই সবার নিজের মতো করে মত প্রকাশ করতে লাগল কিন্তু শব্দার্থের রহস্য সমাধান করা সম্ভব হল না। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সভার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন – “তোমরা শুধু শুধু গণ্ডগোল করছ। আমি বুঝতে পেরেছি ক্যাপ্টেন সাহেব কী চেয়েছেন। সাহেবরা অনেকদিন ধরে জাহাজে রয়েছেন, তাদের কাপড়-জামা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ময়লা হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের একজন ধোপার একান্ত প্রয়োজন হওয়া উচিত। তাই তো বাবুদের কাছে তারা একজন ধোপা অর্থাৎ দুবাসের জন্য অনুরোধ পাঠিয়েছেন”। বৃদ্ধের কথা শুনে সকলেই ভাবলেন সাহেব নিশ্চয়ই তাহলে একজন ধোপার খোঁজই করছেন।
বসাকবাবুদের প্রজাদের মধ্যে অনেক রজক অর্থাৎ ধোপা ছিলেন। অতঃপর তাঁদেরই একজনকে জাহাজে পাঠানোর কথা স্থির করা হল। তবে মনোনীত রজক খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। হাত জোড় করে বাবুদের বলতে লাগলেন, “বাবুমশাইরা, আমায় রক্ষা করুন, আমি গোরাসাহেবের কাছে যেতে পারব না। সেখানে গেলে কি আর ফিরে আসা যাবে! ওরা আমায় আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবে”।
তিনি বাবুদের পা জড়িয়ে অনেক কাকুতিমিনতি করলেন, তবুও বাবুরা তাঁকে ছাড়বেন না। অনেক প্রলোভন দেখিয়ে শেষমেশ তাঁকে রাজি করানো গেল। তবে বাবুদের তাঁকে এত বেশি পীড়াপীড়ি করবার পেছনে মূল কারণ ছিল অন্য। সেটি হল তাঁদের মধ্যে একমাত্র এই লোকটিই কিছু ইংরাজি শব্দ জানতেন। ফলে তাঁরা ভাবলেন, সাহেবের কথা বুঝে কাজ করতে তিনিই ভালো পারবেন।
তাঁকে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে, পেস্তাবাদাম, মিছরি, কাপড় প্রভৃতি নানান উপটোকন সঙ্গে দিয়ে, একটি পানসিতে তুলে জাহাজের দিকে রওনা করিয়ে দেওয়া হল। ক্যাপ্টেন সাহেব দূর থেকে দেখতে পেলেন যে, পানসিতে চড়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে একজন লোক তাঁর জাহাজের দিকে আসছে। তিনি বুঝলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আসছে বসাকবাবুদের কাছ থেকে। তাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জাহাজ থেকে তোপধ্বনি করতে লাগলেন। এদিকে তোপধ্বনি শুনে সেই ধোপার তো ভয়ে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। অবশেষে পানসি জাহাজের গায়ে ভিড়তে আরেকবার তোপধ্বনি হল। ক্যাপ্টেন তাঁকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে জাহাজে তুললেন।
তিনি বসাকবাবুদের পাঠানো উপটোকনগুলি সাহেবের সামনে রাখলেন। বিনিময়ে ক্যাপ্টেন সাহেবও তাঁকে নানাবিধ সামগ্রী উপহার দিলেন। এখন আর সেই ধোপাকে দেখে কে, সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে আবার তিনি পানসিতে চেপে বসলেন। পানসিতে উঠে মনে মনে ভাবলেন, “ব্যাপারখানা মন্দ নয়, কোথায় ভেবেছিলাম আস্ত গিলে ফেলবে, তা না বেশ ভালোই খাতির-যত্ন করে পয়সাকড়ি-উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা করল। তাহলে সাহেবের কাছে তো আবার আসাই যায়।” পরদিন তিনি আবার জাহাজে গেলেন, ক্যাপ্টেন এদিনও তাঁর বেশ খাতির করলেন, কিছু উপহারও দিলেন। তাঁর তো আনন্দের সীমা নেই, এরপর থেকে রোজ জাহাজে যাতায়াত করতে শুরু করলেন। কিছু ইংরাজি আগে থেকেই জানতেন, ফলে সাহেবদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলতে কোনো অসুবিধাই তাঁর হত না। অন্যদিকে সাহেবদের সংস্পর্শে এসে তিনি আরো ভালোমতো ইংরাজি শিখে নিলেন, এবং কালক্রমে এইভাবে অনেক টাকাকড়িও উপার্জন করলেন।
এতো কাহিনি শোনার পর সেই ধোপার নাম জানতে ইচ্ছে করছে তো! তিনি হলেন রতন সরকার, যিনি ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে প্রথম দোভাষীর পদ লাভ করেন। তবে কলকাতার বাবুদের বিষয়ে গবেষণারত অনেকের মতে, রতন সরকারকে বসাকবাবুরা মিস্টার স্ট্যাফোর্ডের কাছে পাঠাননি, তাঁকে পাঠিয়ে ছিলেন পোস্তার নকু ধর বা লক্ষ্মীকান্ত ধর। পরে অবশ্য এই ভুল ভাঙে। কারণ নকু ধর, রতন সরকারের অনেক পরের সময়ের লোক। রতন সরকারের নামে বর্তমানে কলকাতায় দুটি রাস্তাও রয়েছে। প্রথমটি হল জোড়াসাঁকো অঞ্চলের ‘রতন সরকার গার্ডেন’ স্ট্রিট যেটি ‘মাথা ঘষা গলি’ নামেও পরিচিত এবং দ্বিতীয়টি কলুটোলার ‘রতু সরকার লেন’।
দোভাষীর সাহায্যে ভাষা সমস্যার সমাধান তো হল, কিন্তু ইংরেজদের লক্ষ্য বাংলায় তাঁদের বাণিজ্যকে আরও বিস্তৃত করা। তাই জাহাজ থেকে এবার কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর তারপরের ইতিহাস তো কমবেশি সবারই জানা। আর এইসময় থেকেই একশ্রেণির বাঙালির মধ্যে পশ্চিমপ্রীতি জন্মাতে শুরু করে, সাহেবদের জন্য দোভাষী, ঘর-বাড়ি খোঁজা, দাস-দাসী জোগাড় করা থেকে শুরু করে পালকি, বেহারা, ঘোড়া, সহিস এমনকি দেশীয় রক্ষিতা জুটিয়ে দেওয়ার কাজ পর্যন্ত এঁরা করতেন। কোনো কোনো আধুনিক গবেষক এঁদেরকেই ‘সাহেব-ধরা বাঙালি’ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কথায় আছে, ভুল ট্রেনও অনেকসময় আমাদের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, ঘটনার অদ্ভুত সমাপতনে, একজন ধোপা থেকে রতন সরকারের ইংরেজ আমলের প্রথম দোভাষী এবং বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠার কাহিনি যেন আমাদের সেই কথাই আরো একবার মনে করিয়ে দেয়।
তথ্যসূত্র : কলিকাতা সেকালের ও একালের - হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, তিন শতকের কলকাতা - নকুল চট্টোপাধ্যায়।
ছবিসূত্র : শিল্পী - থমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল, কৃতজ্ঞতা - দিল্লি আর্ট গ্যালারি।