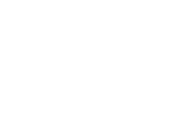চলচ্চিত্রোৎসব দু-হাজার সতের : একটি ঝাঁকিদর্শন

শিরস্ত্রাণ
তখন শীত পড়ত। ইফি হত। জানুয়ারিতে ।
আমার তখন উনিশ-কুড়ি।
গদারের রেট্রো হয়েছিল সে বছর।
পুরো ফেস্টিভাল দেখে বিরাশির ফেব্রুয়ারি মাসে দেশ পত্রিকায় পূর্ণেন্দু পত্রী একটা প্রতিবেদন লিখেছিলেন পঁয়ত্রিশ পাতার। সেখানে আমাদের দৈনন্দিন যাপনের সংগে চলচ্চিত্র উৎসবের তুলনা টেনেছিলেন বিয়েবাড়ির পঙক্তি ভোজের। তাঁর কথাতেই শুনুন, “পূর্ব হইতে জানিবার কোনো উপায় থাকে না বলিয়াই, ভ্রমে নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। চিংড়িমাছের মালাইকারিটা সম্ভবত ততোধিক উৎকৃষ্ট হইবে না অনুমান করিয়া যিনি রুইমাছের কালিয়ার প্রতি প্রেমিক চিলপুরুষের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং মাছের যৎকি়ঞ্চিৎ মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহার জিভের বিস্বাদ মুখে অতৃপ্তির আঁকচোরা কাটিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহাকে শুনিতে হয় পার্শবর্তী খাদকের কন্ঠস্বর, মহাশয়! মালাইকারিটা খাইলেন না? ইহা অমৃতবৎ! চলচ্চিত্র উৎসবের সময় আমাদের বিভ্রান্তের জালে জড়াইতে হয় অনেকটা অনুরূপভাবেই।”
উনি ফেস্টিভাল শেষে সব দেখে তারপর একমাস পরে লিখেছিলেন আর আমার সম্পাদক মহাশয় আমাকে না-দেখেই লিখতে বলেছেন। সুতরাং প্রহারের সময় কথাটা খেয়াল রাখবেন।
 রিডাউটেবল
রিডাউটেবলত্রয়োবিংশতিতম চলচ্চিত্র উৎসব : ১০-১৭ নভেম্বর ২০১৭
সময় পাল্টেছে। তথ্য বিস্ফোট ঘটে গেছে, তথাপি বলব যতক্ষণ না আপনি চর্মচক্ষুতে চলমান চিত্রমালাকে প্রত্যক্ষ করে উঠছেন, আপনার মর্মে না-প্রবেশ করছে, সেই মুহূর্ত অবধি বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। এমনকি পোলাও কষামাংসও হতাশ করিতে পারে। পরন্তু রহিয়াছে আমাদের মতো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চলচ্চিত্রচারী সিনেখাদক বা সিনে পণ্ডিতদের দল যারা আপনাকে কিছু বস্তাপচা দিগনির্দেশ দেবে এই বলে যে, ― ওটা দেখার কোনো দরকার নেই। ও-তো দেশের ছবি। তোমার পাড়ার ছবি।ডিভিডি পাওয়া যায় (পাবেন না আদৌ! বাজি!)। আরে ওটা তো ১৯৪৭ সালের মান্ধাতার আমলের সিনেমা, বহু পুরোনো। ওসব বাদ দাও এখন।এসব কানে নেবেন না। পুরোপুরি ভুল কথা। ইদানীং আইসল্যান্ড থেকে আফ্রিকা, ইওরোপ থেকে আমেরিকা সকল সিনেমাই লভ্য, দেখার সুযোগ পাবেন না কেবল দেশের ছবি, আঞ্চলিক ছবি, পুরোনো বাংলা ছবি। মাথা খুঁড়ে ফেললেও পাবেন না কেননা সেসব অচিরাৎ -নেই- হয়ে যায়, তাদের কোনো বন্টন ব্যবস্থা নেই। আমি পর্দায় সিনেমা দেখার কথা বলছি।
মনিটর-মোবাইল প্রজাতির জন্যে এ লেখা নয়। তাই নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন। কুড়িয়ে নিন, যা পাচ্ছেন, চোখ খুলে রেখে ঢুকে যান হলে, অন্তত ৩০ মিনিট দেখুন, রাবিশ হলে, নিঃশব্দে, আস্তে মাথা নীচু করে সহ-দর্শকের অসুবিধা না করে বেরিয়ে যান, চলে যান অন্য কোনো অন্ধকার হলে, আলোর খোঁজে, রত্ন সন্ধানে, অপর গৃহে। প্রত্যক্ষ করুন, খুঁজে যান ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথরের মতো। মিললেও মিলতে পারে অমূল্য রতন। কোনো পাড়াতুতো সিনে সক্রেটিসের কথা শুনে বোর হবেন না। দেখবেন নিজের হিসেবে আপনিও এক জন দেশ আবিষ্কারক। এভাবেই ভালো। তবে এসব কথা ১৮ থেকে ৩৮ পর্যন্ত ছায়াছবি-যাত্রীদের বলছি। তথাপি, পঞ্চাশোর্ধ এই অর্বাচিীনের ঝাঁকিদর্শনে ইষৎ চোখ-বুলিয়ে নিতে পারেন, যাত্রা শুরুর পূর্বে।

শুভযাত্রা
যে চলচ্চিত্রোৎসবে যত বিভাগ তত দিশাহীন হয়ে পড়ে সেটির অভিমুখ। এবারে ষোলোটি বিভাগ। সুতরাং , আসুন কথা বলা যাক।তাড়াহুড়োয় যা নজরে পড়েছে তা তুলে দিলাম। পরে অবকাশ পেলে আবার জানাব। আপনারাও জানাতে থাকুন। কেননা এটা লাইভ জার্নি।
এখানে, নীচে যেগুলো লিখছি সেগুলো অবশ্য দ্রষ্টব্য ।
আন্দ্রে ওয়াইদার আফটারইমেজ (২০১৬)। কানাল, এ জেনারেশন, ইনোসেন্ট সসার্স, অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়োমন্ডস, দাঁতো, কনডাক্টর দেখা কলকাতাকে ওয়াইদার সঙ্গে আলাপ করাতে যাওয়া ধৃষ্টতা হয়ে যাবে।
৬৯ বছরের টনি গ্যাটলিফ জন্মসূত্রে আলজেরীয়, রোমানী এবং পিয়ের নোয়া। তাঁর চলচ্চিত্র দর্শন সম্পূর্ণ অপর অভিজ্ঞতা। নাগরিক সভ্যতার , সমাজের চোখে তাঁকে ছুঁতে অসুবিধে হতে পারে এমত ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। ওঁর প্রায় সব ছবি দেখেছি, আরও অনেকই দেখেছেন। বিশেষত লাটচো দ্রম, গাডজো দিলো, ভেংগো, সুইং, করকরো, এক্সিলস, জেরোনিমো (২০১৫ সালের কলকাতা ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছিল) খ্যাত এই পরিচালকের সাম্প্রতিকতম সিনেমা ডি-জ্যাম ( ২০১৭ ) এসেছে। সুতরাং এটি তো দেখতেই হবে।গ্যাটলিফ আদ্যন্ত মিউজিকাল এবং সেই মিউজিক যা আপনার অশ্রুত, অধরা থেকে গেছে আজও।
 আফটারইমেজ
আফটারইমেজক্লেয়ার ডেনিসের টাটকা তাজা ছবি ব্রাইট সানশাইন ইন ( ২০১৭)।জুলিয়েট বিনোচেকে মনে আছে নিশ্চয়ই? গদারের হেইল মেরি ((১৯৮৫)-র অভিনেত্রী। স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক প্রত্যাখান করে যিনি ক্রিস্তফ কিয়েসলওস্কির থ্রি কালারস – ব্লু -তে; অভিনয় করেছিলেন, সেই বিনোচে আছেন এই ছবিতে।
ফ্রাঁসোয়া অগস্তো রেনে রোদাঁ-র মৃত্যু হয়েছিল ১৭ নভেম্বর ১৯১৭। রোদাঁকে কলকাতা ভুলবে কি করে! লাইন দিয়ে দেখতে গিয়েছিল তাঁর স্থাপত্য কীর্তি এই শহর। তাঁর থিংকার-এর রেপ্লিকা ( বিকৃত ও অসহ্য ) এখানে ফুটপাথে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়।তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকী স্মরণে জ্যাকুইস দোলিওন বানিয়েছেন রোদাঁ।
 ইসমায়েলস ঘোস্ট
ইসমায়েলস ঘোস্টমিশাল হাজানাভিসাসের ছবি রিডাউটেবল। বয়সে ২০ বছরের ছোটো আনা কারিনাকে নিয়ে গদার যখন লা শিনোয়াজ বানাচ্ছেন আর নায়িকার প্রেমে হাডুডুবু খাচ্ছেন (বিয়েও করেছিলেন), সেই সময়কালকে তুলে আনা হয়েছে এই ছবিতে। আরও অনেক কিছু আছে এই ছবিতে যার জন্যে কেবল গদার প্রেমিক-প্রেমিকারা নয় অন্যজনাও বসত করতে পারে কিছু সময়।
তুরস্কের মহিলা পরিচালক ইয়েসিম উস্তগুলের( ১৯৬০)ছবি ক্লিয়ার অবস্কিওর।
জাপানের বিখ্যাত পরিচালক হিরোকাজু কর-এদা (১৯৬২) ছবি দা থার্ড মার্ডার।
লিও তলস্তয়ের আনা কারেনিনা উপন্যাসকে ভিত্তি করে রাশিয়া-ওয়ান টেলিভিশনে আট পর্বে দেখানো হয়েছিল যে সিরিয়ালটিকে , সেটিকে কাহিনিচিত্ররূপে বেঁধেছেন রাশিয়ান পরিচালক কারেন শাকনাজারভ আনা কারেনিনা-ভ্রনস্কিস স্টোরি নামে।
 পাওলো ও ভিত্তোরিও তাভিয়ানি
পাওলো ও ভিত্তোরিও তাভিয়ানিডায়েরি ফর মাই মাদারস অ্যান্ড ফাদার্স(১৯৯০), ডায়েরি ফর মাই লাভার্স(১৯৮৭), ডায়েরি ফর মাই চিল্ড্রেন(১৯৮৪), অ্যাডপসন(১৯৭৫) এর মতো আত্মজীবনীমূলক ছবির নির্মাতা মার্তা মেসজারাসকে এ শহর ভালোরকম চেনে, জানেও। বিশেষ করে যে বছর আলকেজান্ডার সকুরভের টরাস ( ২০০১ )নিয়ে খুব হৈ চৈ হল কলকাতায় সে বছর রবীন্দ্রসদনে দেখানো হয়েছিল তাঁর লিটল ভিলমা –দা লাস্ট ডায়েরি (২০০০)। মার্তার অরোরা বোরিয়ালিস এসেছে।
জাপানের মহিলা পরিচালক নাওয়ামি কাওয়াসে(সেনটো) জাপানি সিনেমার এক পরিচিত নাম, বহু চলচ্চিত্রের নির্মাতা, বহু পুরস্কারে ভূষিতা। তাঁর সিনেমায় আজকের জাপানের যাপনচিত্র উঠে আসে ডকুমেন্টারি স্টাইলে, ফিচার ডকুর ভেদরেখা মিশে যায় অনায়াসে। তাই তাঁর র্যাডিয়েন্স ছবিটি দেখে নেওয়াই ভালো হবে কেননা নাওয়ামির পরের ছবি ভিশন ২০১৮ সালে রিলিজের জন্যে প্রস্তুতপ্রায়।
আলেকজান্ডার সকুরভের ফিল্ম স্কুলের (খুব অল্পকাল চালু ছিল) ছাত্র ২৬ বছর বয়সী রাশিয়ান যুবা কান্তেমির বালাগভের ছবি ক্লোজনেস সব্বাইকে চমকে দিয়ে ফিপরেস্কি জিতে নিয়েছে এ-বছর কান ফেস্টিভালে।
কান্ট্রি ফোকাস বিভাগে গ্রেট ব্রিটেনের ৫৬ বছর বয়সী মাইকেল উইন্টারবটমের একটা রেট্রো হচ্ছে ছ-টি ছবি নিয়ে। আমি ওঁর ছবি দেখেছি। কনফিডেন্স আছে লোকটার ওপর। সেই ভিত্তিতে বলছি যে ছবির নামগুলো মনে রাখুন – ওয়েলকাম টু সারাজেভো, দা ক্লেম, তৃষ্ণা, এভরিডে, অন দা রোড এবং অতি অবশ্যই দা রোড টু গুয়ানতানামো। এই রেট্রোটা নিয়ম করে প্রতিদিন দেখতে হবে।
 ব্রাইট সানশাইন ইন
ব্রাইট সানশাইন ইনতাভিয়ানি ব্রাদার্সের রেইনবো – এ প্রাইভেট অ্যাফেয়ার একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য চলচ্চিত্র। এ শহর এই দুই ভাইকে চেনে বহুকাল থেকেই --নাইট অফ সান লরেঞ্জো, ক্যাওস, গুড মর্নিং ব্যাবিলন বা তার আগে থেকেই। এমনকি এই সেদিন জেলবন্দীদের নিয়ে সিজার মাস্ট ডাই সিনেমাটাও কলকাতা দেখেছে ভিড় করে।
সমসাময়িক মরক্কোর চলচ্চিত্র নিয়ে একটা বিভাগ করা হয়েছে। দু একটা দেখে রাখুন। তবে যদি দেখতেই হয় দেখুন সেলমা বরখার ছবি দা ফিফ্থ স্ট্রিং (২০১১), আহ্ লারাব আলুই লামহারি-র তৈরি আনদ্রোমা ... ব্লাড অ্যান্ড কোল। মরোক্কো বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ফরাসি-মরোক্কান পরিচালক নাবিল আওয়ুচ-এর ছবি রাজিয়া –র নামোল্লেখ করা দরকার।
এবার রেট্র হচ্ছে থাইল্যান্ডের পরিচালক পেনেক রতনারুয়াং-এর ছবি নিয়ে। আংকল বুম ... খ্যাত আপিচাটপং ইরাসিথাকুল(১৯৭০) কিংবা ইসিট সাসানেতিয়াং (১৯৬৩) এর হাত ধরে থাই সিনেমায় যে নবতরঙ্গের জন্ম তাতে লাস্ট লাইফ ইন দ্য ইউনিভার্সের অবদান অনেকটা। সুতরাং এই রেট্রটা তো তুলে নিতে হবেই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, রেট্রোসপেক্টিভ ছাড়া যাবে না। তাই তালিকাবন্দি করুন এই নামগুলো ―সামুই সং (২০১৭), ফান বার কারাওকে (১৯৯৭), ট্রানসিসটার লাভ স্টোরি (২০০১), প্লয় (২০০৭), নিম্ফ(২০০৯), সিক্সটিনাইন (১৯৯৯)।
 রিডাউটেবল
রিডাউটেবলফেস্টিভাল কর্তৃপক্ষের অনেক দায় থাকে।তাই অনেক বিভাগ।শতবার্ষিকী শ্রদ্ধা জানাতে ঢুকেছে ― নবেন্দু ঘোষের তৃষাগ্নি ( ১৯৮৮), রাজেন তরফদারের গঙ্গা ( ১৯৬০ ) জোলতান ফাবরি-র মেরি-গো-রাউন্ড ( ১৯৫৫)। নবেন্দু ঘোষের মেয়ে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব রত্নত্তমা দাশগুপ্তা বানিয়েছেন অ্যান্ড দে মেড ক্লাসিকস । বিমল রায় ও নবেন্দু ঘোষের সম্পর্ক ও আরও কিছু নিয়ে। সম্প্রতি প্রয়াত অভিনেতা ওম পুরীকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সদগতি ও রামানন্দ সেনগুপ্তকে হেডমাস্টার ( ১৯৫৮) ছায়াছবি প্রদর্শন করে।
স্মরণ করা হচ্ছে দেবকী কুমার বসুকেও তাঁর তৈরি ছবি কবি (১৯৪৯) প্রদর্শনের মাধ্যমে।