ফজলুল হক, হারিয়ে যাওয়া এক কৃষকদরদি নেতা
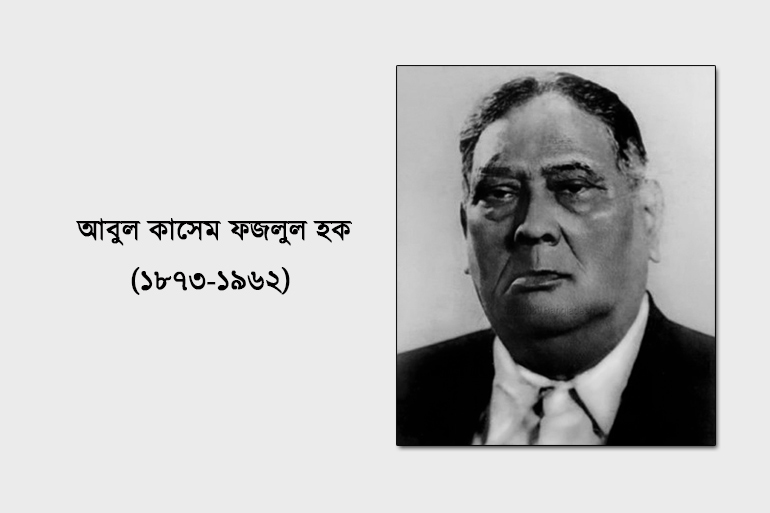
আবুল কাসেম ফজলুল হক বঙ্গ রাজনীতিতে প্রথম নেতা যিনি জমিদারি ব্যবস্থার অবসান চেয়ে হিন্দু-মুসলিম কৃষককে এক সুতোয়, অন্তত কিছুদিনের জন্য বাঁধতে পেরেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন। ১৯৩৬-এ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লখনউ অধিবেশনের মণ্ডপেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা ভারত কিষান সভার প্রথম সম্মেলন। আর তার ঠিক তি মাস বাদে ঢাকায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টির চতুর্থ সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকেই প্রথম দাবি ওঠে, জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের। বলা হয় জমিদারি তুলে দিয়ে রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো জনকল্যাণে ব্যয় করা হোক। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে কিন্তু ভবিষ্যতে এপার, ওপার, কোনও পারের বাঙালিই সে ভাবে মনে রাখেনি।
আজ যখন সাম্প্রদায়িক বিভাজনপন্থীরা দম্ভের সঙ্গে ক্ষমতায়, সেকুলারইজমের কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে,তখন ফজলুল হককে মনে করাটা বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম এবং টানা সাত বছরের বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না), যিনি ভূমি সংস্কারের দাবিকে ভোটের ইস্যু করেছিলেন, আজ ২৩ ডিসেম্বর, কৃষক দিবস উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে কিছু কথা এই লেখার বিষয়।
 তেভাগা আন্দোলনের সময়কার কৃষকদের চিত্র
তেভাগা আন্দোলনের সময়কার কৃষকদের চিত্র
ফজলুল হক মুসলিম লিগের নেতা ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসেরও নেতা ছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না সুচতুর ভাবে তাঁকে দিয়েই পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও, কৃষক প্রজা পার্টি নামে গরিব চাষিদের নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দল গড়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের বাইরে এক তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অবিভক্ত বাংলায় আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন ফজলুল হক।
আজ যখন সাম্প্রদায়িক বিভাজনপন্থীরা দম্ভের সঙ্গে ক্ষমতায়, সেকুলারইজমের কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে,তখন ফজলুল হককে মনে করাটা বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম এবং টানা সাত বছরের বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না), যিনি ভূমি সংস্কারের দাবিকে ভোটের ইস্যু করেছিলেন।
১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি তার অত্যন্ত আধুনিক কৃষকদরদি ম্যানিফেস্টো নিয়ে লড়াইয়ে নামে। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল, কোনও দল একক ভাবে সরকার গড়ার জায়গায় নেই। মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৪টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়। মুসলিম লিগ ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৪০, মুসলিম স্বতন্ত্র ৪২, হিন্দু স্বতন্ত্র ৩৭, ইউরোপীয় গোষ্ঠী ২৫, অ্যাঙ্গলোইন্ডিয়ান ৪, ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টান ২, হিন্দু মহাসভা ৩, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ২, বাকিটা অন্যান্য। পরে কিছু দল বদল হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যায় কিছু বদল (তখন নিয়মিত দল বদল এবং টাকার খেলার কথা প্রায়ই খবরের কাগজে প্রকাশিত হত। বিধানসভাতেও আলোচিত হত) হয়। কংগ্রেস বাংলায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও সারা ভারতের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ফল ছিল বেশ ভালো। ১১৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস জয়ী হয় ৭১৬টি আসনে। কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম লিগ প্রার্থী জয়ী হন ২৬ জন। মুসলিম লিগের টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়ী হন ১০৯ জন। যেটা লক্ষ্মণীয়, সেটা হল, কংগ্রেস এবং ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দলের ৯০ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন আন্দোলন করে জেল ফেরত। মুসলিম লিগের তেমন প্রার্থী ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুসলিম লিগের মুসলিম প্রার্থীদের বাঙালি মুসলিম ভোটারদের একটা বড় অংশ সেই ভোটে ভোট দেননি। তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক দাবির সমর্থনে মূলত কৃষক প্রজা পার্টিকে। মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত বহু আসনে মুসলিম লিগকে হারিয়ে দেয় কৃষক প্রজাদলের মুসলিম প্রার্থীরা।
 লাহোর প্রস্তাবের কার্যকরী কমিটিতে ফজলুল হক
লাহোর প্রস্তাবের কার্যকরী কমিটিতে ফজলুল হক
একটু পেছনের কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ১৯৩৫ সালের আইনসভার সংস্কারকে, অর্থাৎ ১৯৩৭-এ যে আইনে ভোট হয়েছিল, তাকে জওহরলাল বললেন, ‘দাসত্বের সনদ’। তবে অনেক টানাপোড়েন, বাকবিতণ্ডা, আলোচনা, বিতর্কের পর নির্বাচনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। কারণ হিসেবে নেহরু বললেন, নির্বাচনে যোগ দিলে কংগ্রেসের বাণী লক্ষ লক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এমনকী যাদের ভোট নেই, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগের একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা নিয়ে কংগ্রেসের নানা মত থেকেই যায়। সেই নির্বাচনে কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে কৃষিঋণ মকুব, কৃষি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাব থাকলেও জমিদারি উচ্ছেদের কথা ছিল না। ভোট পরিচালনার দায়িত্বে শরৎচন্দ্র বসু, প্রদেশ সভাপতি তখন বিধান রায়। নির্বাচনী ইস্তেহারে কংগ্রেস বলল, আত্মত্যাগ এবং সেবার মাধ্যমে যাঁরা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন কেবলমাত্র তাদেরই যেন জনগণ নির্বাচিত করেন। অন্য দিকে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইস্তেহারে চোদ্দ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হল। বলা হল ক্ষমতায় এলে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, মহাজনি আইন প্রণয়ন, সালিশি বোর্ড গঠন, সেচের স্বার্থে হাজামজা নদী সংস্কার, প্রতি থানা এলাকায় হাসপাতাল, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি।মুসলিম লিগের কর্মসূচিতেও জমিদারি উচ্ছেদের কথা বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলি লিগের কর্মসূচিতে তেমন কোনও প্রগতিশীল বক্তব্যই ছিল না।
ভোট হল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে। মোট ভোটার ৬৬, ৯৫, ৪৮৩ জন। মোট আসন ২৫০। গ্রামীণ আসন ১৭৭। তার ভিতর মুসলমান গ্রামীণ আসন ১১১। হিন্দু ও তফশিলি জাতি নিয়ে গঠিত গ্রামীণ আসন ছিল ৬৬টি। মোট গ্রামীণ ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ। যার ৯৯ ভাগই কৃষক। বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনীতি এই নির্বাচনে ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। এই নির্বাচনে পটুয়াখালি হয়ে ওঠে কৃষক প্রজা দলের ফজলুল হক এবং মুসলিম লিগের স্যার নাজিমুদ্দিনের মহারণক্ষেত্র, সম্মুখসমর। নাজিমুদ্দিনের পক্ষে প্রচারে নামলেন নবাব, নাইট উপাধিপ্রাপ্ত ইংরেজের প্রিয় পাত্ররা, সঙ্গে সরকারি প্রভাব এবং টাকার বন্যা। অন্য দিকে প্রায় অর্থহীন, খেতাবহীন ফজলুল হক। ফজলুল হকের ছিল একটাই কথা, জমিদারি উচ্ছেদ আর ডাল ভাত মোটা কাপড়। অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী স্কুল কলেজের পড়া ছেড়ে এখান থেকে ওখান থেকে টাকা জোগার করে পটুয়াখালি চলে এসেছিল ফজলুল হকের সমর্থনে প্রচার করতে। অন্য দিকে ঢাকার নবাব, বাংলার গভর্নর, ফুরফুরার পীর, শত শত মৌলানা, মৌলবি নাজিমুদ্দিনের প্রচারে এসেছিলেন। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল, নাজিমুদ্দিনের দ্বিগুণ ভোট পেয়ে জয়ী ফজলুল হক। আর সামগ্রিক ভাবে এই নির্বাচনে মোট মুসলিম ভোটের মাত্র ৪.৬ শতাংশ ভোট পায় মুসলিম লিগ।
 রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেরে বাংলা
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেরে বাংলা
কংগ্রেসের যে নীতি ছিল সেই সময়ে তাতে একক গরিষ্ঠতা ছাড়া সরকার গড়া সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তা হল না। কোন দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে বিরোধে। বৃহত্তর রাজনীতির কথা ভেবে কংগ্রেস চাইছিল রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে। কৃষক প্রজাদলের দাবি ছিল অগ্রাধিকার দেওয়া হোক, প্রজাসত্ব আইনের সংশোধন, খাতকদের রক্ষার জন্য মহাজনি আইনের প্রণয়ন, কৃষিঋণ মকুব ইত্যাদি কর্মসূচিকে। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত আলোচনা ভেঙে যায়। ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন পেলেন না। পেলে বাংলার রাজনীতি হয়তো অন্য খাতে বইতো।
কৃষক প্রজা দল বাধ্য হয়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করল। মুসলিম লিগের রাজনীতি যখন বাংলার মুসলিম ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন ফজলুল হককে এই ভাবে মুসলিম লিগের কোলে ঠেলে দিয়ে, মুসলিম লিগের সঙ্গে সরকার গড়তে দিয়ে, কংগ্রেস যেটা করল, তা হল, মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে একটা মান্যতা দিয়ে দিল। ফজলুল হকের হয়তো একটা বাধ্যবাধকতা ছিল গরিব কৃষকদের কাছে। কিন্তু মুসলিম লিগকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যে তাঁর কোনও প্রগতিশীল কর্মসূচিই রূপায়ণ করতে পারবেন না, এটা বুঝেও হয়তো তাঁর অন্য পথ ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস বাংলায় মুসলিম লিগকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত, তাহলে কি আমরা ১৯৪৬-এর দাঙ্গা এড়াতে পারতাম? ইতিহাসে যদির কোনও স্থান নেই। কিন্তু এসব প্রশ্ন থেকেই যায়।
ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন পেলেন না। পেলে বাংলার রাজনীতি হয়তো অন্য খাতে বইতো।
 সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন
সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন
বাংলার পরিবেশ কী পরিমাণ সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিল পরবর্তী সময়ে, কতটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল বাংলার আকাশ তা বুঝতে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর আজাদহিন্দ বাহিনীর বন্দি সেনাদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় একটি বিশাল ছাত্র জমায়েত হয়। সেই জমায়েতে গুলি চলে। নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র। রামেশ্বরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে। তারপরের দিন এক অভূতপূর্ব হরতাল এবং সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। সেই ধর্মঘটে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাকে এক সঙ্গে দেখা যায় বিক্ষোভ মিছিলে। এই আন্দোলনের পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বসুমতী পত্রিকায় লিখলেন ‘চিহ্ন’ উপন্যাস। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখলেন ‘শহিদ রামেশ্বর’ নামে ২১ পংক্তির একটি কবিতা, যার প্রথম লাইন ছিল, ‘হে অশ্বারোহী! বাঁধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ঢাক শোনো’। তার আট মাস বাদে ঐতিহাসিক ডক-তার ধর্মঘট। আর তার মাত্র কয়েক দিন পরে হল ১৯৪৬ এর ১৬ অগস্টের দাঙ্গা। যে দাঙ্গায় ৫ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। কী করে ওই উত্তাল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিবেশ ভেঙে এই দাঙ্গা হল? উত্তর মেলে না। উপর থেকে যে রাজনৈতিক ঐক্যের ছবিটা দেখা যাচ্ছিল, সেটা যে কত ভঙ্গুর ছিল তা প্রমাণ হয়ে গেল।
ফজলুল হকের সাফল্য এবং ব্যর্থতা এখানেই যে তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির প্রথম পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান নয়, বাঙালিই তার প্রথম পরিচয়। মুসলিম লিগের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ভয়ংকর অশান্ত সময়ে এই রাজনীতির চর্চা করেছিলেন। কিছুটা এগিয়েও ছিলেন। হেরেও গিয়েছিলেন অবশেষে। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কথাটা বলে গিয়েছেন এই কৃষকদরদি নেতা।
____
মতামত লেখকের নিজস্ব































