ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম বিদ্রোহের গল্প
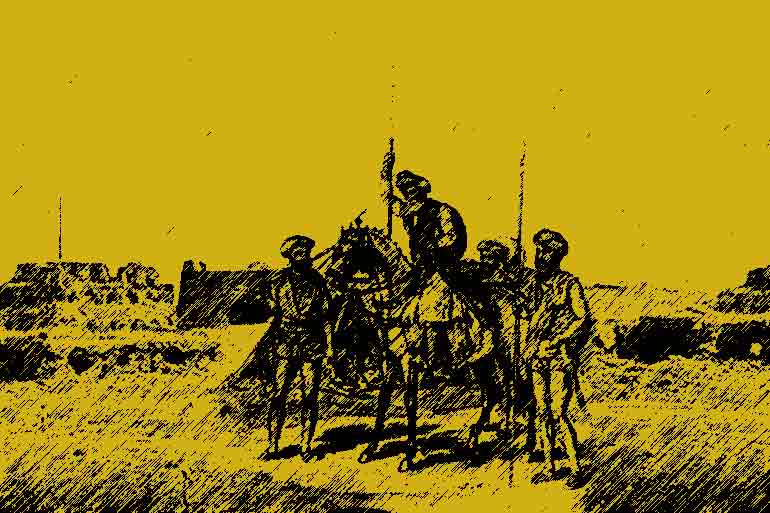
পলাশীর আমবাগানে বাংলার শেষ স্বাধীন নবার সিরাজউদদৌলাকে হারিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মুর্শিদাবাদের দরবারে পুতুল নবাব বসিয়ে নির্বিচারে লুঠপাঠ করে চলেছে ইংরেজ কোম্পানি। বাণিজ্য আর ডাকাতি যে এইভাবে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে, সেটা এদেশের মানুষ আগে কখনও দেখেনি। গ্রামীন বাংলার জমিদার এবং ভূস্বামীদের থেকে যে খাজনা নেওয়া হত, কোম্পানি তা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে খাজনা দিতে দিতে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল। ওই সময়ে হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম ফকিররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন। মাঝেমাঝে বিশ্রামের দরকার হলে ফকিরদের ছিল খানকাহ আর সন্ন্যাসীদের ছিল আখরা। গ্রামেগঞ্জে কৃষক, জমিদার আর ভূস্বামীদের থেকে ভিক্ষা করেই বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করতেন তাঁরা। গ্রামীন মানুষরাও খুশি মনে তাঁদের ভিক্ষা দিতেন। সন্ন্যাসী আর ফকিররাও সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করতেন গ্রামবাসীদের। সাম্প্রদায়িক বিভাজন বা হানাহানি তখনও দেখা দেয়নি। ইংরেজ শাসনের আগে শস্যশ্যামলা বাংলায় এভাবেই গ্রামীন জীবন নিশ্চিন্তে বয়ে চলত।
কিন্তু গোল বাঁধল কোম্পানির আমলে। ইংরেজ বণিকরা এদেশের ধর্মবিশ্বাস একেবারেরই বুঝতেন না। সন্ন্যাসী আর ফকিররা নিজের ইচ্ছে মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতেন, তাতে বাধা দিতে থাকে নতুন সরকার। এদেরকে দস্যু-ডাকাত বলে ঘোষণা করা হয় এবং ভবঘুরে এইসব সাধুসন্তদের ভিক্ষা দেওয়াকে বেআইনি করে দেওয়া হয়। ফকির-সন্ন্যাসীদের জীবনাযাপনে এইভাবে আঘাত নেমে আসলে তাঁরাও প্রতিরোধের পথ বেছে নেন। বনে জঙ্গলে চলতে হত বলে হিংস্র পশু আর চোর-ডাকাতের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব সময়েই তাঁরা দল বেঁধে যাতায়াত করতেন এবং তাঁদের কাছে অস্ত্র থাকত। সেইসব তলোয়ার, বর্শা, বল্লম, বন্দুক, ছোটো কামান নিয়ে দলে দলে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন কোম্পানির কুঠি, কোম্পানির অনুগত জমিদারদের কাচারি আর অত্যাচারী কর্মীদের বাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন গ্রাম বাংলার কৃষকরাও। একে তো এইসব মরমিয়া সাধু-সন্তদের প্রতি চাষিদের যথেষ্ট ভক্তি ছিল এবং এঁদের ওপর ইংরেজ সরকার আঘাত করলে সেটাকে ধর্মের ওপর আঘাত হিসেবেই চাষিরা নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে কোম্পানি এবং অত্যাচারী জমিদারদের শোষণে চাষিরা প্রচণ্ড ফুঁসছিলেন।
বর্ধমান, ঢাকা, রংপুরের মতো কয়েকটি জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সন্ন্যাসী, ফকির আর কৃষকদের যৌথ বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৬০ সাল নাগাদ, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তিন বছরের মধ্যেই। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এটিই ছিল বাংলায় প্রথম বিদ্রোহ। গেরিলা পদ্ধতিতে শাসক আর তার সহচরদের ঘাঁটিতে আক্রমণ নেমে আসত যখন তখন। লুঠ হতে থাকত একের পর এক কুঠি। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। পাঁচ-ছয় হাজার লোকজন নিয়ে বিদ্রোহীরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। চরিত্রগতভাবে এই বিদ্রোহ ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক। ১৭৬৯ সালে বিদ্রোহীদের দমন করতে ক্যাপ্টেন ম্যাকেনজির নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয় সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এক নৃশংস যুদ্ধে সেই দলের লেফটেনেন্ট কিথের মৃত্যু হয়। ১৭৭০-৭১ সালে দিনাজপুরে ফকিরদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধে কোম্পানির সৈন্যরা হেরে পালিয়ে যায়। ১৭৭২ সালে মোটামুটি ২ হাজার লোক নিয়ে বিদ্রোহী ফকির মজনু শাহ রাজশাহী আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধে মারা যান ক্যাপ্টেন টমাস। পরের বছরগুলোতে মজনু শাহ হয়ে উঠেছিলেন কোম্পানির ত্রাস।
১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান মজনু শাহ। তাঁর অবর্তমানে ফকির বিদ্রোহের নেতৃত্ব চলে যায় মুসা শাহ, চেরাগ আলি, সোবহান শাহ, মাদার বকস, করিম শাহের হাতে। এদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন ভবানী পাঠক। আর ছিলেন রানি লক্ষ্মীপ্রিয়া, দেবী চৌধুরানীর মতো মেয়েরা। কৃষক বিদ্রোহের বড়ো নেতা ছিলেন নুরুলউদ্দিন। মজনু শাহ বাঙালি ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। কিন্তু বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীর বিদ্রোহকে তিনি সবথেকে বেশি সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। মজনু শাহের মৃত্যু হলে দক্ষ সংগঠকের অভাবে বিদ্রোহ অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। আরও বেশ কিছু কারণের জন্য প্রায় চল্লিশ বছর একটানা লড়াইয়ের পর ১৮০০ সালের পর থেকে বিদ্রোহে ভাটা দেখা দিল। ছোটো ছোটো আঞ্চলিক লড়াইতে তারপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এই বিরাট আন্দোলন।































