অধ্যাপনা থেকে পরিচালনা – অন্তরঙ্গ আড্ডায় মধুজা মুখোপাধ্যায়
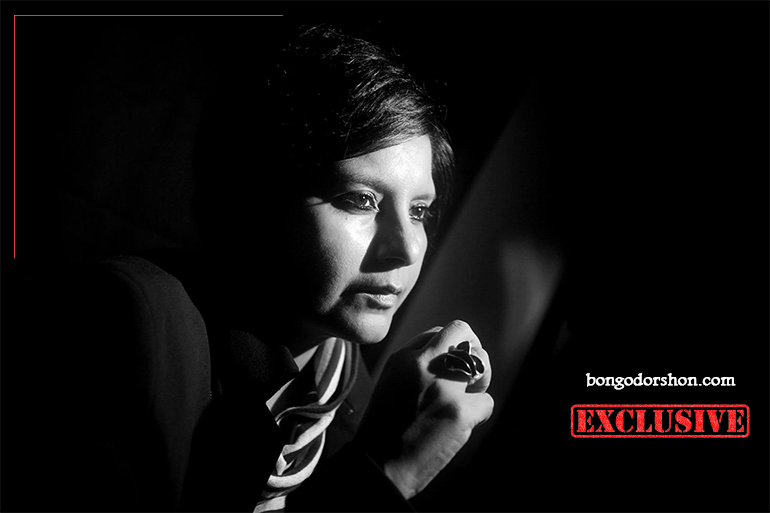
বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে তাঁর ছবি ‘ডিপ-সিক্স’, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন : ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস’ বিভাগে প্রদর্শিত হত এই ছবি। তিনি বহুমুখী প্রভিভা। চলচ্চিত্র বিষয়ের একজন গবেষক, অধ্যাপক। এ বিষয়ে একাধিক বই প্রকাশ করেছেন। তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। ‘কার্নিভাল’ নামে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল ২০১২ সালে। চিত্রনাট্যকার হিসেবেও সুনাম রয়েছে তাঁর। এখন শিক্ষকতা করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফিল্ম স্টাডিজ’ বিভাগে। যুক্ত রয়েছেন উইমেন্স স্টাডিজের সঙ্গে। সেতার বাজাতে পারেন এবং ফাইন আর্টস-এও তালিম রয়েছে। ‘সাইলেন্ট ফর্মস: রিভিজিটিং সাইলেন্ট সিনেমা অব ইন্ডিয়া’ এই শিরোনামে মিডিয়া ইনস্টলেশন উপস্থাপনা করেছেন স্টুডিয়ো ২১-এ। প্রদর্শনীতে জুড়ে ছিল তাঁর সাইট-স্পেসিফিক ইনস্টলেশন। ১৯১৩ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত নির্বাক চলচ্চিত্র নিয়ে যে বহুমুখী কাজকর্ম হয়েছে তারই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে শিল্পী হিসেবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন দৃশ্য-উপস্থাপনা। এই শিল্পরূপ প্রচলিত রীতির চিত্র-ভাস্কর্যের থেকে আলাদা। প্রচলিত ধারার বাইরে আর্ট ইনস্টলেশন – গ্রাফিক নভেল নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ করে চলেছেন নিয়মিত। বঙ্গদর্শন-এর ‘আড্ডামহল’-এ আজকের অতিথি মধুজা মুখোপাধ্যায়।
শুরুতেই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই ‘ডিপ সিক্স’-এর জন্য। সিনেমা বানাবেন, এই ইচ্ছের শুরুটা কবে হয়েছিল, কীভাবে?
মধুজাঃ সিনেমা বানাবো, এই ভাবনাটা ঠিক কবে থেকে মনে এসেছিল এটা বলা মুশকিল। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, যে সিনেমা নিয়ে পড়ে বা সাহিত্য নিয়ে পড়ে, কোনও না কোনও সময় তার মনে হয়ই যে সিনেমা বানাবো, তা সে ছোটো হোক অথবা বড়ো, যে জঁরারই হোক না কেন। আমি ফিল্ম মেকিং-এর সঙ্গে নব্বইয়ের শেষের দিকে স্টুডেন্ট থাকার সময় থেকেই সহযোগী হিসেবে, কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে বা আর্ট ডিরেকশনে বহু বছর ধরেই কাজ করছি। সুতরাং, অভিজ্ঞতাও আছে, মাঝেমধ্যে খামখেয়ালে চিত্রনাট্য তৈরি করা সেসবও আছে। অনুপ সিং-এর প্রথম ছবি ‘একটি নদীর নাম’ (২০০২) ছবিতে আমি ওর সহযোগী এবং কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবেও কাজ করি এবং সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সপোজার ছিল। তারপর ২০০২-২০০৩ থেকে অনুপ আমি স্ক্রিপ্টিং-এর বেশ কিছু কাজ করি।
সিনেমার ব্যাকরণ জেনে অথবা না জেনে, ‘সিনেমা ভেরিতে’ বা স্বতঃস্ফূর্ত সিনেমা এখন অনেকেই বানাচ্ছেন—ছক ভেঙে এক্সপেরিমেন্ট করার প্রবণতা বাড়ছে। ইন্টারনেট, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে দর্শকের কাছে সেসব ছবি পৌঁছেও যাচ্ছে। ভালো বা খারাপ, এসব না ভেবেই সিনেমা দেখার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম - চলচ্চিত্র মাধ্যমের এই বিবর্তন, নতুন এই ভাষাগুলো নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী? বিষয়গুলোকে কীভাবে দেখছেন?
মধুজাঃ আমি খুবই আশাবাদী। যেমন ধরো লিটিল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, প্রিন্টিং-প্রেসের বিস্তার ঘটেছে, এগুলোর বহু সংখ্যক পাঠক রয়েছে, লেখক রয়েছে। এই মুহূর্তে ডিজিটাল টেকনোলজির সহজলভ্যতার ফলে অনেক ছোটো ইন্ডাস্ট্রিস তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মানভূম, রাজবংশী, সাঁওতালি ছবির নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রি আছে। প্রচুর শর্ট ফিল্ম, তথ্যচিত্র হচ্ছে। কোনও সিনেমা যদি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছোয় তাহলে তার একটা আলাদা মান তৈরি হচ্ছে, তার একটা নেটওয়ার্কও তৈরি হচ্ছে। একটা জিনিস ঘটছে যে প্রচুর সিনেমা বানানো হচ্ছে, দর্শকও প্রচুর ছবি দেখছে কিন্তু ভুলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। প্রচারের জন্য একটা সিনেমা বানানোর আগে-পরে অনেক টাকা লাগে। ডিজিটাল মাধ্যম যেমন ছবি তৈরির বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরি করছে, তেমনই ছবি প্রজেকশনেরও গ্যাজেট তৈরি হচ্ছে। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে বহু চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে এখন। আমি নিজে একটা পরীক্ষামূলক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছি ২০১৪ থেকে, এরকম আরও দুটো ফেস্টিভ্যালের নাম তো করাই যায়, পিপলস্ কালেক্টিভ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং ‘ডায়ালগস’ এলজিবিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।
এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
মধুজাঃ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। তার কারণ, সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন জিনিস বিশেষভাবে জানার সুযোগ ঘটে। সরকারি-বেসরকারি বহু নামী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে রয়েছে, যেখানে উন্নতমানের উপকরণ এবং শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়াও সিনেমার ইতিহাস, এক্সপোজার এবং সর্বোপরি সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা, মোট কথা সামগ্রিকভাবে একটা পরিবেশ পাওয়া যেখানে সবাই সিনেমা নিয়ে চর্চা করছে। সেটা তো একটা ধার তৈরি করে, তাই না? তবে এটাও বলা যায় না যে, প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট না থাকলে কেউ সিনেমা বানাতে পারবে না। অনেকে ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাঁরা লেখেন, ছবি আঁকেন কিংবা ভালোবেসে সিনেমা-চর্চা করেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সিনেমা বানাতে চান, তাঁরা সিনেমা বানাচ্ছেন। কেউ কেউ যে খুব প্রশংসনীয় কাজ করেন না, এমনও নয়। এটা তো বরাবরই হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠান হোক বা প্রতিষ্ঠানহীন নিজস্ব উদ্যোগ, ‘লার্নিং’ বা শেখার কোনও বিকল্প নেই।
এর আগেও আপনার কাজ, আপনার লেখা সিনেমা, পরিচালিত ছবি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে, কিন্তু সেই অর্থে প্রচার পায়নি। আপনি কি সচেতনভাবে প্রচার এড়িয়ে চলেন?
মধুজাঃ সচেতন বা অসচেতনতার বিষয় নয়। আসলে, আমার আগের ছবিটা (কার্নিভাল) একেবারেই একটা এক্সপেরিমেন্টাল ছবি ছিল। সেটা নিয়ে খবর হয়েছিল, তবে ২০১২-তে সবার হাতে স্মার্ট ফোন ছিল না, তার ফলে সংবাদ মাধ্যমের যে ব্যপ্তি, সেটা অনলাইন-প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কম ছিল এবং ছবিটাও সে অর্থে ন্যারেটিভ ছবি ছিল না। বলা ভালো এক্সপেরিমেন্টাল ফিচার লেন্থ ফিল্ম। সে অর্থে হল-এ রিলিজ হওয়ার সিনেমা নয়। একটা ন্যারেটিভ ছবি বানালে সেটা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ থাকে, যেটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজে থাকে না। ছবি মুক্তির আগে চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়া, পুরস্কার পাওয়া, দর্শকের স্বাধীন মতামতকে এগুলো প্রভাবিত করে?
ছবি মুক্তির আগে চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়া, পুরস্কার পাওয়া, দর্শকের স্বাধীন মতামতকে এগুলো প্রভাবিত করে?
মধুজাঃ ফেস্টিভ্যালে যাওয়া বা পুরস্কার পাওয়া এগুলো কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে। তবে, আমার মনে হয় সেটা জরুরীও, বিশেষত ইন্ডিপেনডেন্ট ছবির ক্ষেত্রে। যেমন ধরো, তামিল ভাষার ছবি ‘পেবলস্’। একজন তরুণ পরিচালকের প্রথম ছবি। ছবিটা যদি রোটারডাম চলচ্চিত্র উৎসবে ‘টাইগার অ্যাওয়ার্ড’ না পেত এবং সেটা নিয়ে চর্চা না হত, তাহলে হয়তো ছবিটা হারিয়ে যেত। কারণ ইন্ডিপেনডেন্টলি প্রোডিউসড এই ছবির প্রচার-প্রসারের জন্য আলাদা কোনও ফান্ড ছিল না। পুরস্কৃত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এর আলাদা করে একটা গুরুত্ব তৈরি হয়। মানে, এভাবে প্রভাবিত হওয়াটা একদিক থেকে ভালোই। এত ছবির ভিড়ে নির্দিষ্ট একটা সিনেমা দেখার জন্য একটা আলাদা আগ্রহ তৈরি হওয়া। আমার ছবি হোক বা অন্য কারোর, দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইন্ডিপেনডেন্ট সিনেমার ক্ষেত্রে এটা খুবই সাহায্য করে। অনেক সময় পুরস্কৃত ছবি প্রশংসিত হয়, সমালোচিত হয় আবার তিরস্কৃতও হয়। দর্শক ছেলেমানুষ নয় যে ভালো-মন্দ টের পাবে না।
নিজের সিনেমায় চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় মাথায় রাখেন?
মধুজাঃ প্রথমত, চিত্রনাট্য তৈরি হওয়ার পর, সিনেমা বানানোর প্রাথমিক পর্যায়ে চরিত্রগুলোর যে আধা স্ট্রাকচার বা ফর্ম তৈরি হয়, সেখান থেকে কিছু মুখের কথা মাথায় আসে। দ্বিতীয়ত, প্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, অভিনয় হয়তো অনেকেই ভালো করেন কিন্তু চরিত্রের জন্য মানানসই ‘ইন্টেনসিটি’ সবার থাকে না, এই বিষয়টা মাথায় রাখি আমি। যে অভিনেতা চরিত্রটি করছেন তার মুখ মনে থাকবে কিনা, আমার নিজের তাকে স্ক্রিনে ভালো লাগছে কি না। তৃতীয়ত, একটা সিনেমা দাঁড় করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, আমরা যতই অল্টারনেটিভ ছবি বানাই না কেন, আমি একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কাজ করছি, আমার কাস্ট-ক্রু তাঁরা ইন্ডাস্ট্রিরই অন্তর্ভুক্ত, কে কতটা সময় দিতে পারছেন, কতটা পারশ্রমিক নিচ্ছেন বা কতটা অভিজ্ঞ এগুলো নিয়েও ভাবতে হয়। ‘ডিপ সিক্স’ বানিয়ে আপনার নিজের কতটা ভালো লেগেছে? ছবিটা বানাতে গিয়ে মনে রাখার মতো কিছু ঘটেছিল?
‘ডিপ সিক্স’ বানিয়ে আপনার নিজের কতটা ভালো লেগেছে? ছবিটা বানাতে গিয়ে মনে রাখার মতো কিছু ঘটেছিল?
মধুজাঃ দেখো, আমি তো সেভাবে মেনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কাজ করিনি। একটা বড়ো টিম নিয়ে কাজ করাটা খুব সহজ কথা নয়। নিজের একটা জায়গা তৈরি করা, কাস্ট-ক্রু সামলানো, পরিচালনা, এগুলো একসঙ্গে করা একটা অভিজ্ঞতা। পরিচালনা ছাড়াও ‘ডিপ সিক্স’-এ আমাকে অনেক কিছু সামলাতে হয়েছে। চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে কস্টিউম ডিজাইন, আর্ট ডিরেকশন, এডিট…অনেক কিছুই করতে হয়েছে। আর, মনে রাখার মতো ঘটনা বলতে বসলে অনেক কিছুই মনে পড়বে, যেমন তিলোত্তমা (তিলোত্তমা সোম), চন্দন (চন্দন রায় সান্যাল), সুমিত (সুমিত ঠাকুর), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় -এঁদের সঙ্গে আমার ইন্টারঅ্যাকশনগুলো খুবই মনে রাখার মতো। এঁরা আমায় পরিচালক হিসেবে যে সম্মান দিয়েছিলেন, আমার ওপর যতটা ভরসা করেছিলেন, সেটা আমার কাছে বড়ো পাওনা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম যে আমি সঠিক রাস্তায় হাঁটছি, গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছি।
 ‘ডিপ সিক্স’ ছবির একটি দৃশ্য
‘ডিপ সিক্স’ ছবির একটি দৃশ্য
যেহেতু এটা নারীকেন্দ্রিক ছবি, অনেকেই বলেছিল কেউ রাজি হবে না এবং সত্যিই তাই ঘটেছিল। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অনেকের কথাই বলেছিলেন প্রযোজকরা, কেউ করতে চাননি। চন্দনকে আমি আগে থেকে চিনতাম না, সবাই বলেছিল ওকে পাওয়া যাবে না কিন্তু সৌভাগ্যবশত ও রাজি হয়। চন্দন খুব শক্তিশালী অভিনেতা, আমার মনে হয়েছিল ও পারবে। আর তিলোত্তমাকে তো আমি ‘কিস্সা’ (যে ছবির চিত্রনাট্যে সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি)-র সময় থেকেই চিনতাম, আমরা বন্ধু। সুমিতকেও চিনতাম, সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াতাম যখন, তখন ও আমার ছাত্র ছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই ছবিতে একটা দৃশ্যেই আছেন। আমাদের সংশয় ছিল আমরা ওঁর চাহিদা মতো পারিশ্রমিক দিতে পারবো কিনা, একটা দৃশ্যে অভিনয় করতে উনি রাজি হবেন কিনা, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। একটা ঘটনা যেটা আমি বলতে চাই, সেটা খুব ভালো অভিজ্ঞতা নয়, তাও। একটা দৃশ্য আছে যেখানে মেয়েটির বাবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসেছেন, এই দৃশ্যে একজন থিয়েটার আর্টিস্ট কাজ করেছেন। তিনি কোনও কারণে বুঝতেই পারেননি বা ভাবতেই পারেননি যে আমি এই ছবির পরিচালক। ছবির সব কাজ মিটে যাওয়ার পর, ডাবিং-এর সময় উনি বুঝতে পারেন যে আমিই পরিচালক। সেটা আমার খুব অদ্ভুত লেগেছিল কারণ আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এখন অনেক মহিলারাই কাজ করেন কিন্তু, একটু বড়ো পরিসরে কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এখনও অনেকেই স্বীকার করতে পারেন না।
ডিপ সিক্স-এর ট্রেলার
ডিপ সিক্স যেহেতু নারীকেন্দ্রিক এবং ফিল্ম স্টাডিজের পাশাপাশি আপনি উইমেন্স স্টাডিজের সঙ্গেও জড়িত, তাই একটা প্রশ্ন করছি, অনেকেই মনে করেন ‘মি টু’ আর ‘ফেমিনিজম’ একই বিষয়। আবার অনেকের ধারণা, ফেমিনিজম ক্রমশ আর্বান স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠছে এবং এর যথেচ্ছ অপব্যবহার হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার কী মতামত?
মধুজাঃ ফেমিনিজম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাগরণের কথা বলে আর ‘মি টু’ হল একটা ‘আউটবার্স্ট’, যেটা কখনও না কখনও হওয়ারই ছিল বলে আমার মনে হয়। আমি তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন খারাপ ব্যবহার করে যাবো, এই সময়ে দাঁড়িয়েও খাপ পঞ্চায়েত বসাবো, প্রকৃতির নিয়মেই সেটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এমনকি অত্যাচারের শিকার হওয়া মেয়েটির বক্তব্য জানতে চাওয়া হয় না। যারা ডালগোনা কফি পোস্ট করে সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের অনেকেই মূল বিষয় থেকে সরে এসে উস্কানিমূলক মন্তব্য করতে থাকে যে ‘এবার তুই ওকে মার’, ‘এবার তুই ওকে বল’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমি বা তুমি যদি নিজেদের অত্যাচারিত হওয়া সংক্রান্ত কিছু পোস্ট করি এবং সেখানে কেউ ‘মার মার’ এ জাতীয় কমেন্ট করে সরে পড়ে, তখন তো মনে হবেই যে আমরাই বোধহয় কিছু ভুল করছি। এই ধরনের সোশাল অ্যাক্টিভিটি শুধু ‘মি টু’ নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এটা অস্বস্তিকর। তবে ফেমিনিজম ক্রমশ আর্বান স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠছে, এরকমটা বলা ঠিক হবে না। আমি এরকম অনেককেই চিনি যাঁরা প্রান্তিক, কিন্তু অনেক সাহস সঞ্চয় করে নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন এবং তারপরেও খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। একবছরের বেশি হয়ে গেল অনলাইন ক্লাস-এর সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয়েছে ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষকদের, একজন অধ্যাপক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?
একবছরের বেশি হয়ে গেল অনলাইন ক্লাস-এর সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয়েছে ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষকদের, একজন অধ্যাপক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?
মধুজাঃ শুধু আমার নয়, সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছেই এটা খুব কষ্টের, হতাশাজনক একটা বিষয়। ভার্চুয়াল লেখাপড়ার বিষয়টার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল বা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পড়ানো বা পড়া, ইন্টারনেট থাকবে কিনা, পিডিএফ-পিপিটি সকলের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছাবে কিনা, এগুলো খুবই সমস্যার হয়ে ওঠে। না চাইলেও এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছি কিন্তু এখনও তো আমরা রবোটিক হয়ে যায়নি! আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের যেভাবে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সেটা জীবনে প্রথমবার এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা মিস করলাম, তারাও করলো। একটা ব্যাচ পড়ালাম যাদের সঙ্গে আমার সরাসরি কোনও যোগাযোগই তৈরি হল না।
 নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি গ্রাফিক নভেলে মধুজা মুখোপাধ্যায়ের আর্ট-ওয়ার্ক
নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি গ্রাফিক নভেলে মধুজা মুখোপাধ্যায়ের আর্ট-ওয়ার্ক
অধ্যাপনা, গবেষনা, লেখালিখি, ভিজুয়াল আর্ট, পরিচালনা - এগুলোর যেকোনও একটা বেছে নিতে হলে কোনটা বাছবেন?
মধুজাঃ আসলে, এগুলোর কোনওটাই পরস্পর বিরোধী নয়। মোটামুটি একই সুতোয় গাঁথা। এগারো-বারো ক্লাসে পড়ার সময় আমি ঠিক করেছিলাম আর্ট কলেজে পড়বো, বিশ্বভারতী এবং আর্ট কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষাও দিয়েছিলাম, নানা কারণে ভর্তি হয়ে ওঠা হয়নি। সিনেমা পরিচালনায় একটা আলাদা ম্যাজিক আছে, সেটা উপভোগ করি। অধ্যাপনা একটা বড়ো দায়িত্ব, তাছাড়া এর সঙ্গে আমার রুটি-রুজির একটা সম্পর্ক আছে। আমার জীবনে আমি যদি কারো কাছে উত্তর দিতে বাধ্য থাকি, তারা হল আমার ছাত্রছাত্রী। আমি কখনো ওদের সঙ্গে ‘বোরড্’ হয়ে যাই না, পড়ুয়াদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে ভালোবাসি আমি। তবে, সর্বোপরি আমার সত্ত্বা বলে ওঠে, আমি একজন আর্টিস্ট, যে অধ্যাপনা, গবেষণা, লেখালিখি, ভিজুয়াল আর্ট, পরিচালনা সবেতেই আছে।































