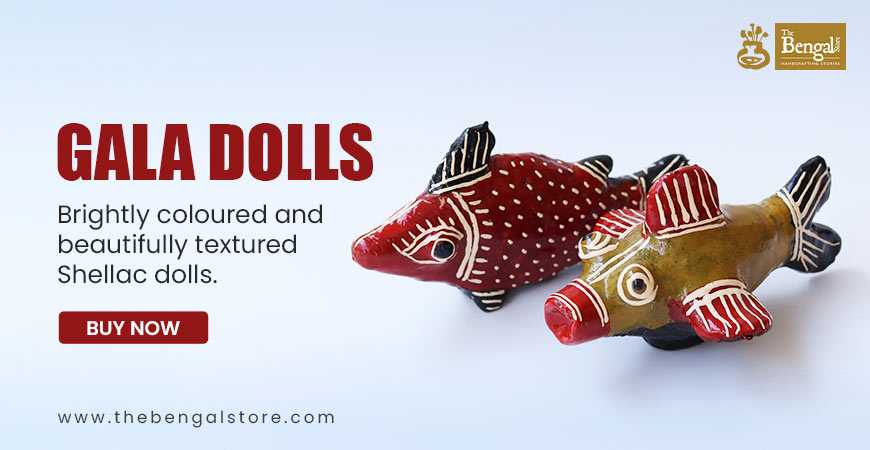একটি নদীর নাম : ঋত্বিক ঘটককে নতুন ভাবে খোঁজার এক আধুনিক মহাকাব্য

- কী দিয়ে শুরু করবে? গপ্পো, যুক্তি, না তক্কো?
- না। দিবাস্বপ্ন দেখবো আমি।
- নস্টালজিয়া?
- হয়তো... নদী। নদীরা ভেসে আসে আমার স্বপ্নে।
- তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ছে?
- এক-ই নদীতে তো আর আগের মতো ফিরে যাওয়া যায় না। জল পাল্টে যায়, পাল্টে যাই আমরাও।
একটি নদীর নাম, নাকি একটি বাড়ির সন্ধান? নদী ও বাড়ি কি পরিপূরক হয়ে ওঠেনি ঋত্বিক ঘটকের জীবনবোধে? তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা, জীবন দর্শন এবং জীবনযাপন জুড়ে ছিল এক বাড়ির সন্ধান; অধরা মাধুরীর মতো শুধু খুঁজে ফেরা এক গন্তব্য। ঋত্বিকের জীবন ও কর্মের এই অভিমুখিতাকেই বোধহয় ধরতে চেয়েছিলেন অনুপ সিং তাঁর প্রথম ছবি ‘একটি নদীর নাম’ (Ekti Nadir Naam/ 2002)-এর মধ্যে। প্রায় ৯০ মিনিটের এই ডক্যু-ফিচার ছবি জুড়ে রয়েছে এক ধ্যনমগ্ন যোগীর মহাকাব্যিক স্তোত্রগান। এ তপস্যা নদীর। আমাদের নদীমাতৃক বঙ্গজীবনের শিকড় লেগে রয়েছে এই নদীর বহমানতায়। তাই এখানে এসে মিলেছে শব্দ, ছন্দ ও দৃশ্যের ম্যাজিক। বাংলার নিজস্ব মিথলজির চরিত্ররা, সাহিত্য ও সিনেমার উপাদান, এবং নস্টালজিয়া একত্রে মিশে তৈরি করেছে এমন এক ওডিসি (Odyssey) যার মায়ামমতা স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখাকে ম্লান করে দিয়ে নির্মাণ করেছে এক আধুনিক মহাকাব্য। এ মহাকাব্যের প্রেক্ষাপট বিভক্ত বাংলাদেশ এবং এর বিস্তার ঋত্বিক।
দেশভাগ থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ- প্রজন্মের পর প্রজন্মের এই ঘর হারানোর আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে অনুপ সিংয়ের ছবিতে। তাই তো এই ছবির চরিত্ররা কাল্পনিকভাবে বিচরণ করেছেন ঋত্বিকের এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে।
নদী শুধুই বহমানতা নয়, একাধারে ভাঙন এবং নির্মাণ। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা এবং দেশভাগের প্রেক্ষাপটে প্রায় এক কোটি মানুষের ঘর ভেঙেছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত সীমান্ত পেরিয়ে শরনার্থী মানুষের ভিড় নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তারা কি তাদের নতুন ঘর খুঁজে পেয়েছিল? অথবা ফিরে যেতে পেরেছিল পুরোনো ঘরে? যাযাবর শরনার্থী জীবনের এই ঘরমুখীনতাকেই তো বারবার ধরতে চেয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক (Ritwik Ghatak) তাঁর ছবিতে। ঋত্বিকের পার্টিশান ট্রিলজির অন্যতম নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী তাই অনুপ সিংয়ের ছবিতে বলেন, “ঋত্বিকের সিনেমায় বারবার ঘরে ফিরতে থাকলাম আমরা। আমাদের পথচলা… ঘর থেকে আরেক ঘরে… ঘর থেকে আবার বাইরে… নতুন বাসার সন্ধানে।” এই পথচলা অমোঘ- অনন্ত।

‘একটি নদীর নাম' ছবিটির নির্মাণশৈলী ঋত্বিকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও, এ ছবির নিজস্বতা এবং অনন্য ভাবনা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিরল। একটি তথ্যচিত্রের প্রধান চরিত্ররা কাল্পনিক হয়েও যেভাবে ঋত্বিকের ঐতিহাসিক সত্যকে ধারণ করেছেন, তা বিস্ময়কর।
দেশভাগ থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ- প্রজন্মের পর প্রজন্মের এই ঘর হারানোর আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে অনুপ সিংয়ের ছবিতে। তাই তো এই ছবির চরিত্ররা কাল্পনিকভাবে বিচরণ করেছেন ঋত্বিকের এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে। ঋত্বিক ঘটকের শিল্পভাবনা, রাজনৈতিক চেতনা এবং তাঁর বিভিন্ন ছবি ও অসমাপ্ত চিত্রনাট্যগুলি থেকে তিল তিল করে চয়ন করা এইসব চরিত্ররা আসলে ঋত্বিক-তন্ত্রেরই এক তাত্ত্বিক সংশ্লেষ। অনুপ সিংয়ের নায়িকা অনসূয়া (শমী কায়সার)-র হয়তো নির্দিষ্ট কোনোও নাম থাকা সম্ভব নয়। তাই তো সে বলে, “এই যাওয়াই আমাকে আমার নতুন নাম খুঁজে দেবে। একটা নাম। তারপর আরেকটা।” ঠিক একই ভাবে এ-ছবির নায়ক নচিকেতা (শিবপ্রসাদ মুখার্জি)-র মধ্যেও বিচরণ করেছে ঋত্বিক-সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্ররা।
দ্য নেম অফ আ রিভার অর্থাৎ একটি নদীর নাম - ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টি। তথ্যচিত্রের আদলে তৈরি হলেও এ ছবির মধ্যে রয়েছে নানান ফিকশন্যাল এলিমেন্ট। মদন গোপাল সিং এবং অনুপ সিং এ ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন ঋত্বিকের জীবনবোধ, রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর বিভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অসমাপ্ত ছবি ও চিত্রনাট্যগুলি থেকে সংগৃহীত নানান উপকরণ সহযোগে। এ-ছবির ক্রিয়েটিভ ও রিসার্চ টিমের অন্যতম সদস্য মধুজা মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক) জানিয়েছেন যে, ঋত্বিকের অভিনেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত গল্পগুলিও এ ছবির চিত্রনাট্যের বুনন তৈরিতে সাহায্য করেছিল। ছবিটির আঙ্গিক প্রথাগত তথ্যচিত্রের নির্মাণশৈলীকে অনুসরণ করেনি একেবারেই; বরং ঋত্বিকের এপিক-মেলোড্রামার লক্ষণকেই স্পষ্টভাবে ধারণ করেছে।
এভাবে ফিকশন ও নন-ফিকশনের মিশেলে অনুপ সিংয়ের এ-ছবি আসলেই ঋত্বিকের বিষয়ভাবনা, নির্মাণশৈলী এবং ঋত্বিকীয় আচ্ছন্নতার মধ্যেই ঋত্বিককে খুঁজতে চেয়েছে। তাই তো ঋত্বিকের ছবিগুলির শ্যুটিংয়ের বিভিন্ন লোকেশনেই- যেমন তিতাস, কার্শিয়াং-সহ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায়- এ ছবির শ্যুটিং সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে এ ছবির নির্মাণ প্রক্রিয়াটাই যেন হয়ে উঠেছিল এক ঋত্বিক-তীর্থে অভিযান। মধুজা মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন.কম-কে এ-প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “ছবির মাধ্যমে আমরা ঋত্বিককে একভাবে চিনি বা তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাকে একভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু অভিনেতারা যাঁরা ছিলেন- বিশেষ করে সুপ্রিয়া চৌধুরী, রোজি, কবরী- এঁদের কাছ থেকে শোনা গল্পগুলি, যার বেশিরভাগটাই ছবিটিতে নেই, থাকা সম্ভব নয়- সেগুলি সাংঘাতিক। এই peripheral গল্পগুলি থেকে উঠে আসা মানুষ ঋত্বিক, ছবির ঋত্বিকের চেয়ে অনেক বেশি volatile- আগ্নেয়গিরির মতো।”

‘একটি নদীর নাম’ ছবিটির নির্মাণশৈলী ঋত্বিকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও, এ ছবির নিজস্বতা এবং অনন্য ভাবনা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিরল। একটি তথ্যচিত্রের প্রধান চরিত্ররা কাল্পনিক হয়েও যেভাবে ঋত্বিকের ঐতিহাসিক সত্যকে ধারণ করেছেন, তা বিস্ময়কর। ছবির কাহিনি মূলত দুজন উদ্বাস্তু যুবক-যুবতীর বহমান প্রেম। এবং তাকে ঘিরেই ঋত্বিকের বিভিন্ন চরিত্ররা এবং তাঁর অভিনেতারা এসে জুড়ে যাচ্ছেন মূল গল্পের মুহূর্ত নির্মাণের জন্য। তাঁরা অনুপ সিংয়ের ছবিতে কখনও ঋত্বিকীয় মেলোড্রামার প্রপস্, কখনও কথক, কখনও ইন্টারলিঙ্ক, কখনও বা জীবন্ত ইতিহাস। এই ছবির চরিত্ররা কেউই রিয়েলিস্টিক ভঙ্গিতে কথা বলছেন না, বরং তাঁদের কথোপকথন নাটকীয় সিচুয়েশনে আধৃত হয়েও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক গভীর তাত্ত্বিক ডিসকোর্স, যা একইসঙ্গে জটিল অথচ কাব্যিক। সেখানে রয়েছে আনন্দ, হতাশা, বিচ্ছেদ, মিলন, নস্টালজিয়া এবং সর্বোপরি ঋত্বিকীয় মাদকতা ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি।
এ-ছবির আখ্যান প্রসঙ্গে মধুজা মুখোপাধ্যায়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তিনি বলেন, “এই ছবির সবচেয়ে জোরের জায়গা হল, ঋত্বিক ঘটকের একটি ছবি থেকে আরেকটি ছবিতে বিচরণ, এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সংলাপ যেটি ছবিটির আখ্যানের মধ্যে সম্ভব হচ্ছে, এবং তাকে চলচ্চিত্রের ভাষার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং আশ্চর্য ব্যাপারও বলা যায়।”
এ ছবির নির্মাণশৈলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেকে মহাজনের ক্যামেরা এবং অর্ঘ্যকমল মিত্রের সম্পাদনায় ছবির বিষয়বস্তু ও ট্রিটমেন্টে যোগ হয়েছে একাধিক স্তর। ঋত্বিক ঘটকের এপিক মেলোড্রামার ছাপ এখানে স্পষ্ট। ঋত্বিকের সাদা-কালো ছবির ভুবনকে রঙে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুপ সিং বেছে নিয়েছেন কিছু বিশেষ এবং বাহুল্য-বর্জিত প্রাকৃতিক রং, যেমন- সবুজ বা নীল। শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারেও এ-ছবি হয়ে উঠেছে বিশেষ, যা ঋত্বিকের ছবির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কাব্য ও সংগীতের আলাপ এই ছবির জটিল বিষয়কেও করে তুলেছে উপভোগ্য। যেহেতু একটি গল্পসূত্রকে অনুসরণ করেও পরিচালক আসলে এক চূড়ান্ত ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অন্য অনেক আলম্বিত গল্প যা ঋত্বিকের জীবনবোধ, রাজনৈতিক ভাবনা, তাঁর বিভিন্ন সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ ছবি ও চিত্রনাট্য, ছবি তৈরির ইতিহাস অভিনেতাদের সঙ্গে ঋত্বিকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্তর থেকে উঠে এসেছে। তাই এই সমগ্র বিক্ষিপ্ততাকে একটি সৃজনশীল আখ্যানের মধ্যে যথার্থভাবে ধারণ করাটা নিঃসন্দেহে পরিচালক, অভিনেতা এবং সম্পূর্ণ ক্রিয়েটিভ টিমের দক্ষতা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর হয়ে থেকেছে।
এনএফডিসি এবং বিএফআই-এর সহযোগিতায়, ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবির শ্যুটিং ১৯৯৭-৯৮ সালে সম্পন্ন হলেও বাজেট বৃদ্ধির কারণে বেশ কয়েক বছরের জন্য এই ছবির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আসলে ছবিটি একটি তথ্যচিত্র হলেও, একঝাঁক তারকা অভিনেতার উপস্থিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শ্যুটিং করাই ছিল এই বাজেট বৃদ্ধির মূল কারণ। তবে অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০০৩ সালের ২৮ জুন ছবিটি মুক্তি পায়। পূর্ব আফ্রিকার সিলভার ধো পুরস্কার বিজয়ী এই ছবি চলচ্চিত্র সমালোচকদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হলেও, বেশিরভাগ দর্শকের কাছেই এই ছবিটি থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত। অবশ্য ঋত্বিক ঘটক নিজেই যেখানে সিংহভাগ বাঙালি দর্শকের কাছে অধরা রয়ে গেলেন, সেখানে ঋত্বিক-বিষয়ক ছবি, বিশেষ করে সেটি যখন একটি তথ্যচিত্র, তার যে যথার্থ মূল্যায়ণ হবে না সে আর আশ্চর্য কী!

তবে সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পালাবদল এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নয়া সমীকরণ হয়তো উসকে দেয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও দেশভাগের স্মৃতি। দুই দেশের সম্প্রীতিকে পাথেয় করেই যেমন তৈরি হয়েছিলো ঋত্বিকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৭৩), তেমনই তৈরি হয়েছিলো অনুপ সিংয়ের এই ছবি- ‘একটি নদীর নাম’। দুই বাংলার নতুন ও পুরোনো ঘরের মধ্যে বিস্তৃত এই যে ক্ষতবিক্ষত স্মৃতিপথের যাত্রীরা অনুপ সিংয়ের ছবিতে অবলীলায় বলতে পেরেছেন, “ওপারে চলে গিয়ে আমরা আকাশ থেকে পাখির মতো এ-সবকিছু দেখবো… জল এবং ডাঙার একে অপরকে ক্রমাগত পার করা দেখতে দেখতে আমাদের চোখ ভিজে উঠবে”; তা কি আগামীর কণ্ঠে সমুচ্ছ্বাসে উচ্চারিত হবে?
_________
একটি নদীর নাম | পরিচালনা: অনুপ সিং | চিত্রগ্রহণ: কেকে মহাজন | সম্পাদনা: অর্ঘ্যকমল মিত্র | সংগীত: সঞ্জয় চৌধুরী | শিল্প: চোকাস ভরদ্বাজ | পোশাক: মধুজা মুখোপাধ্যায় | শব্দ: নীহার সমল