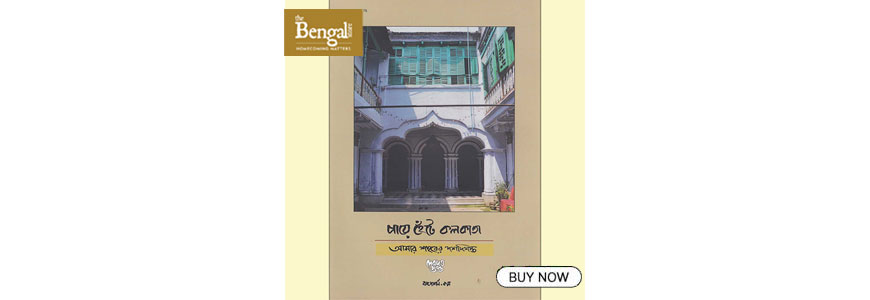করুণ শঙ্খের মতো ‘হাওয়া’

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একটি উপন্যাস রয়েছে, নাম ‘হাওয়া সাপ’। উপন্যাসের এক জায়গায় তিনি বলছেন, সমুদ্র থেকে উঠে আসে এক ধরনের রহস্যময় বাতাসের ঘূর্ণি, “স্নেকউইন্ড”, সাপের মতো সেই হাওয়ার ছোবলে মানুষ খুন হয়ে যায়। ‘বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে’র সঙ্গে তুলনীয় এই রহস্যময় হাওয়ার সাপই যেন ‘গুলতি’ হয়ে উঠে আসে ‘হাওয়া’ চলচ্চিত্রে (Hawa Film)। খুন করতে, প্রতিশোধ নিতে। আছড়ে পড়া ঢেউয়ের নিচে গুমড়ে থাকা ক্রোধ ‘হাওয়া সাপে’র রূপে ধরা পড়ে এই চলচ্চিত্রে। মেজবাউর রহমান সুমনের (Mejbaur Rahman Sumon) এই ছবি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অভূতপূ্র্ব ঘটনা। এর কারণ অনেকগুলো।
প্রথমত, এই ছবির কাহিনি মাঝ দরিয়ার এবং পুরোটাই শুট হয়েছে সেখানে। এমন ভূমি বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্র বাংলাদেশে (Bangladesh) আর হয়নি। দ্বিতীয়ত, এই ছবির গল্প, যা একেবারেই ব্যতিক্রমী, আর দশটা বাংলা ছবির থেকে এর গল্প বলার ধরনটাই আলাদা। তৃতীয়ত, ছবির বহুস্তর। রূপকাশ্রিত পরাবাস্তব এই ছবি যে রাজনৈতিক প্রস্তাবনা নিয়ে হাজির হয়, তার নজির বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে (Bangladeshi Film) বিরল। চতুর্থত, কারিগরিভাবে নিখুঁত ছবিটির গল্পটা ঠিকঠাক বলতে পেরেছেন পরিচালক, এর নজিরও বাংলাদেশে খুব বেশি নেই। পঞ্চমত, চার বছরের প্রস্তুতি ও কঠোর পরিশ্রম করার পর ছবিটি মুক্তি দেয়া হয়েছে, ঢাকাই ছবির অধিকাংশই ‘ধর তক্তা মার পেরেক’ রীতিতে বানানো হয়। প্রস্তুতির কারণেই এ ছবির চিত্রনাট্যে যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।
চার বছরের প্রস্তুতি ও কঠোর পরিশ্রম করার পর ছবিটি মুক্তি দেয়া হয়েছে, ঢাকাই ছবির অধিকাংশই ‘ধর তক্তা মার পেরেক’ রীতিতে বানানো হয়। প্রস্তুতির কারণেই এ ছবির চিত্রনাট্যে যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

মজার বিষয়, ছবিটির ভেতর গতানুগতিক চিত্রনাট্যের ত্রিভুজ কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তাল ও লয়টা একটু ভিন্ন। দ্বন্দ্বগুলো ছোটো ছোটো। এ কারণে অনেক দর্শক হতাশ হয়েছেন। তারা এর ভেতর টুইস্ট চেয়েছেন, স্পাইস চেয়েছেন। আবার অনেকে, ছবি মুক্তির আগে জনপ্রিয় হওয়া ছবির গান ‘সাদাসাদা-কালাকালা’ (Shada-shada Kala-kala) শুনে একধরনের পূর্ব ধারণা নিয়ে ছবি দেখতে গেছেন। গিয়ে যখন তারা নিজস্ব রুচির সঙ্গে ছবিটি মেলাতে পারেননি, তখন বলেছেন, এটা কেমন ছবি, গান ছাড়া আর কিছু জমে ওঠেনি। সিনেমার গল্প জমে ওঠা চাই—এই প্রত্যাশা নিয়ে যে দর্শক সিনেমা দেখতে যান, তিনি সাধারণ দর্শক। সিনেমার সব গল্প যে জমে ক্ষির হয় না, সে তা জানে না। সব গল্পের ভেতর কাহিনি পাওয়া যায় না। কোনো কোনো গল্প হয় নিস্তরঙ্গ, নিথর, ঝিম ধরা দুপুরের মতো।
দুনিয়ায় সিনেমার ধরন ও ধারণ পাল্টে গেছে বহুদিন হলো। সহস্র নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এখন চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। আধুনিক চলচ্চিত্রের (Modern Cinema) এই মনমেজাজ পড়ার মতো পরিপক্কতা দেশের মানুষের ভেতর এখনো অব্দি গড়ে ওঠেনি। সিনেমা দেখা, পাঠ করা এক চর্চার নাম। কবিতা যেমন পড়ার অভ্যাস না থাকলে আধুনিক কবিতা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তেমন আধুনিক চলচ্চিত্রের বয়ান যে পথ ধরে চলে সে পথ অচেনা ঠেকে। তখন দর্শক এক বাক্যে বলে ওঠে, ভালো লাগেনি। কিন্তু যে ধৈর্য্য ও ভালোবাসা আধুনিক সময়ের সিনেমা দাবি করে, সেটা অধিকাংশ দর্শকই ব্যয় করেন না। তারা আর দশটা কাজের পাশাপাশি সিনেমা নিছক বিনোদনই ভাবেন। উল্টোদিকে হাতে গোনা কয়েকজন নির্মাতা সিনেমাকে শুদ্ধ বিনোদনের মাধ্যম মনে করেন না। তারা চিন্তায় ও মননে নাড়া দিতে চান, জায়গা গড়ে নিতে চান।
শিল্পে স্যুররিয়েলিজম, ম্যাজিক রিয়েলিজম, পোস্ট মর্ডানিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, ইম্প্রেসনিজম, এক্সপ্রেসনিজম, কিউবিজম, ভোর্টিসিজম ইতি ও আদি আন্দোলন ও ভাবনা-বিস্ফোরণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। চলচ্চিত্র হলো সেই মাধ্যম, যা সকল শিল্পমাধ্যমকে নিজের ভেতর ধারণ করতে পারে। শিল্পের আন্দোলন ও চিন্তাকেও সে সানন্দে বহন করতে পারে। তাই চলচ্চিত্র শুধু দর্শন বিচ্ছুরণ করে না, মাঝেমধ্যে নিজেও হয়ে ওঠে দর্শন। চলচ্চিত্রকে যদি ফ্লুয়িড বলি, তরলের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলি, ভুল বলা হবে না। সে নানা ধারায় মেশে, নানা চিন্তাকে দ্রবীভূত করে, নানা আকার ও রং ধারণ করে। ‘হাওয়া’ গ্রহণ করেছে পরাবাস্তবকে, বিচ্ছুরিত করেছে রাজনীতি।
ছবি মুক্তির আগে জনপ্রিয় হওয়া ছবির গান ‘সাদাসাদা-কালাকালা’ শুনে একধরনের পূর্ব ধারণা নিয়ে ছবি দেখতে গেছেন। গিয়ে যখন তারা নিজস্ব রুচির সঙ্গে ছবিটি মেলাতে পারেননি, তখন বলেছেন, এটা কেমন ছবি, গান ছাড়া আর কিছু জমে ওঠেনি।
আমাদের দর্শক মূলত তিন অংকের সরল কাহিনি দেখে অভ্যস্ত। শুরু-মধ্যম-শেষ। অথচ জঁ লুক গদার (Jean-Luc Godard) গত শতাব্দীতেই রাষ্ট্র করেছেন গল্পের শুরু, মধ্যমা আর সমাপ্তি থাকবে, কিন্তু সেটা যে অভিন্ন ক্রমেই থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই।
যদি তথাকথিত চিত্রনাট্যের ত্রিভুজ গঠনের কথাও বলি, ‘হাওয়া’তে তা আছে। শাস্ত্রের বাইরে যায়নি ‘হাওয়া’। যেটা তারা করেছে, তা হলো একটি সরল বয়ানের তলে কয়েকটি চোরা স্রোত তৈরি করে দিয়েছেন। সরল দর্শক সরল বয়ানকেই দেখছেন। কিন্তু এর চোরা স্রোতে থাকা মূল প্রস্তাবনাই অনেকে পাঠ করতে পারছেন না বলে বোধ করি। ‘হাওয়া’ শেষ অব্দি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিপ্লবী আদর্শের ফিরে আসা ও এর বিজয়কে রূপকথায় পুরে রাজনৈতিক ভাষাবলয় তৈয়ার করে। এই ছবি যেভাবে বাংলাদেশের পুরাণকে ছেনে তুলে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন, সেটাই আধুনিক শিল্প করে থাকে। আধুনিক শিল্প লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতিকে প্রাসঙ্গিক বা কনটেক্সচুয়াল করে তোলে আধুনিক সময়ের সাথে, নিয়ে যায় বিশ্ব দরবারে। ‘লোকাল’কে সে ‘গ্লোবাল’ করে তোলে। স্থানীয়কে এই বৈশ্বিক করে তোলাকেই বলে ‘গ্লোকালাইজেশন’। আধুনিক শিল্প মানুষের মনকে চমকে দিতে চায় না। চিন্তাশীল করে তোলার তৎপরতা চালায়। আধুনিক শিল্পে ইদানীং বক্তব্যও থাকে না। বার্তা বা মহান বাণী প্রচার করাও আধুনিক শিল্পের দায়ের ভেতর পড়ে না। দর্শককে বিনোদিত করার দায়ও তার নেই। এই সময়ের শিল্পকর্ম দর্শককে নিজের আরামাঞ্চল থেকে ছিটকে দিতে চায়, তাকে আরাম দেয়ার বদলে।
বোঝা যাচ্ছে, ‘হাওয়া’ যে হাওয়া ছড়িয়েছে, তা অনেকের কাছে আরাম বোধ হয়নি। এই যে হয়নি, তারপরও তারা ভাবছেন, চিন্তা করছেন, এটাই চেয়েছে ‘হাওয়া’। ‘হাওয়া’ বাংলাদেশের আধুনিক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে “করুণ শঙ্খে”র মতো বেজে যাবে, একে এড়িয়ে চলা যাবে না।