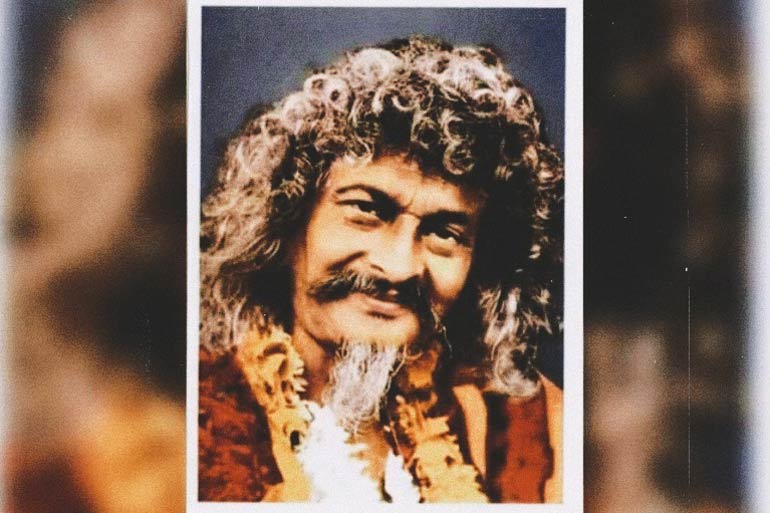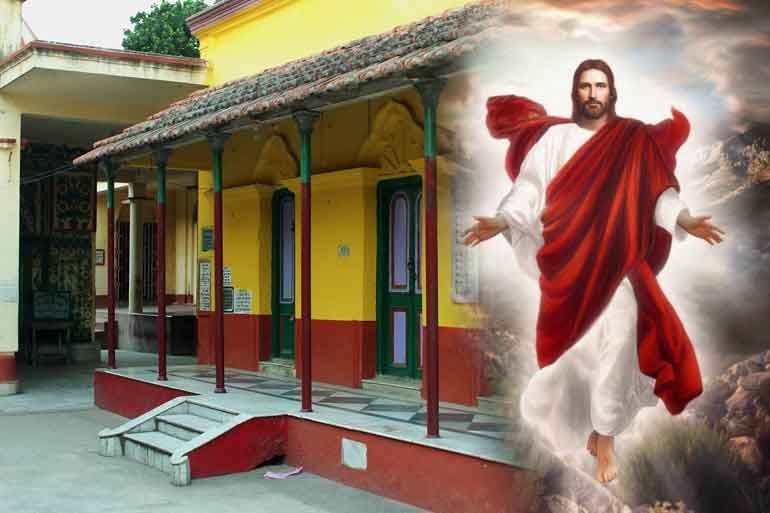অবহেলিত গ্রামবাংলার সাহসী প্রতিবাদ ‘সাহেবধনী’ গান

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান মানে, বড়লোক সাহেবদের গান - আক্ষরিক অর্থ খানিকটা এরকম ঠেকলেও ব্যাপারটা যে আদৌ সেরকম নয়, তা বুঝলাম সুধীর চক্রবর্তীর ‘সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান’ বইটি পড়ার পর। নদীয়ার লোকসংগীত নিয়ে গবেষনা করতে গিয়ে সুধীরবাবু নদীয়ার গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গ্রামের মানুষের ভিটেতে থেকেছেন, গান শুনেছেন। গ্রামবাসীরাই তাঁকে হদিশ দিয়েছেন কোথায় গেলে গান পাওয়া যাবে, কোন আখড়ায় আছে হাতে লেখা গানের খাতা, কোন সাধকগায়ক বা ফকির বোঝাবেন গানের মর্ম, চান্দ্রমাস অনুসারে কোন তিথিতে কোথায় বসে বাউল ফকিরদের মেলা।
ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দুই বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে লোকধর্ম ও গৌণধর্মীদের গান সংগ্রহ করে এবং তারও বেশ কয়েক বছর পর আরও গবেষনা করে সুধীরবাবুর হাতে প্রাণ পায় ‘সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান’ বইটি।
তাঁর লেখা পড়লে জানা যাবে, উদার আত্মনির্ভর এক লোকসমাজের কথা, যাঁদের ভাষায়, ছন্দে, গানে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যমান শ্রেণিবর্ণ বর্গের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনা ও উন্নত মানবধর্ম। তবে সুধীরবাবুই যে প্রথম গৌণধর্মী সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অন্বেষণ করেছেন তা নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন থেকে শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও মনসুরউদ্দিন, এইচ এইচ উইলসন, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আগেই এ সব সম্প্রদায়কে বুঝতে চেয়েছেন বা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের গান। তবে নানা বর্গের নানা গৌণ সম্প্রদায়গত গানকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে না পেরে ‘বাউল’, এমন এক জেনেরিক সংজ্ঞায় তাঁরা ফেলে দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে তথ্যভিত্তিক ও কুতূহলী গবেষণার কাজটি করে গিয়েছেন ১৮৭০ সাল বরাবর অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁর ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ বইয়ের দুই খণ্ডে। হয়তো সম্পূর্ণত বা বিস্তৃত অনুসন্ধানলব্ধ সরেজমিন কাজ নয়, তবু তিনি বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে বিধিবদ্ধ ভাবে সর্বপ্রথম অনেকগুলি লোকায়ত গৌণধর্মের প্রাথমিক প্রতিবেদন লিখে গিয়েছেন।”
সেই সব গৌণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী ও খুশিবিশ্বাসী, এই চারটি সম্প্রদায়ের উৎস, সাধনকেন্দ্র ও গুরুপাট অখণ্ড নদিয়া জেলাতেই। সুধীরবাবুর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান।
সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।
সাহেবধনীদের গানে রয়ে গেছে আঠারো শতক থেকে প্রবাহিত প্রচ্ছন্ন এক জনবিন্যাসের আলেখ্য। বাংলা লৌকিক গানের বড় কয়েকটি নমুনা খুঁজতে গেলে লালন শাহ, রামদুলাল পাল এবং কুবির গোঁসাই, এই তিনজনের নামই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কারণ, লালনের গানে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা বাউল মার্গের সবচেয়ে স্পষ্ট মতামত, রামদুলাল বা দুলাল চাঁদের গানে কর্তাভজাদের ধর্ম ও সাধনতত্ত্বের মূলসত্য এবং কুবির গোঁসাইয়ের গানে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস।
কর্তাভজাদের সঙ্গে সাহেবধনীদের বিশ্বাসের দিক থেকে অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও, আচরণগত তফাৎ আছে বেশ খানিকটা। লালনপন্থীদের সঙ্গে ফকিরি তন্ত্র ও বাউল মতবাদের ছোটখাটো অনেক তফাৎ আছে। সাঁই-মত আর দরবেশীতন্ত্র এক নয়। খাঁটি ইসলামের সঙ্গে ফকিরদের যোগাযোগ যতখানি, বাউলদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের ততটা যোগাযোগ নেই। এসব স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হয়। তাঁরা শাস্ত্র মানেন না, কিন্তু তাঁদের মৌখিক আচরণবিধিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে: ‘আপন সাধন কথা, না কহিও যথা তথা।‘ এটা সব মরমী সাধকই মেনে চলেন, এমনকি সাধারণ অজ্ঞ জিজ্ঞাসুকে তাঁরা খনিকটা উল্টোপাল্টা বলে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে দেন। তাঁদের গানের ভাষা ও প্রতীক তাই আমাদের অচেনা, প্রহেলিকাময়।
আছে আর এক সত্য বাণী
দীনদয়াল সাহেবধনী নামের ধনী
ব্রজের রাইধনী সেই ধনী নদেতে উদয়;
নদীয়া জেলার শালিগ্রাম অঞ্চলে সাহেবধনীদের উৎপত্তিস্থল, সেইজন্যই ব্রজের রাইধনীর ‘নদেতে উদয়’ কথাটার সার্থকতা বোঝা যায়। দীনেশ্চন্দ্র সেন থেকে আহমদ শরীফ পর্যন্ত অনেক পণ্ডিতের অনুমান যে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূলে ছিলেন একজন মুসলমান। আবার, সাহেবধনী সম্পর্কে সর্বপ্রথম লেখা, ১৮৭০ সালে মুদ্রিত অক্ষয়কুমার দত্তের ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ বই থেকে পাওয়া যায়, “এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে একজন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বর আরাধনায় ও পরোপকার সাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দুমতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও একজন মোসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।”
‘সাহেবধনী ঘরের সত্যনাম’ বলে একটি হাতে-লেখা পুঁথি সুধীরবাবু পেয়েছিলেন বৃত্তিহুদা গ্রাম থেকে, যাতে রয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের লৌকিক মন্ত্রতন্ত্র। তার একটিতে লেখা আছে: ‘ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য।’.jpg) সাহেবধনীদের সবচেয়ে বড় গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর দুটি গানে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের চমৎকার উক্তি করেছেন যা উল্লেখযোগ্য:
সাহেবধনীদের সবচেয়ে বড় গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর দুটি গানে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের চমৎকার উক্তি করেছেন যা উল্লেখযোগ্য:
আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।
একহাতে বাজে না তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা ভার।।
অথবা,
একের সৃষ্টি সব পারিনা পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপনসুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
এভাবেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গানে ধর্মসমন্বয় ঘটছে। এ ছাড়াও এই সম্প্রদায়ের গানে, কুবির গোঁসাইয়ের পদে উঠে আসত দারিদ্র। কুবিরের শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের একটি পদে পাওয়া যায়:
যে ভাবেতে রাখেন গোঁসাই সেই ভাবে থাকি
আমি অধিক আর বলবো কী।
কখনও দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী—
কখনও জোটে না ফেন আমানি।
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি।।
কুবির শুধুই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের ভাষাকার ছিলেন না, তিনি দ্রষ্টা ও ভাবুক। শহর জীবনের চোখ-খোলা পরিবেশ, উচ্চশিক্ষা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না, তাহলে কোথা থেকে এত সব কল্পনা ও বিরোধী উদাহরণ তাঁর মাথায় আসত?
এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ এল লয়েড তাঁর ইংল্যাণ্ডের লোকসংগীত-সংক্রান্ত বইতে একটি ঘটনার বিবৃতি দিয়েছিলেন। অ্যান্টিলেসের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের চেয়ে বেশি। সেখানকার পুরুষেরা সকালবেলা চলে যেত কাছে-পিঠে নগরে রুজিরোজগারের চেষ্টায়। তাদের কাছে জরুরি কোনও খবর পাঠানোর দরকার হলেই বৌ বা মেয়েরা একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলত। তাই দেখে অবাক পর্যটক তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তোমরা ঐ গাছের সঙ্গে কথা বল কেন?”
তারা বলে, “আমরা তো গরীব, আমাদের তো টেলিফোন নেই, তাই।”
ঘটনার এই পর্যন্ত বৃত্তান্ত দিয়ে লয়েড একটি চমৎকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তিনি বলেন, “The mother of folklore is poverty.”
এই কথাটাই একটা বড় ইঙ্গিত দেয় যে, দারিদ্র থেকে জন্ম নেয় কল্পনা, অভাববোধ, উপকথা। কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও আছে। দরিদ্র গ্রাম্য জনসমাজে শহর নিরপেক্ষ একটা জীবন-চেতনা গড়ে তোলে, যার প্রতিফলন ঘটে গ্রাম্যগানে - লোকগানে। এখন আর সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। তাঁদের গানও চর্চার অভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ধরা যেতে পারে। তবে, এখনও এই সম্প্রদায়ের গান প্রাসঙ্গিক, শুধু তাই নয়, আমাদের উচিত অবহেলিত উপেক্ষিত বাংলার গ্রাম্য গানের সাহসী প্রতিবাদ বা স্বচ্ছ জীবনের ভাষাকে তুলে ধরা, যাতে মরে গিয়েও বার বার বেঁচে উঠতে পারে তাদের স্বতন্ত্র মতবাদ।
ঋণঃ
সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গানঃ সুধীর চক্রবর্তী
আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৪ বৈশাখ ১৪২০ রবিবার ২৮ এপ্রিল ২০১৩
ছবি ঋণঃ
ইয়ংগিস্তান