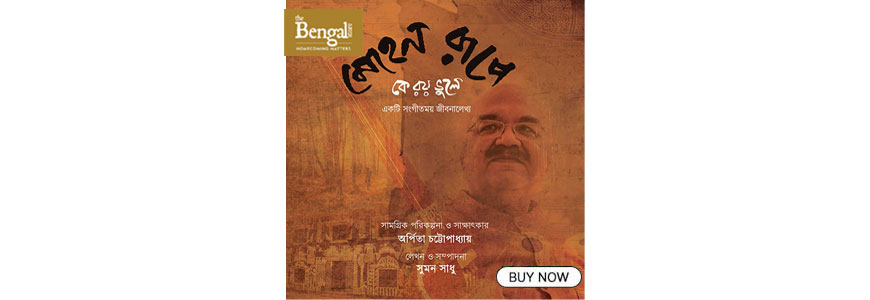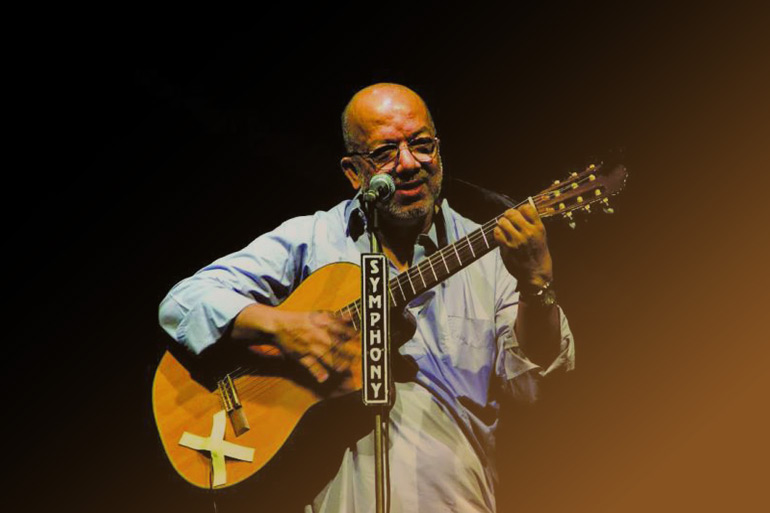কথায়-সুরে দেশ চেনায় দেশপ্রেমের গান
(১)
কখন রচিত হয় দেশপ্রেমের গান? কখন দেশটাকে নিয়ে আমরা এত বেশি ভাবি যে, উত্থিত আবেগ আমাদের গান বা কবিতার দিকে ঠেলে দেয়? দেশ মানে তো দেশের ভৌগোলিক চেহারা-টা শুধু নয়, দেশ মানে দেশের মানুষকে নিয়ে তার সমস্তটা। শুধু দেশের প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা করে যে কবিতা বা গান, তার মূল্য আমাদের কাছে কবিত্বের মূল্যটুকু পায় মাত্র, তার বেশি নয়। কিন্তু যে কবিতা বা গান, দেশের জীবন্ত অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তার মূল্য কি তত বেশি? নিশ্চয় দেশের প্রাকৃতিক, মানবিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক— সব রকমের অস্তিত্বের কথা যদি ফুটে ওঠে কবিতায় বা গানে, তবেই তাকে আমরা স্মরণীয় বলে ভাবি। শুধু নিষ্প্রাণ স্তুতি নয়, তা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের আবেগ আর অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই আবেগটির নাম দেশপ্রেম। দেশের স্বাভাবিক, গতানুগতিক অবস্থায় তা হয়তো আমাদের মনে ঘুমিয়ে থাকে। তাই সব সময় দেশপ্রেমের গান রচনা করা হচ্ছে, এমন ঘটনা ঘটে না।
দেশের কথা ভাবা জরুরি হয়ে ওঠে যখন আমরা ভাবি দেশ কোনও না কোনওভাবে দুর্গত ও বিপন্ন এখন, আমাদের আর সব চিন্তা ও বিবেচনার মধ্যে তার কথা একটু বেশি করে ভাবা দরকার। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, স্বাধীনতার লোপ, দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার অপমান, সেই অপমান ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস, তার জন্য সাধারণ মানুষের চেতনার জাগরণের প্ররোচনা আর এগিয়ে আসার আহ্বান, ভীরুতা ছেড়ে ভয় ভাঙবার ডাক, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ডাক। হয়তো এইভাবে তার একটা সরলীকৃত ক্রম করা যায়। এর বিস্তার হতেই পারে, গীতিকাররা তা দেখিয়েছেন।
ভালোবাসার প্ররোচনা
ক) দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অতীত ও বর্তমান গৌরব, আবেগের তীব্রতা সঞ্চার
খ) দেশের বর্তমান দুর্গতি, (বিদেশি) শত্রুর অপশাসন ও অত্যাচারকে দায়ী করে প্রতিকারের আহ্ববান
গ) সন্তানদের যোগ্য হয়ে ওঠার ডাক, প্রতিকারের উপায় নির্দেশ
ঘ) বিদ্রোহ, যুদ্ধের উৎসাহদান পরিণাম
ঙ) জয়ে উল্লাস, পরাজয়ে সান্ত্বনা

(২)
পঞ্চকবি-র আলাদা আলাদা আলোচনা করলে দীর্ঘ পরিসর দরকার হবে। আমরা উপরে বলেছি যে, ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেশপ্রেমের গান মূলত রচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনে ঔপনিবেশিকতার আবহে। কখনও কখনও অবশ্য এই আধুনিক ঔপনিবেশিকতাকে মধ্যযুগীয় ঔপনিবেশিকতা-র একটা ছদ্মবেশ পরানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের অভিযানকারীদের ভারত আক্রমণ ও অধিকার দেখিয়ে। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) অধিকাংশ দেশপ্রেমের গানই নাটকের গান, যেগুলিতে মূলত বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুতদের দেশপ্রেম বা রাজ্যপ্রেম উৎসাহিত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। তাতে যুদ্ধে যাওয়ার গান (ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে), ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব (ধনধান্যপুষ্পে ভরা), পরাজয়ের গ্লানি থেকে উজ্জীবনের বাণী (গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই) ইত্যাদি সবই আছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এই দেশপ্রেমের নাটকগুলি যখন লেখা হচ্ছে তখন দেশপ্রেম ইংরেজের বিরুদ্ধে চালিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ মুসলমান বহিরাগতরাও তখন পরাজিত, এবং তারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সকল ভারতবাসীর সঙ্গেই ইংরেজের হাতে পরাজয়ের অপমান ভোগ করছে। কিন্তু সরকারি চাকুরে দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না প্রায় ত্রিশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসে ইংরেজকে শত্রু হিসেবে দেখানো। যাই হোক, এক সময়ে এই গানগুলি থেকে বাঙালি যথেষ্ট দেশপ্রেমের প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-এর তো কথাই নেই। বাঙালি বুঝতে পেরেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে ওই ছদ্মবেশ দরকার ছিল, এবং তাই সে সব বিচারমূলক অনুসন্ধান এবং ঐতিহাসিক ক্রমভঙ্গ উপেক্ষা করে তারা ওই গানগুলি থেকে যথেষ্ট উদ্দীপনা গ্রহণ করেছে, এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে।

সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মতোই দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক নাটক-গুলির অধিকাংশ রচিত হয় বঙ্গভঙ্গের আগে ও পরে। কিন্তু, স্বভাবতই বঙ্গভঙ্গের অভিক্ষেপে। বস্তুতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ বাংলা দেশপ্রেমের গানের একটি বড়ো উপলক্ষ্য, ওই ঘটনাই হল বাংলা দেশপ্রেমের নাটকের এবং গানের প্রধান প্রেরণা-উৎস। প্রবীণতর নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে দেশপ্রেমের উপাদানযুক্ত ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) আর অতুলপ্রসাদ সেনের(১৯৭১-১৯৩৪) দেশপ্রেমের গান খুব বেশি নেই। রজনীকান্তের একটি গানই বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীন দুখিনি মা যে মোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই’। তাঁর আর একটি গান ‘আমরা নেহাত গরিব, তবু আছি সাতকোটি ভাই, জেগে ওঠো’ এখন আর ততটা শোনা যায় না। শোনা না যাওয়ার প্রধান কারণ এগুলি – ওই সময় ও রাজনৈতিক প্রতিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, তা থেকে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে আনা সম্ভব নয়। একই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্ত হলে সেগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারত। যেমন ঘটেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সলিল চৌধুরীর ‘মা গো, ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে’র ক্ষেত্রে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলেই দেশপ্রেমের গানেরও পুনরুজ্জীবন ঘটে। কিন্তু সমস্যা হল, ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি খুব কম ঘটে।

(৩)
সেই জন্য কোনও কোনও দেশপ্রেমের গানে দেশের একটা নিত্য মূর্তি খাড়া করা হয়, যা কোনও সময়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, দেশের অতীত ও বর্তমান গৌরব এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা নিয়ে রচিত, ইতিহাসের ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত হলেও সেই ঘটনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকে না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে সচেতন সংগীতস্রষ্টা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকি অতুলপ্রসাদের ‘উঠো গো ভারতলক্ষ্মী’— কথা, সুর এবং লয়বিন্যাসে চমৎকার হলেও তা নিছক পরাধীন ভারতের গান। তবে তাঁর ‘মোদের গরব মোদের আশা’-কে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম নতুন করে একটি ঐতিহাসিক পুনরাবর্তন উপহার দিয়েছিল, ফলে তা বাঙালিদের কাছে নতুন করে প্রেরণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। এবং ‘বলো বলো বলো সবে’ বা ‘হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর’ এই গানগুলি নিছক প্রেরণাদায়ী বলেই এগুলির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী আবেদন তৈরি হয়েছে। এগুলি কোনও প্রতিযোগিতার সূত্র দেয় না, বরং দেশের উন্নতিকে দেশবাসীর আত্মদানকে আহ্বান করে।
কিন্তু যে দেশপ্রেম সংকীর্ণ সময় ও অনিত্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিক্রম করে দেশের একটি নিত্য ছবি ফুটিয়ে তোলে গানে, তার অধিরাজ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ‘জনগণমন’ এই রকম একটি গান, যা আবহমানের ভারত-সত্তার জয়গান, কোনও বিশেষ সময় বা নির্দিষ্ট ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রদেশের নামগুলির ক্ষেত্রে দু-একটি তুচ্ছ উপলক্ষ্য ছাড়া। তা সংগতভাবেই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ‘আমার সোনার বাংলা’-ও বাংলার অধিবাসীর কাছে তার সৌন্দর্য ও মুগ্ধতা আর ভালোবাসার সংবাদে ভর্তি। তার শেষদিকে একটু সময়ের অনুষঙ্গ আছে, ‘আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি’, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে সে অংশ যথার্থভাবেই বর্জিত হয়েছে।

কবিতায় আর গানে স্বাভাবিকভাবেই অতিরঞ্জন থাকে, দেশপ্রেমের গানেও থাকে। হয়তো মানুষকে উজ্জীবিত উদ্দীপিত করার জন্য তার দরকার হয়। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ধনধান্যপুষ্পেভরা’ গানে নিজের জন্মভূমিকে ‘সকল দেশের সেরা’ বলা। সন্তানের চোখে এমন মনে হতেই পারে। কিন্তু এ থেকে একটা ভুল বার্তা তৈরি হতে পারে। প্রথমত এটা বাস্তব সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু তা কখনও আত্মগর্ব ও দেশগর্বকে এমন মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে, যাতে অন্যদের তুচ্ছ করার একটা প্রবণতা এসে যায়, এবং যা থেকে অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করারও একটা ইচ্ছে এসে যেতে পারে। হিটলার মনে করেছিলেন জার্মানরা ঈশ্বরের বাছাই-করা জাত (Chosen people of God), তাই তিনি চেয়েছিলেন জার্মানরা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব করবে। ইংল্যান্ডের একটি জাতীয় সংগীতও এইরকম ছিল, Rule Britannia, rule the waves! অর্থাৎ হে আমার ব্রিটেন, তোমার রণতরীগুলি সমুদ্র শাসন করুক, মানে সাগরপারের বাণিজ্যে (সাম্রাজ্যে) আমাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম থাকুক। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকানরাও এক সময় বলত, It’s the best country in the world. ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে তাদের স্লোগানই ছিল, My country, right or wrong!
আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। শুধু দেশপ্রেমের গানে নয়, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায়, তাঁর আন্তর্জাতিকতা আর জাতীয়তার দর্শনে। তাই তাঁর গান দেশের গৌরববিবৃতির চেয়ে দেশবাসী হিসেবে আমার সঙ্গে দেশের সম্পর্ক— আমার ঋণ, আমার আত্মনিবেদন, আমার কর্তব্য ইত্যাদি বড়ো হয়ে উঠেছে। সেটা বঙ্গভঙ্গের অনেক আগে থেকেই। উনিশ শতকের ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’ বা ‘আমরা পথে পথে যাব সারে সারে’ গানগুলি তার প্রমাণ দেয়। সেই সঙ্গে সময়স্পৃষ্ট পরাধীনতার গ্লানিও আছে কোনও গানে, যেমন ‘আমায় বোলো না গাইতে বোলো না’। কিন্তু তার লক্ষ্য দেশ নয়, আমরা, আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্তদের স্বার্থবুদ্ধি ও দেশকে উপেক্ষা।
সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি, অহংকৃত দেশপ্রেম যে একটি সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রেরণা, তা স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছিলেন, ‘নৈবেদ্য’-এর একাধিক কবিতায় তার সাক্ষ্য আছে। পরে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে, ‘গীতাঞ্জলি’র ‘ভারত-তীর্থ’ (নাম পরে দেওয়া সম্ভবত) কবিতা; ‘গোরা’, ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস ইত্যাদির মধ্যে আর ইংরেজি Nationalism বইয়ে গ্রন্থিত বক্তৃতাগুলিতে ক্রমশ বিশদ রূপ গ্রহণ করে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই তাঁর দেশপ্রেমের গান কোনও দৃশ্য বা অদৃশ্য শত্রু খাড়া করে না সামনে, দেশের কল্পিত শ্রেষ্ঠতা দাবি করে না। তাঁর ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’ গানে ‘মনোমোহিনী’ কথাটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। এ গানটি বিশ্লেষণ করলে কোথাও কোনও শ্রেষ্ঠতার দাবি উচ্চারিত হতে দেখি না, যদিও এর অনন্যতা ও ঐতিহ্যের কথা বহুভাবে বলা হয়েছে। ‘চিরকল্যাণময়ী’ কথাটির স্বস্তিবাচন লক্ষ করার মতো।
অন্যান্য গানেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেতন। হ্যাঁ, বঙ্গভঙ্গকালীন তেইশটি গানে উদ্দীপক নানা গান আছে, কিন্তু তার পাশাপাশি ‘সার্থক জনম আমার’, ‘ও আমার দেশের মাটি’ – এই গানগুলিকে যদি লক্ষ করি, দেখব যে, এখানে দেশজননীর কাছে আত্মনিবেদন আর ঋণস্বীকারের নিবেদনই বড়ো হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গানটির ‘তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা’ ছত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথ কোনওভাবেই নিজের দেশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে রাজি নন। এই সময়ের গানে তাঁর দেশি পল্লিসুরের ব্যবহার লক্ষ করার মতো, যদিও আগে নানা ধরনের সুর ও তাল তিনি ব্যবহার করেছেন। ‘এক সূত্রে’ গানটির মধ্যে কুচকাওয়াজের তাল থাকলেও তা দেশি রাগ-রাগিণীকে বর্জন করেনি।
দেশপ্রেমের গানে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সংখ্যায় সকলকে ছাড়িয়ে যান তা নয়। এই গানগুলি সম্বন্ধে আরও জরুরি কথা বলা সম্ভব। এ সব গানে রবীন্দ্রনাথ শুধু আবেগবিদ্ধ নন, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ মনন সেই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অন্যরা দেশপ্রেমের স্বরূপ, তার ভালোমন্দ নিয়ে সচেতনভাবে কতটা ভেবেছেন, তাঁদের গান থেকে তার কোনও ইঙ্গিত উঠে আসে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখ এই বিচার থেকে কখনও সরে যায়নি। অন্যদের গানের কথা ও সংগীতগুণে আমরা মুগ্ধ হই, তবে সাংগীতিক বৈচিত্র্যে আর শিল্পশৈলীর শ্রেষ্ঠতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে নানাভাবেই স্বতন্ত্র করে দেখতে প্ররোচিত না হয়ে পারি না।