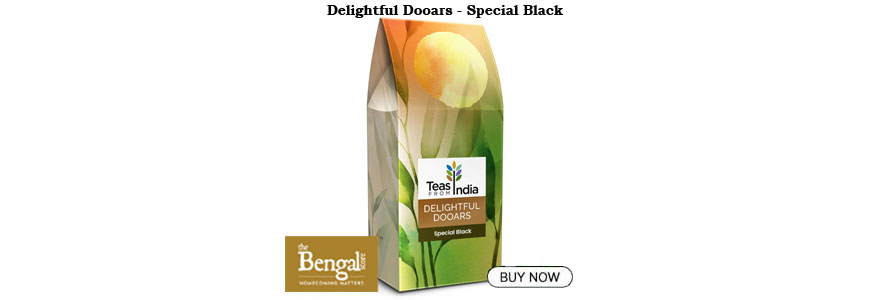তাঁর নামে রয়েছে নক্ষত্রও, অথচ সেভাবে প্রকাশ্যেই আসেননি বিজ্ঞানী-বঙ্গবালা ডঃ বিভা চৌধুরী

তখন অভিজাত এবং ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রথাগত শিক্ষাকে বাঙালি-মননে স্থান দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা তারও আগে বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব, প্যারীচরণ। এমনকি ততদিনে (১৯০২) সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও। ধীর লয়ে হলেও শুধু শিক্ষা নয়, বঙ্গ সমাজে নারী শিক্ষা-অগ্রগতির বীজ বপনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে কলকাতায় এমন এক প্রতিভার জন্ম হয়, যাঁর নামে ২০১৯ সালে মহাকাশে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি নক্ষত্র। তিনি আজ বাঙালি সমাজে প্রায় অনালোচিত এক অধ্যায় – বিজ্ঞানী, মিতভাষী, প্রচারবিমুখ, বিদুষী-বঙ্গবালা - ডঃ বিভা চৌধুরী (Bibha Chowdhuri)।
তখন শিক্ষার অর্থ উপার্জন বা শুধুমাত্র ‘ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-কর্পোরেট’ হওয়ার গড্ডালিকা স্রোত ছিল না। শিক্ষার অর্থ ছিল সম্মান ও নির্ভেজাল জ্ঞানার্জন। বিভার ক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা ছিল তাঁর পারিবারিক শিক্ষাগত ভিত্তি, উন্মুক্ত পরিবেশ। বাকিটা তিনি নিজেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর বাবা বঙ্কুবিহারী চৌধুরী ছিলেন ডাক্তার। হুগলি জেলার ভাণ্ডারহাটি গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান বঙ্কুবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সময় প্রেমে পড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, বিয়ে করেন ঊর্মিলাকে। ঊর্মিলার দিদি নির্মলা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী। সে সময় গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্মদের পছন্দ না করার কারণে বঙ্কুবাবুকে ভিটেমাটি, পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। নবদম্পতি কলকাতায় ব্রড স্ট্রিটে বসবাস শুরু করেন, যেখানে জন্ম হয় বিভার।
বিভারা ছিলেন পাঁচ বোন এবং এক ভাই। প্রত্যেকেই পড়াশোনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বিভার বড়দি রমা চৌধুরী ছিলেন ব্রাহ্ম বালিকা স্কুলের শিক্ষিকা আর এক বোন লীলা চৌধুরী যাদবপুর বিদ্যাপীঠের শিশু বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসর নেন। সব থেকে ছোট বোন উমা চৌধুরী ছিলেন সোস্যাল সাইকলজিতে পি এইচ ডি।
বিভা কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন, এরপর ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে জন্য ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে সেখান থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এস.সি পাস করলেন। তাঁর আগে মাত্র দু’জন মহিলা এই কৃতিত্বের অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে যোগ দিয়েছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সেখানে দেবেন্দ্রমোহন বসু ওরফে ডি.এম বসুর সঙ্গে কাজ শুরু করেন। কিন্তু, ডি.এম. বোস প্রথমে রাজি না হয়ে তাঁকে বলেন, কোনও মহিলাকে দেওয়ার মতো কাজ তাঁর কাছে নেই। হাল ছাড়েননি বিভা। শেষপর্যন্ত তাঁর আগ্রহে মাস্টারমশাই নরম হলেন, বিভা শুরু করলেন তাঁর অধীনে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার কাজ। তাঁর আগে কোনও বাঙালি মহিলা আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেননি।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার শুরু বিভার। ক্লাউড চেম্বার বা মেঘকক্ষের সাহায্যে মহাজাগতিক কণার ভর নির্ণয়ে সমস্যা হয়েছিল, তাই এই যন্ত্র বেশি ব্যবহার করা যেত না। যে কারণে বিকল্প উপায় খোঁজার চেষ্টায় ছিলেন বিভা। বিকল্প পথের সন্ধান পেয়েছিলেন মারিয়েটা ব্লাউ নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী। সেই উপায়টি ভারতে এসে সায়েন্স কংগ্রেসে বলেছিলেন বোথে ও টেলর। তা শুনে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বিভাকে বলেন ডিএম বসু। তার পরই ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন বিভা ও বসু। এই প্লেটে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পড়লে প্লেটে থাকা আয়োডাইড সিলভার অর্থাৎ রুপো ও আয়োডিনে ভেঙে তা রুপোর প্লেটে আটকে যায়। এই বিন্দুগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, মৌলিক কণা কোন পথ দিয়ে গিয়েছে। ১৯৪১ সালে বিভা ও বসুর ভর নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণাপত্র বিখ্যাত পত্রিকা ‘নেচার’-এ প্রকাশিত হয়। গবেষণার জন্য ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলিকে তাঁরা দার্জিলিং, সান্দাকফু ও ভুটান সীমান্তের কাছে ফারি জং নামে এক এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
দুই ধরনের কণা ‘মিউয়ন’ আর ‘পায়ন’-এর ভরের তফাত করতে পারেননি বিভারা। কিন্তু হাফটোন প্লেট ব্যবহার করায় ভর নির্ণয় সঠিক ছিল না। সঠিক ভর পরিমাপের জন্য দরকার ছিল ফুলটোন প্লেট। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ওই প্লেট ব্যবহার করতে পারেননি বিভারা। পরবর্তী কালে গবেষকরা জানতে পারেন, বিভারা পায়নের কথা ভেবেছিলেন। সেই পায়ন প্লেটে ধরা দিলেও বিভাদের পরীক্ষায় ভর এক এক রকম আসছিল। ফলে আলাদা করে চিনতে পারেননি তাঁরা। যে কারণে প্রকাশিত প্রবন্ধে পায়নের কথা তাঁরা লেখেননি। পরে ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের সেসিল পাওয়েল ফুলটোন ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করে সাফল্য পান। বিভাদের পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও উন্নত গবেষণা চালিয়ে ১৯৫০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান পাওয়েল। তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে আরও অনেক আবিষ্কার ছিল, তবে বিভাদের অসমাপ্ত কাজও তার মধ্যে ছিল। গবেষকদের মতে, সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে নোবেল পেতেন ডিএম বসুই। কারণ পরিকল্পনাটা ছিল তাঁরই। আর এই নোবেলপ্রাপ্তির সঙ্গেও জুড়ে যেতে পারতো বিভার নামও। তবে, তা না হলেও পদার্থবিদ্যায় বিভার অবদানে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে না।
 ১৯৫৫-তে ইতালিতে আয়োজিত International Conference in Pisa-য় বিভা চৌধুরী। ছবিটি সুকুমার বিশ্বাসের লেখা “Cosmic Quests” বইতে রয়েছে।
১৯৫৫-তে ইতালিতে আয়োজিত International Conference in Pisa-য় বিভা চৌধুরী। ছবিটি সুকুমার বিশ্বাসের লেখা “Cosmic Quests” বইতে রয়েছে।
১৯৪৯ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত টাটা মৌলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিভাকে বাছেন হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। ওই বছর সেখানে যোগ দেন বিভা। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন তিনি। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভিশেন অব সায়েন্সেও গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন বিভা। TIFR বা PRL র আর্কাইভ- এ তাঁর কাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মেলে। তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডক্টরেট অফ সায়েন্স অসীমা চট্টোপাধ্যায় যে তুলনায় দেশে-বিদেশে পরিচিতি পেয়েছিলেন, তার উল্টো পথেই হেঁটেছিলেন বিভা। স্বেচ্ছায় রয়ে গিয়েছিলেন অন্তরালে কিন্তু, ১৯৯১-র ২ জুনে মারা যাওয়ার আগে অবধি গবেষণা জারি রেখেছিলেন।
বিজ্ঞানে বিরল কৃতিত্বের জন্য ২০১৯ সালে বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানী বিভা চৌধুরীকে সম্মান জানাতে প্যারিসের ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন’ তাঁর নামে একটি নক্ষত্রের নাম রাখে। বিভা নামের এই নক্ষত্রটির যে গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেট তার নাম রাখা হয়েছে সংস্কৃত শব্দ সান্তামাসা, যার অর্থ মেঘে ঢাকা। মেঘে ঢাকা প্রকৃতির কারণেই এমন নামকরণ করা হয় গ্রহটির। নক্ষত্রটির আগের নাম ছিল ‘এইচডি ৮৬০৮১’। নক্ষত্রের নামকরণের জন্য সব দেশকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিভা চৌধুরীর নামানুসারে ভারতের দেওয়া ‘বিভা’ নাম অনুমোদন পায়। সত্যিই তো, এর থেকে যোগ্য নাম আর কিই বা হতে পারতো!
তথ্যঋণঃ
প্রথমাঃ বিভা চৌধুরীঃ গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় (ekapornika.blogspot.com)
যে হাতে জ্বলেছিল আলোর শিখা - ডঃ বিভা চৌধুরী, স্বাতী রায় (www.guruchandali.com)
আনন্দবাজার পত্রিকা
www.tifr.res.in