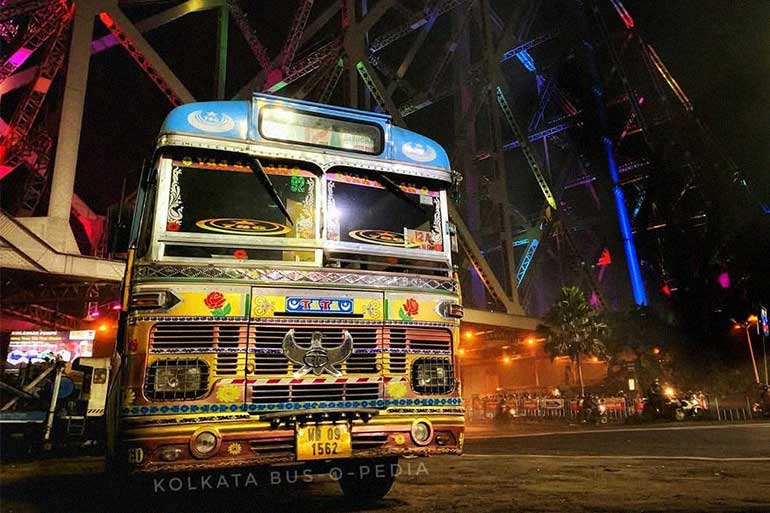যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লি থেকে আজকের বিজয়গড় : উদ্বাস্তু মানুষের স্পর্ধার নাম

ক্যুইজ-এ যদি প্রশ্ন আসে, ‘পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা শহরের প্রথম উদ্বাস্তু কলোনির নাম কী?’ একবাক্যে উত্তর আসবে, ‘বিজয়গড়’। নামটার মধ্যে—স্পর্ধা, লড়াই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আজও...
একটা সময়, মানুষ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতেন, (তাঁদের মাইগ্রেশন হত) উন্নততর জীবন-যাপনের আশায়, বিশ শতকের ‘সভ্য’ সমাজ দেখাল, রাতারাতি কীভাবে জন্মভূমি আলাদা হয়ে যায় রাজনীতির আঁচড়ে।
১৯৪৭-এ দেশভাগ হওয়ার পর, কলকাতা শহরের এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশের ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা মানুষদের প্রথম আশ্রয়। তখন, অঞ্চলের নাম ছিল ‘যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লি’। নিজেদের উদ্যমে, কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের আবাস। ইতিহাসের বয়ানে এগুলি ‘জবরদখল’ করা জমি হলেও এই দখল যেন অধিকারের দখল, ঠিক যে রাজনীতিতে তাঁদের দেশ রাতারাতি আলাদা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তার প্রতি প্রশ্নের স্পর্ধাতেই এই জবরদখলিকৃত জমিগুলি নিয়ে, জঙ্গল সাফ করে নীচু অংশ ভরাট করে তৈরি হল প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ। এই জয়ের সৌধস্বরূপই ‘বাস্তুহারা পল্লি’ নাম বদলে, অঞ্চল হয়ে উঠল— ‘বিজয়গড়’।
 ১৯৪৮ সালে নির্মিত বিজয়গড় বাজার
১৯৪৮ সালে নির্মিত বিজয়গড় বাজার
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এগুলো ছিল সরকারের অধিগ্রহণকরা জমি, এখানে ছিল মার্কিন সেনা ছাউনি; যুদ্ধ শেষে, তাঁদের পরিত্যক্ত কাঠের ঘর, যাতায়াতের জন্য তৈরি হওয়া রাস্তা, খুব সহজেই বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলি। বিজয়গড়কে গড়ে তোলার প্রাণপুরুষ সন্তোষ দত্ত। তিনি ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী, মূলত তাঁর নেতৃত্বেই বাস্তুহারা পল্লি হয়ে উঠেছিল বিজয়গড়। নানা সময় অঞ্চলের নানা অভাব পূরণে ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা। আজও এই অঞ্চলের মানুষ শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করেন, রয়েছে তাঁর নামে একটি কমিউনিটি হলও।
১৯৪৭-এ দেশভাগ হওয়ার পর, কলকাতা শহরের এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশের ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা মানুষদের প্রথম আশ্রয়। তখন, অঞ্চলের নাম ছিল ‘যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লি’। নিজেদের উদ্যমে, কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের আবাস।
কলোনির মূল কাঠামো গড়ে ওঠার সময়টা ১৯৪৮ থেকে ’৫১ সাল। তথ্য বলছে, এবং আজও বিজয়গড় ঘুরে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেল, এঁরা মূলত অর্থনৈতিক ভাবে মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত, প্রায় অধিকাংশই ‘উচ্চবর্ণভুক্ত’। বিজয়গড়-এর শিরোপায় প্রথম কলোনির পাশাপাশি, এ বিশেষণও রয়েছে, বিজয়গড় ছিল ‘ভদ্রলোক’দের কলোনি। অবশ্য কোন-কোন শর্ত পূরণ করলে সমাজ কাউকে ‘ভদ্রলোক’ বলে তা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু, বিজয়গড়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যে অর্থনৈতিক ভাবে বেশ স্বচ্ছল তার প্রমাণ মেলে কলোনি গড়ে ওঠার পাঁচ বছরে মধ্যে এখানে তৈরি হওয়া স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাক্ষে। যদিও শুধু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার সাপেক্ষে এগুলির বিচার করলে হবে না, বিচার্য মানুষের উদ্যম, অনেককিছু হারিয়েও নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস।
 বিজয়গড় ব্যায়ামাগার (বাঁদিকে) এবং জাগরণী ক্লাব (ডানদিকে)
বিজয়গড় ব্যায়ামাগার (বাঁদিকে) এবং জাগরণী ক্লাব (ডানদিকে)
আবার, একটি উদ্বাস্তু কলোনি হওয়া সত্ত্বেও, সদ্য ভিটে মাটি ছেড়েছে যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এহেন উন্নয়ন দৃষ্টান্তস্বরূপ। সে সময়, জওহরলাল নেহরু বিজয়গড় সম্পর্কে বলেছিলেন, “I am delighted to learn of the fine work done here and I congratulate them on it.”
আসলে, এঁদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা শুরু হওয়ার আগে, বাংলাদেশ থেকে টাকা-সহ নানা অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে এদেশে চলে আসেন এবং অনেকেরই কলকাতা শহরে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ফলত, জায়গা নির্বাচনে, শহরে এসে নিজেদের বসতি সাজিয়ে নিতে বাড়তি সুবিধে পেয়েছিলেন তাঁরা, কিছুটা হলেও স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতেন। তবে (১৯৪৮-৫০) প্রথম কয়েকবছর জমি নিয়ে আশঙ্কা ছিলই। আদপে জমি দখল করে তা অধিকারে রাখাই ছিল এঁদের আসল লড়াই। যুদ্ধের সময়, সরকার যাঁদের থেকে জমি নিয়েছিলেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত গুন্ডা বাহিনি পাঠিয়ে এঁদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতেন এদিকে উদ্বাস্তু স্রোত চলছিলই, একইসঙ্গে গড়ে উঠছিল প্রতিরোধের দুর্গ— সেই থেকেই বিজয়গড়। পরে যখন উদ্বাস্তু উচ্ছেদের জন্য এভিকশন বিল এল, লড়াই আরও কঠিন হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গড়ের বিজয় অক্ষুণ্ণ থাকল! সরকারি স্বীকৃতি পেল বিজয়গড়, ভারতবর্ষের নাগরিক হলেন দেশ ছাড়া মানুষগুলো…
বিজয়গড়-এর সংগঠকরা অঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করে এটিকে টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেন শুরুতেই, পাশাপাশি, ১৯৫০-এর মধ্যেই গড়ে উঠল ব্যায়ামাগার।
 বিজয়গড়ের অন্যতম প্রথম প্রাইমারি স্কুল
বিজয়গড়ের অন্যতম প্রথম প্রাইমারি স্কুল
বিজয়গড় কলোনি-র মানুষদের স্বচ্ছলতা, বলা ভালো এদেশে এসেই নিজেদের যাপন গুছিয়ে নেওয়ার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। জ্ঞান ঘোষ বিজয়গড় অঞ্চলের পরিচত নাম, ’৪৮ সালে এঁরা চলে আসেন বাংলাদেশ-এর ফরিদপুর থেকে এবং সেই থেকে আজও এঁদের বাড়িতে পূর্বপুরুষের দুর্গাপুজো চলে আসছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পুজো এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আজও বহমান। কতটা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকলে দেশভাগের পরপরই অন্যদেশে এসে পুজো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! জ্ঞান ঘোষ-এর বাড়ির বিরাট জমির একাংশ আজ প্রোমোটিং হয়ে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ির একপাশে আজও রয়েছে পুরোনো টিনের চালা যেখানে বর্তমানে পুজো চালিয়ে নিয়ে যান তাঁর পুত্রবধূ মঞ্জু ঘোষ; আবার, একপাশে সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের টিনের ছাউনি দেওয়া দ্বিতল একটি বাড়ি। একইসঙ্গে উল্লেখ্য, বিজয়গড় অঞ্চলে, অধুনালুপ্ত বাদল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছেই, ফরিদপুর-এর কুনিয়া অঞ্চল থেকে আসা ধর বাড়ির পুজো। এঁরাও এদেশে আসার পর একবারও পুজো বন্ধ করেননি, প্রায় ২৯৪ বছরের পুজো এই পরিবারের।
বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনি হলেও এহেন উন্নতির পেছনে ছিল সঠিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন। কোনো অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠলে সেখানে প্রথমেই গড়ে ওঠে বাজার। অঞ্চলের প্রথমদিকের সৌধগুলির তালিকা করলে বাজার তার মধ্যে একটি। বাজার সংলগ্ন একটি মন্দিরও রয়েছে।
বিজয়গড় ও আজাদগড় কলোনির সীমান্তে থাকা দীপঙ্কর পাল চৌধুরী বললেন, “বাজার ছাড়াও, উদ্বাস্তু পরিবার নির্মিত প্রথম সৌধগুলির মধ্যে অঞ্চলের ক্লাবগুলিকেও ধরতে হবে। কারুর কোনো সমস্যা হলে ক্লাবেই সকলে এসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতেন।” একতাই ছিল ক্লাবগুলির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্লাবগুলির নামেও সেই ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। যেমন: জাগরণী ক্লাব, যার প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮-এ।
 সন্তোষ দত্ত নামাঙ্কিত কমিউনিটি হল-এর দিকনির্দেশ
সন্তোষ দত্ত নামাঙ্কিত কমিউনিটি হল-এর দিকনির্দেশ
বিজয়গড়কে রক্ষা করার জন্য কলেজ, হাসপাতাল, বাজার, মন্দির, প্রাথমিক স্কুল— এমন অনেক নির্মাণের সাক্ষী এই ক্লাবগুলো। এর প্রায় সমসময়ে, কখনও কিছু পরে নির্মিত ‘অগ্রগামী’, ‘কালচারাল এসোসিয়েশন’ সময়ের স্মারক হিসেবে এখনও উজ্জ্বল। প্রসঙ্গত, দীপঙ্করবাবুর পরিবারও দেশভাগের পর এখানে উঠে আসেন, এবং এখানে এসে মাত্র ৬-৭ মাসের ব্যবধানে, তাঁর বাবা-কাকারা পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা শুরু করেন।
বিজয়গড়-এর সংগঠকরা অঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করে এটিকে টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেন শুরুতেই, পাশাপাশি, ১৯৫০-এর মধ্যেই গড়ে উঠল ব্যায়ামাগার। তাঁরা এ-ও উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু বসতি গড়লেই হবে না, নিশ্চিত করতে হবে, তাঁদের উত্তর প্রজন্মের শিক্ষাও। তাই ১৯৪৯-এ গড়ে উঠল, বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ, (যার বর্তমান পরিবর্তিত রূপ বিজয়গড় আদর্শ বিদ্যালয়), অনেক প্রাইমারি স্কুলও পরপর গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ‘শিশুর দেশ’(১৯৫৩) — এই স্কুল বর্তমানে চালান, অঞ্জন চক্রবর্তীর পরিবার, তাঁরাও বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন, তাঁর বাবা অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ছিলেন বিজয়গড় কলেজের অধ্যক্ষ। অঞ্জনবাবু আবার কলকাতা অঞ্চলের অন্যতম ‘বিবলিওফিল’ (বইপোকা) তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ৩৫ হাজারেরও বেশি বই।
 জ্ঞান ঘোষের মন্দির
জ্ঞান ঘোষের মন্দির
বিজয়গড় কলেজই বর্তমানে জ্যোতিষ রায় কলেজ নামে পরিচিত। কলেজটির বর্তমান অবস্থানে মিলিটারিদের একটি টিনের ছাউনি দেওয়া ব্যারাক ছিল, সেখানেই গড়ে ওঠে কলেজের প্রাথমিক রূপ। অবিশ্বাস্য হলেও, মাত্র ১০ আনা সম্বল করে শুরু হয়েছিল এই কলেজের পথ চলা। মেঝেতে কাগজ পেতে চলত কলেজের ক্লাস, চেয়ার টেবিল কেনার সামর্থ্য ছিল না কমিটির। মাস্টার্স ডিগ্রিধারী নানা মানুষ নিজেদের চাকরি সামলে এই কলেজে ক্লাস নিতেন স্বল্প বেতনে। এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করার জন্য দরকার হয়েছিল ২০ হাজার টাকা। নানা মানুষ সাহায্য করেছিলেন সে সময়। তবু সব টাকা ওঠেনি। অবশেষে জনৈক কাঠ ব্যবসায়ী রায় পরিবার ২০ হাজার টাকা ও কিছু চেয়ার টেবিল দান করেন কিন্তু শর্ত দেন, কলেজের নাম বদলে রাখতে হবে ‘জ্যোতিষ রায় কলেজ বিজয়গড়’। এদিকে স্থানীয় মানুষের কাছে বিজয়গড় আবেগ, তাঁদের লড়াইয়ের চিহ্ন! তারা বলেন, বিজয়গড় শব্দটাই আগে রাখতে হবে। অবশেষে কলেজের নাম হয়, ‘বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ’। মজার ব্যাপার এখনও কিন্তু এই কলেজকে মানুষে বিজয়গড় কলেজ নামই বেশি চেনেন।
বসতি গড়ে ওঠার স্বাভাবিক নিয়মেই এখানে তৈরি হল, বিজয়গড় ঠাকুর বাড়ি। কিন্তু এই ঠাকুর বাড়ি নানা মত সমন্বয়ের নিদর্শন, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের মধ্যে ছিলেন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব এমন নানা ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষজন, তাই ঠাকুরবাড়ি তৈরির সময়তেও একটি ছাদের তলায় রইল আলাদা-আলাদা মতে বিশ্বাসী মানুষের আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্তি। এখানেও কী আশ্চর্য একতার পরিচয়!
 ১৯৫০ সালের বিজয়গড় কলেজ - এটাই ছিল সেই মিলিটারি ব্যারাক (ছবি ঋণ: দেবদত্ত গুপ্ত/ বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ)
১৯৫০ সালের বিজয়গড় কলেজ - এটাই ছিল সেই মিলিটারি ব্যারাক (ছবি ঋণ: দেবদত্ত গুপ্ত/ বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ)
বিজয়গড় অঞ্চলে কিন্তু শুধু দেশভাগের সময়তেই মানুষের আগমন ঘটেনি, সত্তরের দশকে মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরেও, বহু মানুষ এসে বিজয়গড়ে নিজেদের আবাস গড়ে তুলেছেন। যেমন বিজয়গড় সাধারণ গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান নমিতা গুহ (মিত্র) বললেন, তাঁরা সত্তরের দশকের শেষে মুক্তিযুদ্ধের আগেই অস্থির পরিস্থিতি এড়াতে টাঙ্গাইল থেকে এদেশে চলে আসেন। তিনি বলেন, “আমার বয়স তখন সাত, আমাদের পাসপোর্ট অ্যাপ্রুভ হয়নি, কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে পালিয়ে আসতে বাধ্য হই! রাতের অন্ধকারে, চোরের মতো। তবে এ-ও ঠিক, আমাদের আতঙ্ক ছিল বেশি, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শান্তিই ছিল তুলনামূলক ভাবে, তবুও পালিয়ে আসার মূলে ছিল ভয়, রাতের অন্ধকারেই আমরা নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়েছিলাম, এক রাতেই আমাদের দেশ আলাদা হয়ে গেল।”
বিজয়গড়-এর অলিতে-গলিতে এমন অনেক গল্প ছড়িয়ে রয়েছে, যা যন্ত্রণার এবং একইসঙ্গে হার না মেনে, নতুন করে বাঁচার কথা শেখায়, এই গল্পগুলোর অনেক দলিল আজ আর নেই, কিন্তু যা রয়েছে তা এই অঞ্চলটির বর্তমান চেহারা, যেখানে বাজার থেকে শুরু করে রয়েছে বিদ্যায়তন যা নির্মাণে সেই উদ্বাস্তু ঘরছাড়া মানুষগুলোর সংগ্রাম আজও বিজয়গড়-এর ইট-কাঠ-পাথর স্মরণ করে…