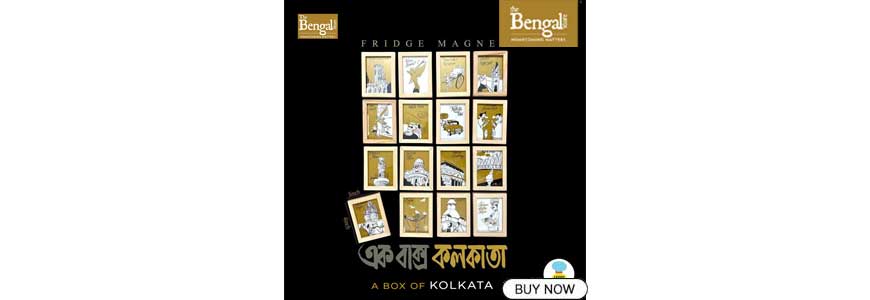রাজেন তরফদার : বাংলা সিনেমার এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই সময়ের দাবী মেনে সমাজ রাজনীতির চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্য। কিন্তু তখনও এই চেতনা সেভাবে উন্মোচিত হয়নি বাংলা সিনেমায়, হয়েছিল বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। বাংলা সিনেমা সম্পর্কে নতুন ভাবনার সূত্রপাত হয় এক ঝাঁক তরুণের উদ্যোগে। কলকাতায় শুরু হয় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। এই আন্দোলন থেকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে উঠে এসেছিলেন একজন রাজেন তরফদারও।
চলচিত্রবেত্তা অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখা এক্ষেত্রে মনে পড়ে যেতে বাধ্য, যেখানে তিনি উল্লেখ করছেন, ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চারটি চলচ্চিত্রের নাম, বাংলা ছবির ইতিহাসে যাদের অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি। সত্যজিৎ রায় কৃত ‘দেবী’, ঋত্বিক কুমার ঘটক কৃত ‘মেঘে ঢাকা তারা’, মৃণাল সেন কৃত ‘বাইশে শ্রাবণ’ ও রাজেন তরফদার কৃত ‘গঙ্গা’। তাই যদি হয়, সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিকের সমতুল ভাবে শেষের ব্যক্তিটি আলোচিত হলেন না কেন?
বাংলাদেশের বরেণ্য পরিচালক তারেক মাসুদ তখনও বোঝে ওঠেননি সিনেমা বিষয়টা ঠিক কী। তখন তিনি সত্তরের দশকের সাহিত্যমনস্ক যুবা। সেসময় সিনেমাকে খানিক খাটো করেই দেখতেন। সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পাল্টে গিয়েছিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ (বিএফএস) আয়োজিত একটি মার্কিন প্রামাণ্যচিত্র দেখার মধ্য দিয়ে। এইরকম একটা সময়ে তিনি দেখে ফেলেছিলেন রাজেন তরফদার নির্মিত ‘পালঙ্ক’। তারেক মাসুদ তাঁর ‘চলচ্চিত্রযাত্রা’ বইটিতে লিখেছেন, “মূল গল্পটির লেখক নরেন মিত্র (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) কেবল যে আমার প্রতিবেশী গ্রামের মানুষ ছিলেন, তা-ই নয়, গল্পটি আমার পরিচিত একটি পরিবার ও গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে দেশে তখন সামরিক শাসন চলছে। সেন্সর বোর্ড পালঙ্ক ছবিটির মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়-সংশ্লিষ্ট রঙিন অংশটুকু কেটে বাদ দিল। জবাই করে রক্তাক্ত করল প্রধানত সাদা-কালোতে নির্মিত রাজনৈতিকভাবে নিরীহ ছবিটিকে। সম্পাদক সেন্সর বোর্ডের কল্যাণে পৃথক ‘পালঙ্ক’ একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলাম। ব্যস, ফেঁসে গেলাম।”
তাঁকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ মুহম্মদ খসরু (‘পালঙ্ক’ ছবিতে রাজেন তরফদারের সহকারী ছিলেন)। একটি আড্ডায় পালঙ্ক সম্বন্ধে মাসুদ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরায়, তাঁর খসরু ভাই ফরমান জারি করেছিলেন, আড্ডায় পালঙ্ক সম্বন্ধে যা যা বলেছেন, তা লিখে জমা দিতে। কুণ্ঠিত ভাব নিয়েই একটি লেখা তিনি জমা দিয়েছিলেন। যা চলচ্চিত্র সংসদের নিয়মিত বুলেটিনে প্রকাশিত হয়।
শ্যাম বেনেগাল বলেছেন, “রাজেন তরফদার হলেন জিনিয়াস পরিচালক”। সে তুলনায় মর্যাদা বা স্বীকৃতি তিনি পাননি।

‘পালঙ্ক’ দেশভাগ, পূর্ববাংলা, অধুনা বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আখ্যান। একটি পালঙ্ক ঘিরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আসে বাঙালি মূল্যবোধ। সমরেশ বসুর কলম থেকে মাছমারাদের জীবন, আত্মহত্যা-প্রবণ এক বৃদ্ধকে জীবনে টেনে আনার গল্প কিংবা একটি পালঙ্ককে ঘিরে টানাপড়েন। ভারত বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হলো এই সিনেমা। শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করল ‘পালঙ্ক' (১৯৭৫)। অথচ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রাজেন তরফদার সে ভাবে আলোচিত হলেন না।
জন্ম ৭ই জুন, ১৯১৭ রাজশাহী বাংলাদেশে। সেখানেই ছোটোবেলা এবং স্কুলজীবন কেটেছে রাজেনবাবুর। দুই বাংলা তাঁর কাছে এক। বাংলার মাটি তাঁর মা। সেই মায়ের যাবতীয় রক্তপাত, দুঃখ, দুর্দশা, ভালো-মন্দের অংশীদার তিনিও। ১৯৪০-এ কলকাতায় গভর্মেন্ট আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরবর্তীকালে কর্মজীবন শুরু করেন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বিজ্ঞাপন সংস্থা ডে ওয়াল্টার টমসন-এ। আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। বিজ্ঞাপন জগৎ, নাটকের মঞ্চ পেরিয়ে সিনেমার জগতে আসা ১৯৫৭-য়। নাটক থেকেই আস্তে আস্তে শিখেছিলেন সবাইকে নিয়ে অভিনয় কন্ট্রোল করতে হয় কীভাবে। তাঁর ছেলে গৌর তরফদারের কথা থেকেই জানা যায় রাজেনবাবু যখন ছোটো তখন যাত্রা, পালাগান ইত্যাদির প্রচলন ছিল, স্কুলজীবনে যা আকৃষ্ট করতো তাঁকে। হয়তো সেই অনুসঙ্গই হয়ে উঠেছিল তাঁর ফর্ম—ঋত্বিক ঘটকের মতো রাজেন তরফদারও মেলোড্রামাকে ফর্ম হিসেবে ধারণ করেছিলেন। “ঋত্বিক ঘটকের মতো রাজেনবাবুও বাঙালির অখণ্ড চৈতন্যে বিশ্বাসী ছিলেন” বলেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
ছবি তৈরির পাশাপাশি রাজেন তরফদার অভিনয় করেছেন মৃণাল সেনের ‘খণ্ডহর’, ‘আকালের সন্ধানে’, শ্যাম বেনেগাল এর ‘আরোহন’, শেখর চট্টোপাধ্যায় এর ‘বসুন্ধরা’ সিনেমায়।
১৯৫৭ থেকে ১৯৮৭, তিন দশকে সিনেমা করেছেন মাত্র সাতটি। ওই সাতটি ছবিতেই রাজেনবাবু যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৫১-য় জাঁ রেনোয়ার ‘দ্য রিভার’-ই তাঁকে ছবি নির্মাণে আকৃষ্ট করেছিল। ইতালির নয়া বাস্তবতা রাজেন তরফদারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর প্রথম ছবি ‘অন্তরীক্ষ’ (১৯৫৭)। কাহিনিকার তুলসী লাহিড়ী। সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল ছবিটি। ১৯৬০ সালে সমরেশ বসুর কাহিনি নিয়ে তৈরি হলো ‘গঙ্গা’। রাজেনবাবু কৃত এই ছবিটিই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এবং প্রচার পেয়েছে। মৎস্যজীবি সম্প্রদায়কে নিয়ে এই সিনেমা। অভিনয় করেছেন নিরঞ্জন রায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতা। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী। ছবিটি সমালোচকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৬১ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছিল ‘গঙ্গা’। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসেবে ‘গঙ্গা' জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। এই ছবির গান “আমায় ডুবাইলিরে, আমায় ভাসাইলিরে” (মান্না দে) আজও শোনা যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনি নিয়ে এরপর ছবি করলেন ‘অগ্নিশিখা'(১৯৬২)। এই সিনেমা একজন সৎ শিল্পী হিসেবে রাজেন তরফদারকে বাংলা ছবিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।
আত্মহত্যা প্রবণ এক বৃদ্ধকে জীবনে টেনে আনার গল্প শোনালেন ‘জীবন কাহিনী'(১৯৬৪) ছবিতে। সিরিও-কমিক এর আঙ্গিকে একটি অসাধারণ নিবেদন এই ছবি। দুরন্ত অভিনয় করলেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায় এবং অনুপ কুমার। এই ধরনের ছবি বাংলা ছবিতে বিশেষ দেখা যায়নি।
১৯৬৭-তে তৈরি হলো ‘আকাশ ছোঁয়া’। এই ছবির মূল কেন্দ্রে ছিল সার্কাস। এমন অভূতপূর্ব বিষয় নিয়েও বাংলা সিনেমা তৈরি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সুপ্রিয়া চৌধুরী-র অভিনয়ে ধন্য এই সিনেমা।
১৯৭৫-এ পালঙ্ক-এর পর তাঁর শেষ ছবি ‘নাগপাশ'(১৯৮৭) এর শুটিং হয়েছিল সুন্দরবনের গোসাবায়। সাধন চট্টোপাধ্যায় এর সমকালের রাজনীতি নিয়ে লেখার উপর ভিত্তি করে এই সিনেমা।
ছবি তৈরির পাশাপাশি রাজেন তরফদার অভিনয় করেছেন মৃণাল সেনের ‘খণ্ডহর’, ‘আকালের সন্ধানে’, শ্যাম বেনেগাল এর ‘আরোহন’, শেখর চট্টোপাধ্যায় এর ‘বসুন্ধরা’ সিনেমায়। তিনি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তরুণ মজুমদারের ‘গণদেবতা’ এবং ‘সংসার সীমান্তে’-র। শ্যাম বেনেগাল বলেছেন, “রাজেন তরফদার হলেন জিনিয়াস পরিচালক”। কিন্তু সে তুলনায় মর্যাদা বা স্বীকৃতি তিনি পাননি।

আকালের সন্ধানে ছবিতে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজেন তরফদার
সবার চোখের আড়ালে ১৯৮৭-র ২৩ নভেম্বর প্রয়াত হন এই ব্যতিক্রমী স্রষ্টা। অবহেলায় পড়ে থাকে তাঁর সৃষ্টি। আমাদের অদূরদর্শিতায় নষ্ট হয়ে যায় তাঁর অধিকাংশ ছবির প্রিন্ট। “ইচ্ছা করে, ও পরানডারে, গামছা দিয়া বান্ধি”—‘গঙ্গা’ সিনেমার এই গানটি আকাশে বাতাসে ভাসতে থাকে কিন্তু, আমরা তাঁর ছবিগুলিকে হৃদয় দিয়ে বেঁধে রাখতে পেরেছি কি?
পারিনি, ডাঁহা ফেল করেছি। তাই-ই তো বছর কয়েক আগে অনাড়ম্বরে কেটে যায় রাজেন তরফদারের জন্ম শতবর্ষ।
ভারতীয় তথা বাংলা সিনেমায় সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের পাশে অদৃশ্য একটা আসন পাতা রয়েছে তাঁর জন্যেও। একথা আমরা ভুলে গেলেও ইতিহাস সহজাত ভাবে মনে রেখে দেবে।
তথ্যঋণঃ
চলচ্চিত্রযাত্রা, তারেক মাসুদ
তপন মল্লিক চৌধুরী
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
ইমানুল হক
গোরা তরফদার-এর সাক্ষাৎকার (সিনেমা মেমরি প্রোজেক্ট, Cinemaazi TV)