বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ হীরালাল সেন
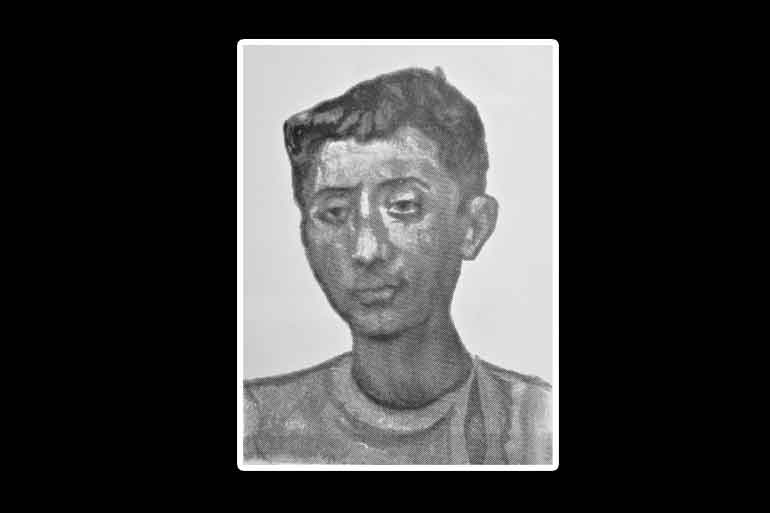
কৃ ষ্ণ বি স্মৃ তি স মী পে
মনে রেখেছিলাম সেপ্টেম্বর শেষের দুর্গাপূজা, পয়লা অক্টোবরের মহরম। দানবীয় ধুমধামে পালনও করলাম আমরা। মনে রাখি বিদ্যাসাগর, গান্ধি, রাসমণি, ভগৎ সিং-এর জন্মদিন। পূর্ণবৃত্ত চন্দ্ররাতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শঙ্খধ্বনি সহযোগে উদযাপিত হয়েছে এই সেদিন। ছ-তারিখ মেঘনাদ সাহার জন্মদিন কতিপয় বাঙালি জানে। বুনুয়েল তারকোভস্কি উত্তমকুমার সত্যজিতের জন্মদিন-মৃত্যুদিন, আমরা সংস্কৃতি সচেতন বাঙালিরা খেয়াল রাখি। এসব ব্যাপারে আমাদের একটা ঐতিহ্য আছে - যার অপর নাম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য! যমচতুর্দশী - চোদ্দ শাক, চোদ্দ প্রদীপ এমনকি ভূত প্রদীপও হল। এই লেখা তৈরি করছি পয়লা কার্ত্তিক কালিপুজো তথা দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজার রাতে। চারদিকে আলোর ঝরনা। একুশে ভাইফোঁটা তাও মনে রেখেছি নিখুঁতভাবে। বাড়ির ছাদে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো শুরু হল আজ থেকে কেননা আমরা নাকি স্বর্গে বাতি দিই! প্রয়াত আত্মাদের আলো দেখাই!
 আলিবাবা । নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমারী
আলিবাবা । নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমারীবাজে কথা! আমরা মনে রাখি না!
মনে রাখিনি!
মৃ ত্যু শ ত ব র্ষ
আজ্ঞে! আমরা মনে রাখিনি যে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ হীরালাল সেনের মৃত্যুদিন। এবং শততম!
কোনো পাঁজি, কোনো চলচ্চিত্র ক্যালেন্ডার, কোনো সরকারি সিলমোহর, কোনো পাঠ্যপুস্তক এমনকি কোনো ফিল্ম অধ্যাপকের লেকচার নোটেও তিনি নেই, থাকেন না। ১০-১৮ নভেম্বর কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসবের গর্ব-উঠান নন্দন জমজমিয়ে জমাট হবে, কালচারে ঝলসাবে, আমরা আবারও প্রমাণ করব আমাদের বঙ্গীয় কৃষ্টিকে। কিন্তু বাংলা সিনেমার জন্মশতবর্ষ ( ১৪ মার্চ ১৯১৭) আর হীরালাল সেনের মৃত্যুশতবর্ষ এই একই বছরে মাত্র সাত মাসের ফারাকে হয়ে গেল, হয়ে যাচ্ছে। আমরা খেয়াল করিনি। আমরা মনে রাখিনি। এটা লজ্জার। এ-ব্যাপারে বাঙলা ভাষাভাষী হিন্দু মুসলমানের কী অভূতপূর্ব মিল! ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি হিসেবে আমাদের খ্যাতি আছে বটে, তা-বলে শতবর্ষ কেটে গেলেও উচ্চবাচ হবে না!
একটি সেলুকাসীয় বিস্ময় চিহ্ন দরকার এখানে!
আমাদের ধোঁকা লাগে, যখন সত্যজিৎ বলেন - ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য থেকে তিনি কিছুই নেননি। আমাদের হাঁ-মুখ বন্ধ হয় না যখন মৃণাল সেন বলেন, ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে তথ্য আহরণ তাঁর প্রিয় কর্মের মধ্যে পড়ে না। কেবল এক জন ঋত্বিককুমার ঘটক আমাদের মাটিতে ফিরিয়ে দেন, যখন বলেন, শিল্পকলাকে হতে হবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী। জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কোনো শিল্পী যদি অনুপ্রবেশ না করেন তা হলে জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না...

এক-শো বছর আগের সেদিন
৺বিজয়া দশমীর রাত। বৃহস্পতিবার। পাঁজি বলছে, দশমী ছিল সন্ধ্যে ৫-৩৬ পর্যন্ত। পরদিন শুক্রবার, একাদশী তিথির ভোররাতে চলে গেলেন হীরালাল সেন। ইংরেজি ২৬ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে, বাংলা ৮ কার্ত্তিক ১৩২৪। আজ থেকে ১০০ বছর আগে। মৃত্যুকালে ছোটোবেলার বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যু ঘটে ১৮ নং, ব্ল্যাকি স্কোয়ারের বাড়িতে এবং এখানেই শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়েছিল। স্টার থিয়েটার ছাড়িয়ে হেদুয়ার দিকে যেতে ডানহাতে পাবেন নেতাজী নামাঙ্কিত একটি বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান। পাশ গলি দিয়ে এগোলে পড়বে হরি ঘোষ স্ট্রিট। সেখানে ননীলাল ঘোষের মিষ্টির দোকানের পাশের গলি দিয়ে গেলে যে পার্কটি পাবেন সেটিই ব্ল্যাকি স্কোয়ার ( অধুনা সাধক রামপ্রসাদ উদ্যান)।

মৃত্যু হয়েছিল ক্যান্সারে। কিন্তু সে তো চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা । ডেথ সার্টিফিকেটে যা ছিল না সেটা জানা দরকার বইকি । মৃত্যুর চার বছর আগে(১৯১৩) পরিবারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় । হরিতকী বাগান লেনের বাড়ি ছেড়ে দু-ভাই গেলেন দু-জায়গায় । দু-ভাইয়ের ঝগড়া যে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কত বড়ো সর্বনাশ করেছিল তা হীরালাল-পড়ুয়া ও গবেষক মাত্রই ওয়াকিবহাল আছেন। হীরালাল উঠে আসেন ১৮ নং ব্ল্যাকি স্কোয়ারের এই বাড়িতে। ভাই মতিলাল উঠে যান রায়বাগানের ভাড়াবাড়িতে, যার নীচ তলার গুদাম ঘরে থাকত রয়াল বায়োস্কোপ কম্পানি( হীরালাল সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম সিনেমা কম্পানি) ও প্যাথে কম্পানির চলচ্চিত্র সরঞ্জাম অর্থাৎ ওই গুদামেই ছিল হীরালালের সারা জীবনের যাবতীয় ফিল্ম ও ফোটোগ্রাফ, বলা ভালো, বাংলা-তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রামাণ্য নথি বা দলিলসমূহ(প্রিন্ট রিল স্টিল নেগেটিভ ইত্যাদি)। পুরোটাই সহজদাহ্য পদার্থে ভরা ঘর। ১৯১৭ সালের ২৪ অক্টোবর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় হীরালালের প্রাণাধিক প্রিয় ভাইঝি অমিয়বালাকে (মতিলালের বড়ো মেয়ে) চারদিক থেকে আগুন ঘিরে ধরে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে নবমীর রাতে চলে গেল ভাইঝি। নীচের গুদামে তখনও জ্বলছে হীরালালের সারাজীবনের কাজ অথবা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস। এর ঠিক দুদিন বাদে চলে যান ভারতীয় তথা বঙ্গীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পুরুষ হীরালাল সেন।
 হীরালালের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী
হীরালালের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীএ বছর ২০১৭ সালে ২৬ অক্টোবর পড়েছে বৃহস্পতিবার। আমরা উত্তরপুরুষেরা ;কি তাঁকে স্মরণের জন্য প্রস্তুত আছি?
সা র্ধ শ ত ব র্ষ
মাইকেল মধুসূদন কলকাতায় ফিরেছেন, দ্বারকানাথ মিত্র জাঁকিয়ে বসেছেন কলকাতা হাইকোর্টের জজের পদে, শিয়ালদায় ক্যাম্বেল হাসপাতাল(এন আর এস)শুরু হয়েছে বছরখানেক আগে। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে শিশির কুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা বের করে ফেলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভরতি হচ্ছেন, বাগবাজারে নবীন চন্দ্র দাস রসগোল্লার দোকান খুলছেন― ঠিক এরকম এক সময় জন্ম হল ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পুরুষ হীরলাল সেনের। এখন তাঁর সার্ধশতবর্ষ চলছে।
১৮৬৮ সালের ২ আগস্ট(১৯ শ্রাবণ ১২৭৫) শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন, অখণ্ড ভারতবর্ষের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরি গ্রামে হীরালাল সেনের জন্ম। বাবা– চন্দ্রমোহন, মা– বিধুমুখী। ঠাকুর্দা –গোকুলকৃষ্ণ সেন মুনশি। দাদু – শ্যামচাঁদ। দিদিমা – ব্রহ্মময়ী। ছোটোপিসি রূপলতার সঙ্গে বিয়ে হয় ঈশ্বরচন্দ্র সেনের আর তাঁদের সন্তানই হলেন আচার্য, লেখক ও সাহিত্যিক ড. দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্রের লেখা ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য–ই হল হীরালালের ছোটোবেলা সম্পর্কে আকর গ্রন্থ। দীনেশ লিখছেন, “বগজুরীর মাতুলালয় ছিল অতি প্রকাণ্ড, খুব বড় কোন রাজবাড়ীর মত। বাড়ীটি ৩০|৪০ বিঘা জমি লইয়া তন্মধ্যে প্রায় ৪/৫ বিঘা শুধু ফুলবাগানই ছিল।” (পৃ. ৮৪, প্রকাশক –জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় মুদ্রণ –জৈষ্ঠ্য ১৩৬৯, বানান অবিকৃত)। ২০১৫ সালে এপার বাংলার বিখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজকর্মী বাসুদেব মণ্ডল গেছিলেন হীরলালের জন্মভিটেতে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, “বাড়িটি খুবই নীচু জমির ওপর ছিল কেননা মূল রাস্তা থেকে নেমে বাঁধের মতো পথ ধরে পায়ে হেঁটে যেতে হয় সেখানে। দুধারে নীচু জমি। ইতস্তত কিছু হতদরিদ্র মানুষের বসতি দুপাশেই। পাটকাটি, হোগলা পাতা চ্যাঁচাড়ির ঘরবাড়ি। মূল ফটক যেখানে ছিল, সেখানে এখন কিছুই নেই। সরকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করেছে সেখানে। সেটা চালুও আছে আর জমির পরিমাণ খুব বেশি হলে ১০ বিঘা মতো হবে। বাড়িটি যেখানে ছিল সেখানে একটু উঁচু চাতাল মতো আছে কিন্তু কোনো ইঁট কাঠের চিহ্ন নেই। ওই রাস্তার বাম দিকে গাছপালার আড়ালে জঙ্গলাকীর্ণ একটি মন্দির আছে। ব্যাস।”
 হীরালাল সেন ব্যবহৃত মাউন্টবোর্ডের পিছনের ছবি
হীরালাল সেন ব্যবহৃত মাউন্টবোর্ডের পিছনের ছবিস্ম র্ত ব্য
এটা যে বঙ্গ চলচ্চিত্রের শতবর্ষ তা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম বছর শুরু হতেই যে বিগত শতকের ২৪ মার্চ ১৯১৭ শনিবার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাংলা নির্বাক কাহিনিচিত্রটি ময়দানের নতুন তাঁবুতে সন্ধ্যে ৬-১৫ ও রাত ৯-৩০-এর দুটি শো-এ দেখানো হয়। লেখাটি ২১ জানুয়ারি ২০১৭ প্রকাশিত হয়, এই বঙ্গদর্শন-এর পাঠ পরিসরেই, সেটা এখানেই আছে বাংলা সিনেমার শতবর্ষ শিরোনামায়। শ্রদ্ধেয় পাঠককে বলব দেখে নিতে। এরপর ১০ মার্চ বাংলা সিনেমা নিয়ে বঙ্গে বায়োস্কোপ বিষয়ে অপর একটি লেখায় দুর্ভিক্ষ প্লেগ মহামারী এবং শিরোনামায় একথা প্রমাণ করা গেছিল যে ফিল্ম স্ক্রিনিং-এর ক্ষেত্রে কলকাতা বম্বের থেকে মাত্র দু-মাস পিছিয়ে ছিল । সেই লেখাটিও এখানে আঙুল নাড়ালে পাওয়া যাবে । তো ওই লেখাটি যেখানে শেষ হচ্ছে এই লেখাটি সেই সময়বিন্দুকে কেন্দ্র করেই বৃত্তসম্ভবা...
 ভ্রমর ( অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারী
ভ্রমর ( অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারীপ্রথম পুরুষ ॥
১ম– ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক নিয়ে ছায়াছবি আলিবাবা মুক্তি পায় ২৩ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে। প্রায় দু-ঘণ্টার ছবি। যদিও সিকোয়েলের মতো করে আলাদা আলাদা স্ক্রিনিং করা শুরু হয়েছিল ১৯০০ সালে। উল্লেখ থাকুক দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি রিলিজ করে ১৯০৩ সালে এবং বিশ্বের প্রথম কাহিনিচিত্র হিসেবে খ্যাত। কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে এটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। ভ্রমর হীরালালের প্রথম ছবি হলেও সেটির সন তারিখের নথি না-পাওয়ায় অনুল্লেখিত রইল।
২য় –প্রথম বিজ্ঞাপন চিত্র ( ১৯০৩) ( ভারতে, সম্ভবত বিশ্বে )
৩য় –প্রথম রাজনৈতিক তথ্যচিত্র (১৯০৫) ( ভারতে, সম্ভবত বিশ্বে)
৪র্থ – প্রথম রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ তথ্যচিত্র (১৯০৫) ( ভারতে, সম্ভবত বিশ্বে )
৫ম – প্রথম সবাক চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ প্রচেষ্টা ( ১৯০৫ , টাউন হল )
৬ষ্ঠ– প্রথম তথ্যচিত্র ( ১৯০৫) ( ভারতে, সম্ভবত বিশ্বে )
৭ম- প্রথম রঙিন চলচ্চিত্রের স্রষ্টা ( সেলুলয়েডে রঙ লাগিয়ে ১৯০০ সালে )
৮ম- প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্র প্রদর্শক ( রয়্যাল বায়োস্কোপ কম্পানি, ১৮৯৮)
৯ম- প্রথম বাঙালি ল্যাব টেকনিশায়ান ( ১৯০০)
১০ম- প্রথম বাঙালি ফিল্ম ডেভেলপার ( ১৯০০)
১১তম –প্রথম ভারতীয় স্বর্ণপদক জয়ী স্থিরচিত্রগ্রাহক (১৮৯৮)
১২তম- প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শক ( ভারত শিল্প প্রদর্শনী, ১৯০০ সাল, রয়াল বায়োস্কোপ কম্পানি )
** সব কটি সম্পর্কে বিশদ টীকাভাষ্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখনে শব্দসীমা বিবেচনা করে সেসব থেকে বিরত রইলাম।
হী রা লা ল সে ন চ ল চ্চি ত্র প ঞ্জি :
কা হি নি চি ত্র : ১) ভ্রমর ; ২) আলিবাবা ৩) হরিরাজ ; ৪) দোল লীলা ; ৫) সরলা ; ৬) বুদ্ধ ; ৭) সীতারাম ।
( ১৯০০-১৯০১ সময়সীমায় তোলা এই ছবিগুলির দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ১৫০ ফিট পর্যন্ত)
৮) দুটি প্রাণ ; ৯) মৃণালিনী ; ১০) সোনার স্বপন ; ১১) মনের মতন ; ১২) মজা ; ১৩) বধু ;
(১৯০২- ১৯০৫ সময়সীমায় তোলা এই ছবিগুলির দৈর্ঘ্য ২০০ থেকে ৩০০ ফিট পর্যন্ত - বিদেশ থেকে ক্যামেরা এনে নতুন ক্যামেরায় তোলা)
১৪) চাবুক ; ১৫) গুপ্তকথা ; ১৬) ফটিকজল ; ১৭) দলিতা ফনিনী (১৯০৩-১৯০৫ সময়সীমায় তোলা ছায়াছবি )
সং বা দ চি ত্র : ১৮) করোনেশন দরবার -দিল্লি (১৯০৩) ; ১৯) করোনেশন দরবার -কলকাতা ( ১৯০৩) ; ২০) গ্র্যান্ড প্যাট্রিওটিক ফিল্ম; (১৯০৫) ; ২১) সুরেন্দ্রনাথের শোভাযাত্রা (১৯০৫) ; ২২) দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র ( ১ম) ( ১৯১১-১২) ; ২৩) দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র ( ২য়) ( ১৯১১-১২) ; ২৪) দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র (৩য়) ( ১৯১১-১২) ; ২৫) দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র (৪র্থ) ( ১৯১১-১২) ; ২৬)দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র ( ৫ম) ( ১৯১১-১২) ; ২৭) দিল্লি কলকাতার দরবার চিত্র (৬ষ্ঠ) ( ১৯১১-১২)
ত থ্য চি ত্র : ২৮) পথের ছবি ; ২৯) গঙ্গার ঘাটের ছবি ; ৩০) প্যাথে নৃত্য দৃশ্য ; ৩১ ) প্যাথে ছবি ( গুচ্ছ) ( ১৯০০ সালে তোলা ) ; ৩২) চিৎপুর রোডে চলমান দৃশ্য; (১৯০০- ১৯০১ সময়সীমায় তোলা ছায়াছবি ) ; ৩৩) বগজুরি গ্রামের বিবাহোৎসব ; ৩৪) বগজুরি গ্রামের স্নানার্থী তথ্যচিত্র ( ১৯০২- ১৯০৩ সময়সীমায় তোলা ছায়াছবি ) ; ৩৫ ) রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির বিবাহোৎসব ; ৩৬) দুলিচাঁদ মল্লিকের বাড়ির বিবাহোৎসব ; ৩৭ ) শিবচরণ লাহার বাড়ির বিবাহোৎসব ; ৩৮ ) রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির বিভিন্ন উৎসব ; ৩৯ ) শিবচরণ লাহার বাড়ির বিভিন্ন উৎসব (১৯০২-১৯০৫ সময়সীমায় তোলা ছায়াছবি ) ;
প্র চা র চি ত্র ৪০ ) এডওয়ার্ড অ্যান্টি ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক কম্পানির পেটেন্ট ওষুধ ; ৪১) জবাকুসুম তেল (সি কে সেন-এর আগরপাড়া বাগানবাড়িতে গৃহীত ) ৪২) সার্সাপেরিলা (ডব্লিউ মেজর কম্পানির তৈরি । সি কে সেনের বাগানবাড়িতে গৃহীত) ১৯০৩ সালে তৈরি ।
সা রি সা রি পাঁ চি ল
হীরলাল সেনের জীবনের ইতিহাস কিংবা কর্মের পরিচয় প্রদান, এ- লেখার উদ্দেশ্য নয়। পাঠকরা আগ্রহ দেখালে সে-কাজ করা যাবে। আজ কেবল জানার দরকার যে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। নিজের ক্যামেরায় নিজে ছবি তোলা এবং সে ছায়াছবি দেখানো এই সবকটি কাজ তিনিই প্রথম করেন। তিনি অবিভক্ত ভারতের অর্থাৎ দেশভাগের পূর্বে যে রেখাহীন মানচিত্রে আমরা বাস করতাম তাঁর প্রথম পুরুষ। প্যাথেফেরিজ কম্পানি সেকথা বুঝেছিল, স্টিফেনস সাহেব বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে পালিয়েছিল, বুঝিনি কেবল আমরা।
পুনশ্চ : বহু গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা পড়তে, দেখতে ও খারিজ করতে হয়েছে, সেসবের বিস্তৃত তালিকা অপ্রকাশিত রইল। বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদকের কাছে আমার ই- মেইল আই ডি আছে সেখানে জানালে উত্তর দেওয়া যাবে। তবু বলব কালীশ মুখোপাধ্যায়, সৈকত আসগর ও সজল চট্টোপাধ্যায়ের বইগুলি পাঠকদের পড়ে নিতে। গত এক বছর ধরে ক্রমাগত তর্ক করে, রাগিয়ে আমাকে এই লেখায় প্ররোচিত করেছেন বন্ধু অভিজিৎ গোস্বামী ( চন্দন )। ব্ল্যাকি স্কোয়ারের ও ১৮ নং বাড়ির ছবি তুলে দিয়েছেন অর্পণ রায়।































